গ্রামীণ বর্ষার জলস্মৃতি

প্রবীর বিকাশ সরকার : স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত সময় ১৯৭০ সাল থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম সেই কয়েক বছর সময়কার কথা। তখন বাঁধভাঙা উদ্দাম এক কিশোর আমি। নাগরিক জলবায়ুতে বেড়ে ওঠা সেই কৈশোরে গ্রামীণ বর্ষাঋতুর অনন্য রূপমাধুরী, জলস্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার সুযোগ হয়েছিল।
জন্মভূমি সিলেটের পল্লীগ্রামের বর্ষাকালীন সেইসব জলস্মৃতি এখনো কত টাটকা সতেজ ভাবলে আশ্চর্য হই! রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে দেহমন! মানসচে দেখতে পাই মাঠ-ঘাট-প্রান্তর-পুকুর-দীঘি-খাল কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার।টকা সতেজ ভাবলে আশ্চর্য হই! রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে দেহমন! মানসচে দেখতে পাই মাঠ-ঘাট-প্রান্তর-পুকুর-দীঘি-খাল কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। চারদিকে কেবলি ঘোলা থৈ থৈ ঢেউতোলা জলরাশি। জলের উপর ভেসে আছে ছবির মতো গ্রামকে গ্রাম। অধিকাংশ খড়ের চালাঘর, মাঝেমাঝে ঢেউটিনের বাড়ি আর গাছগাছালি দিগন্তহীন জলরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি করে। এবাড়ি-ওবাড়ি, হাট-ঘাট-বাজার আর স্কুলে যাওয়ার জন্য একমাত্র বাহন নৌকো।
সিলেট নিচুভূমি তাই আষাঢ় মাসেই অতিবৃষ্টির ফলে, বৃষ্টি না হলেও আসাম থেকে নেমে আসা জলের বন্যায় তলিয়ে যায় এই জেলাটি। বড় জেঠু এসে আমাকে নিয়ে যেতো গ্রামের বাড়িতে বর্ষাযাপনের জন্য। কবিপ্রকৃতিমনা আমার কাছে বর্ষা যে অত্যন্ত প্রিয়ঋতু সেটা বাবা-মা জানতো তাই বাবাই জেঠুকে অনুরোধ করেছিল প্রতি বর্ষায় গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাছাড়া বাবা ছিল গ্রামের সন্তান তাই গ্রামকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। বাবার প্রভাবই আমার ওপর পড়েছে নিঃসন্দেহে। ফলে বাবা ও জেঠুর কল্যাণে রাতের রেলে চড়ে সকালে নামতে হত ফেঞ্চুগঞ্জ স্টেশনে। তারপর সেখান থেকে আফতাব কোম্পানির লঞ্চে সাগরের মতো অস্থির কুশিয়ারা নদীর ঘনঘোলা জল চিরে চিরে যেতে হত বালাগঞ্জ থানা হয়ে কালিগঞ্জঘাটে। তীর ছুঁই ছুঁই জলওঠা ঘাটে আমাকে স্বাগত জানাত কয়েকটি কদমগাছ। আহা কী উজ্জ্বল সোনালি মাধুর্য নিয়েই না গুচ্ছ-গুচ্ছ কদমফুলগুলো বাদলা বাতাসে দুলে দুলে আমাকে বরণ করে নিত! কালিগঞ্জঘাট থেকে আবার নৌকো করে সিন্দ্রাকোনা গ্রামে, ঠার্কুদার বাড়িতে। কয়েকটি বুনোছন আর টিনের চালাঘর নিয়ে একটি বড় পরিবার। বাড়িভর্তি লোকজন। আমাকে পেয়ে তো হৈ হৈ রৈ রৈ কান্ড জেঠাত ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন ও গোমস্তাদের। কোথায় বসাবে, কি করবে অস্থির সবাই। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন, ছেলেমেয়েদের উড়ে আসা আমাকে দেখার জন্য। এ্যাত কৌতূহলের কারণ শহুরে মানুষ বলে। তখন শহুরে মানুষের মর্যাদাই ছিল আলাদা গ্রামেগঞ্জে।
সেইসময় গ্রামে লোকসংখ্যাও ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আদরযত্ন, পারস্পরিক আদানপ্রদান, ভাববিনিময় ছিল প্রগাঢ়। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল। শিার আলো না থাকলেও গ্রামীণ মানুষের নীতিজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। আতিথেয়তার তো কোনো তুলনা ছিল না গ্রাম বাংলায়। পূর্ববাংলার আতিথেয়তা তো এখনো উপমহাদেশ কেন বিশ্বব্যাপী বহুশ্রুত প্রশংসিত ব্যাপার। কত বাড়িতে যে গিয়েছি বেড়াতে তার হিসেব নেই। বড়বাড়ি, ছোটবাড়ি। প্রতিটি বাড়ি উঁচুভূমিতে অবস্থিত বন্যা থেকে রা পাবার জন্য। প্রতিটি বাড়িরই পরিবেশ নানা জাতের বড় বড় আম, জাম, ডুমুর, কাঁঠাল, চাঁপা, হিজল, কদম, বেতস, অশ্বত্থ, নিম আর বাঁশের ঝোঁপ-ঝাড়কে জড়িয়ে থাকা নিবিড় বুনো গাছগাছালি-লতাপাতার নিঃশব্দ মায়াজালে জড়ানো। প্রায় প্রতিটি বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে একটি শান্ত শাপলা-কলমিফোটা পুকুর তার চারপাশে ঘনসবুজ রঙা বেতের জঙ্গল। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে মুত্রাগাছ। নির্গন্ধ সাদাফুল ফোটা এই গাছ কেটে চিকন-চিকন ফালি করে চিরে রোদে শুকিয়ে তারপর শীতলপাটি তৈরি করা হয়। এটা সিলেটের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। আবার পাটকাঠি, বুনোছন, ডাঁটাশাক, হালকা পণ্যসামগ্রী বাঁধা; হাট থেকে কেনা মাছ বেঁধে ঝুলিয়ে আনার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই কাঁচা বেতের ফালি। জানি না এই রীতি এখনো প্রচলিত আছে কিনা।
সে এমন একটা সময় যখন জিনিসপত্রের দামও ছিল সস্তা, কিন্তু মানুষের অভাব-অনটন ছিল নিত্যমৈত্তিক ব্যাপার। জেঠু ছিল মাঝারি গোছের একজন কৃষক, বৈঠকিসভার গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। সিলেটের ঐতিহ্য অনুযায়ী বর্ষাকালে জেঠু মাছ ধরে বিক্রিও করতো আড়তদার, মহাজনের কাছে। এই মাছ ধরার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি জেঠুর সঙ্গে থেকে। জলভর্তি মাঠে, হাওরে এবং নদীতে নৌকো করে বড় বড় জাল ফেলে মাছ ধরতো গোমস্তাদের নিয়ে। রাতের বেলা বাড়ির চারপাশে বড় বড় বাঁশের চাঁই পেতে রাখতো। এক গাছ থেকে দূরবর্তী আরেক গাছে, আবার বাঁশের খুঁটি গেঁথে গেঁথে দীর্ঘ সুতোর মধ্যে চার/পাঁচ হাত অন্তর অন্তর বড়শি বেঁধে তাতে ব্যাঙ, তেলেপোকা, কেঁচো, টাকি, পুটি, গুতুম ইত্যাদি ছোট-ছোট মাছ গেঁথে দিত। রাতের বেলা ছোট-বড় বিভিন্ন মাছ যেমন বোয়াল, রুই, মিরকা, কালিবাউস, আইর, ঘাগট, গজার, বড় বড় বাইনমাছ বড়শিতে আটকা পড়ে ছোটোছুটি করত। পরের দিন ভোর বেলা জেঠাত ভাই মাখনদা ও গোমস্তাদের নিয়ে নৌকোতে টেনে তুলতো সেই মাছ। তবে বোয়াল মাছই বেশি ধরা পড়ত। একবার তো বিশাল এক চিতল মাছ ধরা পড়েছিল। সচরাচর এমন ঘটে না। ভালো দামে বিক্রি করেছিল জেঠু। চিতল মাছ কাঁটাবহুল কিন্তু মুড়মুড়ে ভাজি খেতে দারুণ স্বাদ। বড় বড় কচ্ছপও যেমন ধরা পড়ত মাঝেমধ্যে তেমনি ঢোঁড়া, চন্দ্রবোড়া, মেটেসাপও। কোনো-কোনো সাপ মরে ভেসে থাকত। বেশি কষ্ট হত বড় বড় কচ্ছপগুলোর মুখ ও গলা থেকে বড়শির কাঁটা খুলতে গিয়ে। রক্তারক্তি কান্ড। তারপর সেগুলোকে ছেড়ে দেয়া হত। অপোকৃত ছোট মাছগুলোকে ছেড়ে দিত জেঠু আরও বড় হওয়ার জন্য। পুরো বর্ষাকালব্যাপী সমগ্র সিলেট জেলা জুড়ে মাছ ধরার মৌসুম। উৎসব উৎসব সাজ। বর্ণাঢ্য মৎস্য উৎসব। তখন প্রচুর মাছ পাওয়া যেত সিলেটে। আর কত রকমের যে মাছ, এখন তো সেসব দেখাই যায় না! প্রত্যেকদিন সকাল বেলা বাড়ির ঘাটে মহাজনী নৌকো আসত মাছ কেনার জন্য। দরদাম চলত অনেকণ। প্রতিদিন ওঠানামা করত দাম মাছের আকার অনুযায়ী। ডিমওয়ালা মাছের দাম ছিল বেশি। অবশ্য নিজেদের খাওয়ার জন্য মাছ রেখে দেয়া হত।
বাড়ির আশেপাশে থৈ থৈ জল। ঘরগুলোর পেছনভাগ জুড়ে বুনোঘাস, দীর্ঘ ছন, গাছগাছালি, লতাপাতায় একাকার এক জঙ্গল। বুনো গন্ধে এসে জটলা করত পোকা, মাকড়সা, ছোট-বড় নানা রঙের আল্পনাআঁকা প্রজাপতি, ফড়িং, ঘাসফড়িং ইত্যাদি। আর বড় বড় লাল, কালো ডোঙা বা কাঠপিঁপড়ে লতাপাতা জড়ানো ঝোঁপের ভিতরে বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ত। জঙ্গলের তলে তলে জলের প্রবাহ তাতে ডিম ঝরে ঝরে পড়ে স্রোতে ভেসে চলে যেত, মাছেরও উদরস্ত হত। গরু ও ছাগলগুলো সেখানে জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই বুনো গাছগাছালির লতাপাতা খেত। খড়ের গাদা থেকে টেনে টেনে খড়ও খেত। খড়ে অরুচি ধরলেই চলে যেত জঙ্গলে। হাঁসগুলো সেখানেই শামুক-গুগলি খেত ডুবে ডুবে সারাদিন। ঐ জঙ্গলের তলে জলের নিচে পেতে রাখা হত মাছ ধরার ফাঁদ চাঁই সন্ধেবেলা। এগুলো জেঠিমা, জেঠাত বোন, মোমস্তাদের বৌ-ঝিরা-পেতে রাখতো শামুকের ছোট ছোট টুকরো, কেঁচো আর গোবরের গোলা ভিতরে দিয়ে। তারপর শক্ত কোনো গাছে বা মাটিতে খুঁটি গেড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত যাতে জলের তোড়ে ভেসে চলে না যায়। বর্ষায় কত রকমের কেঁচো যে কিলবিল করত উঠোনে, বাড়ির দাওয়া ও দেয়ালে হিসেব নেই। গোয়ালঘর তো ছিল কেঁচোর কারখানা মূলত গোবরের জন্য। ঐ আধারগুলো খাওয়ার লোভেই রাতের বেলা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাঁইতে ঢুকে পড়ত। খলসে, মেনি, টাকি, বাইন, ট্যাংরা, ঘোলা ট্যাংরা, ছোটপুটি, সরপুটি, মেনি, পাবদা, কাঙলা, চাঁদা, কই, মাগুর, শিং, বেলে, গুতুম, চিংড়ি কত রকমের মাছ!। কাঁকড়া তো বটেই মাঝে মাঝে সাপও ঢুকে পড়ত কিন্তু বেরোতে পারত না। তাই সাবধানে চাঁইগুলো জলের তল থেকে তুলতে হত দড়ি ধরে টেনে টেনে। এত মাছ ধরা পড়ত যে বেশ শক্তি ব্যয় করতে হত চাঁইগুলো তুলে উঠোনে নিয়ে আসতে। প্রচুর জলজোঁকও লেপ্টে থাকত চাঁইগুলোতে। আমরা সেগুলোকে লবন দিয়ে মারতাম।
প্রায় বাড়িতে মাছ ধরা ছিল গ্রামীণ রীতি। অনেকেই ধৃত মাছ হাটে বা দূরের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। পাশের বাড়ির লোকদের সঙ্গে আমিও গিয়েছি কয়েকবার বালাগঞ্জ থানার বড় বাজারে। জেঠুর সঙ্গেও অন্য গ্রামে একবার গিয়েছিলাম এক আত্মীয়র বিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। উপহার ছিল বড় বড় রুই ও বোয়াল মাছ। সেকি আদরত্ন আমাদের! বিশেষ করে সম্মানিত বিদেশির মতোই আমার সমাদর দেখে লজ্জাই পেয়েছিলাম। কিন্তু এটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার তৎকালীন গাঁওগেরামে। বর্ষাকালে গ্রামের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান সে আরেক বিরল অভিজ্ঞতা। সেবার দেখেছি ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে বরযাত্রীদলকে ভাড়া করা একাধিক ময়ূরপঙ্খী নৌকো সাজিয়ে ঢোলঢোলক, কাঁসর, করতাল ইত্যাদি বাদ্যবাজনা বাজিয়ে এসে বাড়ির পাশ্ববর্তী বনের মধ্যে নৌকো বেঁধে তার উপর সেজেগুজে, কাপড় পাল্টিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি ও টোপর পরে কনের বাড়িতে উঠতে। চারদিকে উলুর ধ্বনি, বাদ্যবাজনা, হুড়োহুড়ি, শিশুদের হৈচৈ এসবের মধ্য দিয়েই মেয়েরা সাজানো কুলো থেকে ফুল ছড়িয়ে বরবরণ করে নিল। সেই বরের সঙ্গে এক ফাঁকে আলাপও হয়েছিল আমার। তিনি হবিগঞ্জের কোনো এক স্কুলের অঙ্কের শিক ছিলেন। পরে কুমিল্লায় আমাদের বাসায়ও একাধিকবার বেড়াতে এসেছিলেন। প্রতিবারই নিয়ে আসতেন মাটির পাতিলে করে নারকেলের নাড়ু, কদমা, জিলিপি, পেড়া আর মুড়ির মোয়া। সেই ঐতিহ্যবাহী খাবার এখন মনে হয় উঠেই গেছে!
বাংলার বর্ষাঋতুতে কয়েকদিন লাগাতার বৃষ্টি লেগে থাকাটাই রীতি। সারা দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি, কখনো কখনো দমকা বাতাস। বারান্দা থেকে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যেত দেখতাম কত রকমের নৌকো যে যাওয়া-আসা করত, নানা রঙের পালতোলা যাত্রীবাহী নাও, জলে ডুবুডুবু প্রায় মালবাহী বিশাল গয়না নাও, বরযাত্রীর নৌকোমিছিল, ইলসে ধরার ছিপনৌকো। নৌকো-বাইচ উৎসব কী ঘটা করেই না অনুষ্ঠিত হত! প্রতিবেশী বাড়ির কেউ কেউ মাঝেমাঝে কলাগাছ, বাঁশের ভেলা নিয়েও জলামাঠ ভেঙ্গে মাছ ধরতে চলে যেতো কোথাও। মাঝেমাঝে একাধিক দৈত্য গম্ভীরমুখো কালো গয়না নৌকো সারি বেঁধে রাত্রিযাপনের জন্য বাড়ির অদূরে নোঙর ফেলত। রাতের বেলা টিমটিম আলো জ্বলত নৌকোর মধ্যে, রান্নাবাড়া হত, কেউ কেউ জল সেচে বাইরে ফেলত। পালগুলো গুটিয়ে ফেলা হত। গভীর রাতে কোনো বিরহী পুরুষ কন্ঠের পল্লীগানের সুর ভেসে আসত। কোনো-কোনোদিন আকাশের ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ঝলকের আলোতে রাতের বেলাও দেখতাম ভেজা বাতাসে থৈ থৈ করে নাচছে মাঠের জলরাশি। চলন্ত এক চলচ্চিত্র যেন। আহা বহু বছরের ব্যবধানে সেই দৃশ্য আর কোথাও দেখতে পেলাম না!
কোনো-কোনোদিন দুপুরবেলা বারান্দায় বসে লুডু খেলেছি। পায়রাগুলোকে ডাল, চাল খাইয়ে আনন্দ করেছি। আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, কামরাঙা, আখ, জামরুল, তরমুজ, বাঙ্গি, বেতস ফলের স্বাদ নিয়েছি চেটেপুটে। খিরে, শসা বা কাঁঠালের মুচির সঙ্গে মরিচপোড়া ও লবন মিশিয়ে খাওয়ার স্বাদ পৃথিবীর আর কোথাও কি আছে? মাঝেমাঝে বুনো তেঁতুল, চালতে ফল খাওয়ার ফলে দাঁত হয়ে যেত টক তখন কোনো শক্ত খাবার খেতে পারতাম না। নাগরিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ফলফসারি এবং মাছ-মাংশ আর শাকসবজি রান্নার মধ্যে রং ও স্বাদের একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সিলেটের মানুষ সাধারণত মাছ, মাংশ ও আনাজ ছোট ছোট করে কেটে রান্না করে। ঝাল খায় প্রচুর। নানা রকম ভর্তা তো আছেই। সাদা ভাতের সঙ্গে এই নানা পদের খাবারের গন্ধ ও স্বাদ আর কোথাও আমি পাইনি আজও! অদ্ভুত, অবিস্মরণীয় সেইসব স্বাদ ও গন্ধ আজও আমার স্মৃতিকে উদ্বেল করে। সাদা সুগন্ধী বিরুন চালের শক্ত-আঠালো ভাতের সঙ্গে ইলিশ, বোয়াল আর রুই মাছের কড়কড়ে ভাজির স্বাদ ভুলি কী করে! দুপুর বেলা খাওয়ার পর জেঠিমা দিত ঘরে পাতা দই আর রাতের বেলা দুধের সঙ্গে আম। সকাল বেলা ছিল বেতের সাজিতে করে মুড়ি খাওয়া নারকেলের নাড়–, গুড়, পাটালি সন্দেশ বা পেড়া দিয়ে, আবার কোনো-কোনোদিন সিদ্ধ থকথকে পাট বা নালিতা শাকের সঙ্গে গরম ভাত, কোনো- কোনোদিন ঘরেই তৈরি মৌ মৌ ঘি এর সঙ্গে আলুর ভর্তা। অন্য এক গ্রাম থেকে সারা বছরই মাঠা আর কলাপাতায় মোড়া ধবধবে সাদা মাখন দিয়ে যেত একজন ভুড়িওয়ালা হিন্দুলোক। কী অসামান্য স্বাদ সেই মাঠা আর মাখনের! নালিতা পাতার অদ্ভুত তেতো সে স্বাদ আজও যেন অনুভূত হয়। বর্ষার অন্যতম পদ শর্ষের ইলিশ কিংবা সবজির সঙ্গে ছোট ছোট করে কাটা নোনাইলিশের চচ্চড়ি অথবা শুকনো খিচুড়ি খাওয়ার জন্য মনে হয় আবার ছেলেবেলায় ফিরে যাই।
সিলেট চায়ের জন্য প্রসিদ্ধ হলেও গ্রামে চা খাওয়ার রীতি ছিল না। বাসা থেকে নিয়ে যেতাম চাপাতা। চা তৈরি করে দিত জেঠাত বোনেরা। আমার আগমন উপলে একটি উৎসবই যেন হয়ে যেত বাড়িতে। আত্মীয়স্বজন আসতো। লোকজন, বিশেষ বিশেষ রান্না, পিঠেপুলি তৈরি, ঢেঁকি ভানার শব্দ, ছেলেমেয়েদের হৈচৈতে গম গম করত সারাবাড়ি। বর্ষাকালে গ্রামের স্কুলগুলো প্রায় বন্ধই থাকত। দু-একটি মাত্র স্কুল তাও জলের তলে ডুবে থাকত সারা বর্ষাকাল। কাজেই-ছেলেমেয়েদের হাতে অফুরন্ত ছুটি। জেঠু নিজে ছোট-ছোট কাঠের নৌকো তৈরি করে দিয়েছিল। বাড়ির ঘাটায় রীতিমতো লোহার চেইন দিয়ে বাঁধা থাকত, যাতে কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে। নৌকোচুরির কথা প্রায় শোনা যেত। সেগুলোর উপর চড়ে দাপাদাপি করা, জলে ঝাঁপ দেয়া ইত্যাদি জলক্রীড়ায় মেতে উঠতাম। বেশ ঠান্ডা জল যদিও কিন্তু জ্বরজারি হত না তেমন তবে জলে, কাদায় হাঁটাহাঁটি করার কারণে পায়ের পাতা ও আঙুলে ঘা হত প্রায় সবারই। আমারও হয়েছিল। কী যে ভীষণ চুলকানি। চুলকাতে যে কী আরাম ভুক্তভোগী ছাড়া সেটা অন্য কারো উপলদ্ধি করা সম্ভব নয়। রাতে ঘুম হারাম হয়ে যেত যেদিন বেশি চুলকানি উঠত। কেরোসিন, মলম আরও কি কি ওষুধ জেঠিমা মেখে দিত।
সন্ধ্যে হলেই সারাটা গ্রাম, গ্রাম তো নয় সমগ্র পৃথিবীটাই নিমজ্জিত হয়ে যেত গভীর কালো মায়াবী-ডাকিনী অন্ধকারে। সুয়োরানী-দুয়োরানী, শুকশারি, রাস-খোক্কস, সাতভাইচম্পা, রামলণ, মহাভারতের গল্প জমে উঠত বারান্দায় হারিকেনের অস্পষ্ট দুর্বল আলোয়। গল্প বলতো বৌদি, কাকিমা বা বয়স্ক অন্য কেউ। মাঝেমাঝে জেঠুও যেসব রহসম্যয় গল্প বলতো তাতে শরীরের লোম খাঁড়া হয়ে যেত। মনে আছে একবার বলেছিল, হাওরে ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে মধ্যরাতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে মেছোভূত কিভাবে তাড়া করেছিল বাড়ি পর্যন্ত! সেবার বাতাসে কুপি নিভে গিয়েছিল, তেলও ছিল না। আগুন না থাকাতে পিছু নিয়েছিল দুটি ভূত। চেহারা তো দেখা যায় না কিন্তু ঠান্ডা লিকলিকে হাত দিয়ে মাছের খালুই থেকে মাছ তুলে নেয়ার চেষ্টা করেছিল সারা পথ। জেঠু শক্ত হাতে আগলে রেখেছিল খালুই। পাটাতনের নিচেও মাছ ছিল, খলবল করছিল। সেগুলো ধরতে পারেনি। দুজন সঙ্গীর একজন নৌকো বেয়ে চলছিল। অন্যজন বৈঠা এলোপাথাড়ি ঘুরিয়েছে। কয়েকবার বৈঠার বাড়ি খেয়ে কুঁই কুঁই শব্দ করে জলের উপর ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দে কিছু পড়ার শব্দ উঠেছে। কিন্তু কিছুণ পরে আবার ঠান্ডা হাড় জিরজিরে হাতের স্পর্শ! ভোরবেলা বাড়ির ঘাটে এসে দুটো মাঝারি গোছের বোয়াল মাছ মটকি থেকে বের করে জেঠু ছুঁড়ে দিয়েছিল উঠোনে এবং নিমিষেই তা হাওয়া হয়ে গিয়েছিল! আর একবার বলেছিল আঠালুকা নামের একটি বিরাট ছাইরঙা সাপ কিভাবে তাড়া করেছিল ফনা তুলে দিনের বেলা হাওরে মাছ ধরার সময়! হঠাৎ জেঠুর মনে পড়েছিল এই সাপ দুর্গন্ধযুক্ত তামাকের জল পছন্দ করে না। সেবার হুঁকোর ভিতরে থাকা জলের সঙ্গে পোড়া তামাকের ছাই মিশিয়ে ঢেলে দিলে ঘুরে চলে গিয়েছিল সাপটি।
একবার আমি থাকা অবস্থায় প্রায় সাত হাত লম্বা শেওলাপড়া বিশাল এক কাতল মাছ ধরেছিল কালিন্দী খালে জাল বের দিয়ে কয়েক ঘন্টা সময় লাগিয়ে দশবারো জন মিলে। মাছ তো নয় জলদৈত্য যেন! সে এক এলাহী কান্ড! সেই ঘটনা দেখার জন্য সারাদিনই সিন্দ্রাকোনা ও পাশ্ববর্তী গ্রামের শিশু-কিশোর, লোকজন বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। মাছটি কাটার পর পেটের ভিতরে ছোট-ছোট থালাবাসন, হাঁড়ি-পাতিলের টুকরো, পিতল ও কাচের চুড়ি, কাঠের টুকরো, পাখির হাড়গোড়, প্রচুর ছোট ছোট মাছ পাওয়া গিয়েছিল। অনেকেই মাছের টুকরো নিয়ে গেছে, আবার অনেকেই কুসংস্কারে আক্রান্ত বলে নেয়নি, কারণ তাঁদের বিশ্বাস মাছ কখনো এ্যাত বড় হতে পারে না! এটা জলের দেওদানব হবে! সুতরাং এর দেহাংশ খেলে পরে নির্ঘাৎ অভিশাপ নেবে আসবে পরিবারের ওপর। অবশ্য যারা খেয়েছে তাঁদের কিছুই হয়নি। আমারও হয়নি। আসলে অনেক অশিতি মানুষই জানে না যে, সমুদ্রের বিশালাকার তিমিমাছ শিকার করে খাওয়ার রীতি কত প্রাচীন! যাহোক, জেঠুর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাও আছে মাঝেমধ্যে কিছু বলতো সময় পেলে আর শ্বাসরুদ্ধকর ভৌতিক পরিবেশে আমরা শুনতাম সেসব গল্প। ভয়ে কাঁটা দিত শরীর। মনে হত পেছনে বুঝি কেউ এসে বসে আছে।
হঠাৎ পলকা বাতাস ঘাড়ে এসে লাগতেই মনে হত কোনো অশরীরী প্রেতাত্মার হাতের স্পর্শ বুঝি! অবশ্য এর কারণও ছিল: প্রথমত, রাত্রিকালীন গ্রামীণ ভৌতিক পরিবেশ আর দ্বিতীয়ত, দস্যু-তস্কর-ডাকাত, রহস্যগল্পের প্রভাব। সেই বয়সে আমরা পড়তাম শালর্কহোমস, দস্যু শশধর, দস্যু বাহরাম, দস্যু বনহুর কিংবা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্যেপন্যাস, অদ্রীশ বর্ধনের রোমহর্ষক খুনাখুনির গল্প আর ভূত-পেত্নী-প্রেতাত্মার নানা রকম ভয়ঙ্কর কাহিনি-গল্প-উপন্যাস তো ছিলই। এসবের প্রভাবে শহরবাসী আমার মনেও ভয় দোলা দিত বৈকি মূলত পরিবেশের কারণে। মনের অজান্তে পেছন ফিরে দেখতাম কেউ আছে কিনা ঘুটঘুটে অন্ধকারে! রাতের বেলা আমি ঘুমুতাম আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় মাখনদার সঙ্গে। গ্রামের মানুষ সারাদিন প্রচন্ড পরিশ্রম করে তাই বালিশে মাথা রাখতেই দ্রুত ঘুমসাগরে তলিয়ে যায় গভীর ক্লান্তির কারণে। মাখনদাও তাই, আমার চোখের পাতা সহজে মিলিত হত না নিকষ অন্ধকারে। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে ঝিঁঝিপোকাসহ নানা রকম পোকামাকড় ও নিশিজাগা পাখির পাখা ঝাঁপটা-ঝাঁপটি, সহসা কান্নার সুর মিলেমিশে অদ্ভুত এক ভয়ঙ্কর রস জমে উঠত মনের মধ্যে। দস্যু বা ডাকাতের ভয়ও যে ছিল না তা নয়।
বর্ষাঘন রাতে ডাকাতি বেড়ে যেত। যদিওবা বড় কোনো ডাকাতি হয়নি আমার অবস্থানকালে কখনো সিন্দ্রাকোনা গ্রামে। তবে শুনতাম বালাগঞ্জ, বিয়ানিবাজার, শেরপুর, হাদিগঞ্জ, জকিগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কালিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মানিককোণা, ঢাকাদণি, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় বড় বড় ডাকাতি হওয়ার খবর। কিন্তু মানুষ মারার কথা খুব একটা শোনা যেত না। সম্ভবত অস্ত্রের মুখে ডাকাতি করে সব নিয়ে যেত ডাকাতরা। সুরমা, কুশিয়ারা, মনুনদীতেও যাত্রীবাহী নৌকোতে, গয়না নৌকোয় এবং লঞ্চে ডাকাতি হত। গ্রামে বেশি ডাকাতি হত অমাবশ্যার সময়। বর্ষাকালে শীতল বাতাসে মানুষের ঘুম হয় খুব গাঢ় আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগায় ডাকাত-দস্যুর দল। কতিপয় ডাকাতের নাম শুনলে তখন পিলে চমকে যেত সাহসী মানুষেরও। বাবা ছিল পুলিশ অফিসার তাঁর মুখেও ডাকাতি ও ডাকাত ধরার গল্প কম শুনিনি!
গ্রামের বাড়িতে সন্ধেরাতেই রাতের খাবার খাওয়ার নিয়ম। রান্নাঘরে জেঠিমার মুসুরি ডাল রান্নার শেষ সিগনাল হিসেবে ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ-ঝাঁ ঝাঁ করে শব্দ উঠত লোহার বড় কড়াইয়ে, পেঁয়াজ-তেজপাতা-এলাচি- মেথির মিশ্রিত ঝাঁঝালো গন্ধ এসে লাগত নাকে। বুঝতাম রান্না শেষ। এবার থালা পেতে বসে যাও। সবাই একসঙ্গে খেতে পারতাম না। অতিথি বলে আমিও ছোটদের সঙ্গে একসঙ্গে আগে খেতাম। জেঠু তাঁর বন্ধু বা পাশের বাড়ির প্রতিবেশীদের সঙ্গে বসে বারান্দায় অন্ধকারেই গড়গড়া তামাক খেতো কথা বলতে বলতে। হয়ত সেদিন বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকেই, টিনের চালে টুপটাপ, ঝিম ঝিম বৃষ্টির শব্দ, ঘরের মধ্যে পিঁড়ি, চাটাই বিছিয়ে কুপির স্বল্পালোকে ভাত খাচ্ছি, রেণুদি বেড়ে দিচ্ছে, রবির মা পিসিমা যোগান দিচ্ছে, ছোট পিসিমা এক্কেবারে যারা ছোট্ট তাদেরকে খাওয়াচ্ছে বেড়ালটাকে আগলে রেখে, মাটির দেয়ালে সবার কালো কালো ছোট, দীর্ঘ ছায়া নড়ছে। একটা ভৌতিক কিন্তু বড়ই রোমাঞ্চকর পরিবেশ যা শহুরে পরিবেশে বেড়ে ওঠা আমার জন্য ছিল অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা।
মাঝেমাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত কানে এসে বাজত চাপা মেয়েলি কন্ঠ, হাসাহাসি, জিনিসপত্রের টুংটাং শব্দ। বুঝতাম রান্নাঘরে পিঠেপুলি তৈরি হচ্ছে। গুড়, নারকেল, মিষ্টান্নের আকুলি-বিকুলি ঘ্রাণ বৃষ্টিভেজা বাতাসে ভেসে এসে নাকে লাগত। কোনো-কোনো দিন গভীর রাতে গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামত। আর এই সুযোগে মাছচোর এসে মাছ তুলে নিয়ে পালিয়ে যেত। তাই জেঠু, মাখনদা ও গোমস্তারা অন্ধকারে প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেই পাহারা দিতে চলে যেতো নৌকো নিয়ে। ফিরতো একেবারে ভোরবেলা মাছ নিয়ে। ছইয়ের ভিতরে থাকা সত্ত্বেও ভিজে জবজবে হয়ে যেতো।
যেদিন রোদ উঠত সেদিন গ্রামীণ বর্ষার আরেক রূপ দেখে অভিভূত হতাম। হলদেরঙা ঘোলা জলরাশি সূর্যের আলোতে সোনার মতো চকমক করত দিগন্তব্যাপী। গাছগাছালির সবুজ পাতাপল্লবে চিকচিক করত সোনালি রোদ। জলপায়রাগুলো ভিড় জমাতো গাছগাছালির মাথায়, ডিগবাজি খেয়ে উড়ে উড়ে বেড়াতো। কয়েকদিন একাধারে রোদালো দিন থাকলে পরে নৌকো করে বেড়াতে যেতাম দূরে কোথাও মাখনদার সঙ্গে বাড়ির সব ছেলেমেয়ে। সঙ্গে নিতাম ছিপ-বড়শি। কোথাও কোথাও স্বচ্ছ শীতল অগভীর জলের দেখা পেতাম সেখান থেকে তুলে নিতাম শাপলা, কলমিফুল, জলজ ঘাসফুল, লতাগুল্ম, ছোট ছোট মাছ, শামুক। কোনো এক বনের ধারে যেখানে জল কম হিজল গাছে নৌকো বেঁধে মাছ ধরত---ট্যাংরা, ঘোলা ট্যাংরা, পাবদা, কাঙলা, টাকি, সরপুটি, মেনি, কই, বাইন, বেলে, শিং প্রভৃতি। মাছ ধরার যে কী আনন্দ সত্যি ব্যাখ্যার অতীত! শুধু একটি মাছ ধরা যেত না, অবশ্য সবখানে মাছটি ছিলও না, তার নাম রানীমাছ। টকটকে হলদে শরীরে মোটা কালো রেখাবলিযুক্ত ছোট্ট এই মাছ ধরা পড়ত বাঁশ বা বেতের চাঁইয়ে বাড়ির পেছনে জঙ্গলের তলে পরিষ্কার জলে। এই মাছের চচ্চড়িভাজি খেতে দারুণ স্বাদ। কোথা থেকে যে আসত ঝাঁক বেঁধে সে এক রহস্য। প্রবীণ অনেককেই জিজ্ঞেস করে এই রহস্যের কিনারা করতে পারিনি। বিকেল বেলা তপ্ত সোনালি রোদে নাইতে নাইতে ফেরার পথে দূরে বড় বড় ঢেউ তুলে নদীর মাঝ দিয়ে বড় লঞ্চ নাকি স্টিমার চলে যেত ধোঁয়ার কুন্ডুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে আকাশে, মাঝেমাঝে ভোঁ ভোঁ শব্দ ছেড়ে, সেই আগ্রাসী দুরন্ত ঢেউ আমাদের নৌকোতেও এসে বাড়ি খেত, বেশ জোরে-শোরে দুলত নৌকো, আমরা ছইয়ের ভিতরে গিয়ে বসে পড়তাম, জল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিত শরীর, নৌকো সামাল দিত মাখনদা। কোনো-কোনোদিন সন্ধেবেলা জেঠু নিয়ে যেতো নদীর তীরে অবস্থিত আমাদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মন্দিরওলা এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত দালান বাড়িতে। বেশ বড়বাড়ি। আত্মীয়টি বালাগঞ্জ বাজারের অন্যতম বড় কাপড়ের ব্যবসায়ী। পুজো বা উৎসব জাতীয় কিছু অনুষ্ঠিত হত।
কয়েকদিনের ঠা ঠা রোদে শুকিয়ে যেত কাদা, উঠোনে শীতল পাটি বিছিয়ে গ্রামের লোকজনকে বসতে দেয়া হত। প্রতিবেশী, দূরদূরান্ত থেকে মুসলমানরাও আসতো। জ্বালিয়ে দেয়া হত কয়েকটি হ্যাজাক লাইট। ফলে বেশ আলোকিত হয়ে উঠত চারদিক। বাড়ির ভিতরে ছিল মন্দির, সেখানে বৌ-ঝি-বয়স্ক মহিলারা জড়ো হতো, গান করতো। ধুতি আর ফতুয়া পরা একদল লোক যাদের কপালে, নাকে সাদা রঙের তিলক আঁকা থাকত, বৈষ্ণবীদল বলে পরিচিত, আমন্ত্রিত হয়ে আসতো অন্য গ্রাম থেকে উৎসবে ঢাক-ঢোল-করতাল-হারমনিয়ম-বাঁশী বাজানোর জন্য। জমজমাট পদাবলী কীর্তনের আসর বসত। অল্পবয়সী যুগলদম্পতির রাধা-কৃষ্ণের নাচ দেখেছি। শহুরে ছেলে বলে সমাদরও পেয়েছি সমবয়সী একটু সাহসী মেয়েদের কাছে। সেইসঙ্গে আড়ালে-আবডালে লাজুক মেয়েদের কৌতূহলজনিত ফিসফাসানি, হাসির শব্দ শুনেছি। চোখাচোখিও হয়েছে কারো কারো সঙ্গে। গানের আসর শেষ হলে পরে কলার পাতায় করে মাছভাজিসহ গরম গরম তরল খিচুড়ি খেয়েছি বৈঠকখানায় বসে। খাওয়ার পর জেঠু রীতি অনুযায়ী হুঁকোতে কয়েক দম দিয়ে, পানসুপুরি মুখে পুরে বিদায় নিতো। বেশ রাত করে ফিরতাম নৌকো করে। জেঠুই নৌকো বেয়ে যেতো। আমি বিপরীত পাটাতনে বসে দেখতাম অপার বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেও চরাচরব্যাপী অস্বচ্ছ একটা আলো ছড়িয়ে আছে। এই আলো ল-কোটি গ্রহ-তারা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ধরায় ছিটকে এসে পড়েছে। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের শব্দ, নৌকোর দুলুনি, কাঠের বৈঠার জলকাটার অদ্ভুত এক সুরলহরি আর শীতল বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম জানি না। ঘুমের ঘোরে কানে এসে বাজত বহুদূরে কারো বাজানো বেউর বাঁশীর চিকন সুর, কোনো এক নিশিযাত্রী মাঝির উদাসীকন্ঠে গীত হাসনরাজার মরমী গান। তখন ছিলাম বালক তেমন কোনো বিশেষ অনুভূতি জাগেনি কিন্তু এখন জীবনের এই অপরাহ্নে সেই একই দৃশ্য কতখানি ভিন্নমাত্রার হবে, কত গভীরভাবে স্মৃতিকাতর করে তুলবে ভাবতেই বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে।
আবার জোছনারাতে গ্রাম বাংলার বর্ষার অপরূপ রূপ দেখার সুযোগও হয়েছে। চাঁদের আলো এত উজ্জ্বল যে দিন বলেই ভ্রম হত। সন্ধেবেলা বাড়ির ঝোঁপঝাড় থেকে ধেয়ে আসত জুঁই, চাপা, বেলি এবং অকালে ফোটা শিউলির মিশ্রিত ভারী গন্ধ। দিগন্তব্যাপী দেখতাম ঘোলা জলরাশি চাঁদের আলোতে সোনালি রূপ ধারণ করেছে। মাখনদার ছিল যাত্রাপালা দেখার প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ। এছাড়া গ্রামেগঞ্জে তৎসময়ে বিনোদন বলতে আর কীইবা ছিল একমাত্র যাত্রাপালা, কীর্তন, মেয়েদের ধামালি নাচ ছাড়া। নৌকোয় করে মাখানদা কয়েকবার নিয়ে গিয়েছিল যাত্রা দেখাতে। কিস্তু আমার ভালোলাগেনি কেমন যেন সেকেলে সেকেলে ঠেকেছিল, সম্ভবত শহরে চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক দেখার ফলে এমনটি মনে হয়েছিল। আমি প্যান্ডেলের নিচে বিছানো পাটির উপর ঘুমিয়ে পড়তাম।
শেষবার বর্ষাযাপনের জন্য সিলেটের দিকে একা একা রওয়ানা হয়েছিলাম। বাবার অনুরোধে একজন কনস্টেবল আমাকে ট্রেনে তুলে টিটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল যাতে নিরাপদে যেতে পারি। ফেঞ্চুগঞ্জ স্টেশন থেকে জেঠু এসে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। শ্রাবণ মাস। এই রোদ এই বৃষ্টি। লঞ্চে চড়ে দিগন্তপ্লাবিত কুশিয়ারা নদীর ঘোলা জলরাশি জুড়ে মেঘলা রোদের ঝিলিমিলি চিরে চিরে জলপায়রার ওড়োওড়ি আর ভেসে ভেসে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে দুপুরে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছালাম। প্রায় মাস খানেক আনন্দ-ফূর্তি করেছি সেবার। প্রতিবারের মতো সেবারও নবরূপে আবিষ্কার করেছি গ্রামীণ বর্ষাঋতুকে। কৈশোর ও যৌবনের মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছি তখন সবেমাত্র। আধফোটা সাহস, আধোলাজুক বয়সের দৃষ্টিতে তখন সবই রমণীয়, স্বপ্নময় আর রোমাঞ্চকর ফলে আমি যেন মায়াকাননের বিপিনবিহারী। অন্যরকম এক ছায়া-মায়ার আলোয় আবিষ্কার করেছিলাম শেষ গ্রামীণ বর্ষাকে।
ফেরার দিন কয়েক আগে এক রোদালো সকালে জেঠিমা যাবে পুজো দিতে প্রাচীন কালাচান্দ বটবৃকে। প্রাচীনত্বের ভারে নুয়ে পড়া নাতিদীর্ঘ বটের পাতার মধ্যে কালো কালো ছোপ আছে যা অন্য বটে নেই। এই বিশেষত্বের কারণে পুরনোকাল থেকে হিন্দুদের বিশ্বাসে এই বৃক্ষ লৌকিক দেবতা, মানত করলে ফলে নাকি। কী ভেবে জেঠিমা সঙ্গে নিল আমাকে আর সরমাকে। সরমা, পিতৃহারা মেয়েটি আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে, বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর জেঠু দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বলে মা-মেয়েকে নিয়ে আসে এই বাড়িতে। সরমার মা রাঙ্গাপিসী জেঠিমাকে গেরস্থালির কাজ ছাড়াও নানা রকম সাহায্য-সহযোগিতা করে। মাঝেমাঝে ভেবেছি কেন তিনি রাঙ্গাপিসী, রেণুদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, আসল নাম আমিও জানি না, বাবা ‘রাঙ্গা’ বলেই ডাকে সম্ভবত পিসীর গায়ের রং খুব ফর্সা বলে। সেই কারণেই কিনা জানি না সরমাও মায়ের মতো গৌরী এবং খুবই সুন্দরী। তাকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে জেঠু। সেদিন সকালে জেঠিমা নিজেই নৌকো বেয়ে নিয়ে গেলো, আমি লগি গেড়ে বেঁধে রাখলাম নৌকোটি গাছের কাছে। জেঠিমা কুলো থেকে ধানদুব্বাফুল নিয়ে ছিটিয়ে দিল গাছটিতে, শাখায়-পাতায় মাখিয়ে দিল উজ্জ্বল লাল তরল সিঁদুর। তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে প্রণাম করল অনেকণ ধরে। দেখাদেখি স্বল্পভাষী সরমাও তাই করল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম শুধু এই দুর্লভ দৃশ্য। কী মানত করল জেঠিমা জানি না, তবে দুটি বটের পাতা ছিঁড়ে ঘটির জলে ভিজিয়ে সেই জল আমাদের মাথায়, তাঁর নিজেরও মাথায় ছিটিয়ে দিল বিড়িবিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ে। কী মন্ত্র কৌতূহল থাকলেও একসময় তা মুছে গেছে সময়ের স্রোতে।
পুজো শেষে ফেরার পথে অদ্ভুত এক মায়াবী সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে ফিরলাম। আম, জাম, হিজল, জারুল, বাঁশ, বেতস, ডুমুর ইত্যকার গাছগাছালির জড়াজড়ি করা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসছিলাম বাড়ির দিকে তখন প্রচুর হলুদ, লাল, খয়েরি নানা রঙের ছোট-বড় ফড়িং, প্রজাপতি ওড়োওড়ি করছিল। প্রায় ব ডুবন্ত একটি মেদবহুল কাঁঠাল গাছে দেখলাম মৌমাছির জটলা গুনগুন গুঞ্জনরত মধুতে টইটুম্বুর একটি বড় আকারের মৌচাক ঘিরে। আর এক জায়গায় দেখলাম স্বচ্ছ জলে টকটকে লাল রঙের এক ঝাঁক পোনা নিয়ে ভেসে আছে বড় দুটি টাকি মাছ। পোনাগুলো একবার সুড় সুড় করে জলের তলে নেমে আবার ভেসে উঠছিল খেলাচ্ছলে। দারুণ লাগছিল দেখতে। সরমা বলল, ‘একটি লাল রাজা ফড়িং ধরে দাও না দাদাবাবু!’
আমি কয়েকবার নৌকোতে এসে বসা লাল রঙের রাজা ফড়িং ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একটিও ধরতে পারলাম না। যতবারই ধরার চেষ্টা করলাম ততবারই ব্যর্থ হলাম, সেই দৃশ্য দেখে মজা লাগছিল বলে খিল খিল করে হাসছিল সরমা অবিরাম। সবুজ জঙ্গলঘেরা জলগম্ভীর আবহ ভেঙে ফেলা সেই মায়াময় হাসি আজও যেন কানে বাজে কখনো কখনো।
আজও মনে পড়ে ফেরার আগের দিনের স্মৃতি। শনিবার, শনিপুজোর দিন, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল ফলে সন্ধেবেলা উঠোনের তুলসীতলে পুজোর বদলে ঘরেই অনুষ্ঠিত হল। মনটা খুব বিষণ্ন তাই অন্ধকারে চেয়ারে বসে ছিলাম জানালা দিয়ে প্রায় নিবুনিবু দিনের আলোর দিকে তাকিয়ে। শ্রাবণের কিছু ঝিরঝিরে বৃষ্টি কখন যে মনের আকাশে এসে ঝরতে শুরু করেছে জানি না। এমন সময় একটা ছায়া এসে দাঁড়ালো দরজার পাশে। অস্ফুট স্বরে বলল, ‘অন্ধকারে কী করছ দাদাবাবু?......সেদিন সকালে অমন করে হেসেছিলাম বলে তুমি কিছু মনে করোনি তো?’
সহসা আমার মনের মধ্যে বজ্রপাত হল যেন! দাঁড়িয়ে উঠে মনে মনে তার সরল প্রশ্নের উত্তরে বললাম, ‘সেই হাসিটা কান্নাও তো হতে পারে সরমা।’ তার ডান হাতের মুঠোতে কি যেন ধরে রাখা। বললাম, ‘তোমার ঐ হাতে কী?’
----‘তোমার জন্য পুজোর প্রসাদ।’
সেই হারিয়ে যাওয়া বর্ষার স্মৃতিভাসা জলে সরমার মুখ আজও পদ্মফুলের মতো ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। এ যেন এই জীবনের সঙ্গে অন্য এক জীবনের স্মৃতিময় দৃশ্যাবলির লুকোচুরি খেলা। হয়ত সেটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম প্রেম যার শুভসূচনার পুরোহিত ছিল আর কেউ নয়---গ্রামবাংলার বর্ষা। বর্ষা আজও আসে, মেঘ গুড়গুড় শব্দ তুলে ধেয়ে এসে দিগ্দিগন্তব্যাপী জলবতী কালো-ধুম্রধূসর রঙে ছেয়ে ফেলে, ঝাপসা করে দৃষ্টির কাচ, স্মৃতিরা ফিরে ফিরে আসে--------ফিরে আসে না শুধু সে।
(ওএস/এএস/এটিআর/ জুলাই ০৫, ২০১৪)
পাঠকের মতামত:
- গরমে আইস ফেসিয়ালে যে উপকার পাবেন
- মে দিবসের কবিতা
- টানা ৮ দফা কমার পর বাড়লো স্বর্ণের দাম
- জালাল মেলায় গান শুনে অন্ধ বাউল প্রদীপ পালের ভাগ্য বদলের উদ্যোগ
- কেন্দুয়ায় খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন
- শ্যামনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগে আওয়ামীলীগে ত্রিমুখী লড়াই
- বেলকুচিতে বোমা বিস্ফোরণ মামলার আসামি আবু তালেব গ্রেফতার
- বহিস্কারের পর বিএনপির প্রার্থী আরও বেড়েছে
- প্রার্থী হয়েছেন ভাই, প্রচারণায় সংসদ সদস্য
- বরিশালে গৃহবধূকে পিটিয়ে আহত
- সড়ক দুর্ঘটনায় শাহরাস্তির বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩
- বরিশালে প্রতিবন্ধী কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ২
- পাল্টাপাল্টি মামলায় আ.লীগের শতাধিক নেতাকর্মী আসামি, থমথমে গৌরনদী
- সাতক্ষীরা শহরের ফারাজানা ক্লিনিকে ভুল অপারেশনে প্রসূতির মৃত্যু
- বেলকুচিতে থানায় ঢুকে প্রার্থীর ওপর হামলার অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ ইসির
- ডিবি ও সাংবাদিক পরিচয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে আটক ৭
- বেলকুচিতে থানায় ঢুকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ওপর হামলা, ইন্জিনিয়ার আমিনুল শোকজ
- জুয়েলারি শিল্পে বিপ্লব ঘটাতে বাজুসের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান
- বোয়ালমারীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নির্বাচন স্থগিতের অভিযোগ
- ফুলপুরে ট্রলি-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক নিহত
- দেশের আলোচিত কিশোরী ইয়াসমিনের মায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু
- নিঃস্ব কামালের মুখে হাসি ফোটালেন মেয়র ও মানবিক মানুষ
- বিদেশে বসে টাকার বিনিময়ে পরকীয়া প্রেমিককে হত্যা
- ‘কাপ্তাই লেকের হারানো যৌবন ফিরিয়ে আনা হবে’
- পাংশাকে স্মার্ট উপজেলা করতে নিরলস কাজ করছেন ইউএনও জাফর সাদিক
- লংগদু গণহত্যা দিবস উপলক্ষে স্মরণ সভা
- শেখ হাসিনা: পঙ্কিল রাজনীতির পথ অতিক্রম
- কানাডার এশিয়ান হেরিটেজ মাস
- খনি শ্রমিকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত প্রয়োজন
- অসাধু জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের তালিকা করবে বাজুস
- সুদানে ক্ষুধার জ্বালায় ঘাস খাচ্ছে মানুষ
- নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা রবিবার
- নিরাপদ সড়কের দাবিতে নড়াইলে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত
- ‘সমৃদ্ধশালী ন্যায় বিচার ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে নাগরিক সচেতনতার বিকল্প নেই’
- কানাডায় শিখ নেতা হরদীপ হত্যাকাণ্ডে ৩ ভারতীয় গ্রেপ্তার
- সবজির বাজারে গরমের তাপ
- ‘ভোটারবিহীন নির্বাচনে আনন্দ নেই, সৌন্দর্য্য নেই’
- ঢাকাসহ ৫ বিভাগে ঝোড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টির আভাস
- চামড়াখাতে ন্যূনতম মজুরি ২২ হাজার ৭৭৬ টাকার প্রস্তাব সিপিডির
- কাপ্তাইয়ে চিৎমরম নদীর ঘাট পারাপারে দুর্ভোগ, সিঁড়ি বর্ধিতকরণ ও ছাউনি নির্মাণ দাবি এলাকাবাসীর
- ফরিদপুরের সিং পাড়ায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ৮ দিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত
- ফরিদপুর পৌরসভার একটি ইটের রাস্তা পাকা করার দাবিতে মানববন্ধন
- সালথায় মানবপাচার মামলায় এক নারী গ্রেপ্তার
- এক যুগ কাটিয়ে ডর্টমুন্ড ছাড়ছেন রয়েস
- রাজবাড়ী-ঢাকা রুটে ভাঙ্গা ও চন্দনা কমিউটার ট্রেনের উদ্বোধন
- পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো ভারত
- ১০ কোটির মাইলফলকে পরীমণি-সিয়ামের ‘তুই কি আমার হবি রে’
- আজ থেকে শুরু হচ্ছে ট্রেনের বাড়তি ভাড়া
- হেলিকপ্টারে আগুন, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন নায়ক দেব
- জিম্মি চুক্তিতে রাজি হতে হামাসকে ৭ দিনের সময় দিল ইসরায়েল
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- এবারও মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ফাঁদে শিক্ষার্থীরা
- এবারও মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ফাঁদে শিক্ষার্থীরা
- সিলেটের ভ্রমণ কাহিনী
- শুধু প্রভাবশালীদের পক্ষেই আইন!
- অম্ল-মধুর যন্ত্রণায় অপু বিশ্বাস
- লাইন ধরে খেতে হয় লিখনের জগা খিচুড়ি !
- আমার বোন শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি : চিনে নিন কে এই বরকত!
- 'ইতিহাসের ইতিহাস'
- ধনী হওয়ার আট কার্যকর উপায়
- মেয়ে পটানোর কৌশল!
- লক্ষাধিক রাখাইন জনগোষ্ঠী আড়াই হাজারে নেমে এসেছে
- উত্তরাধিকার ৭১ নিউজের নতুন যাত্রা ১ বৈশাখ
- লোভী মানুষ চেনার সহজ উপায়
- আমায় ক্ষমা কর পিতা : পর্ব ১৪'তোমার সহজাত উদারতা তোমাকে আকাশের সীমানায় উন্নীত করলেও তোমার ঘনিষ্ঠ অনেকের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ তোমার নৃশংস মৃত্যুর পথে কোনই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি'
- বাংলা বই পড়ার ওয়েবসাইট
- শাকিবের নায়িকা শ্রাবন্তী, অপুর নায়ক জিৎ
- মঠবাড়িয়ায় ৯ বছরের শিশুকে পাশবিক নির্যাতনের পর হত্যা
- হুমায়ূনের মৃত্যুর কারণ মদের পার্টি !
- দেশে ফিরছেন তারেকস্ত্রী জোবায়দা রহমান
- বোরকা পরা মেয়ের গণধর্ষণের ভিডিও নিয়ে সিলেটে তোলপাড়
- ইউটিউবে নায়লার আত্মপ্রকাশ
- নেপালের ভূমিকম্প প্রাকৃতিক নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি !
- বিএনপির আন্দোলন হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে !
-1.gif)


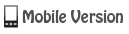








.jpg&w=60&h=50)




-1.jpg&w=60&h=50)













































