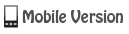একাত্তরের এক রজনী

যুথিকা বড়ুয়া
১৯৭১ সালের মার্চ মাস। মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন আমাদের পরাধীন মাতৃভূমি বাংলাদেশের কি ভয়াবহ, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তখন। গ্রামে-গঞ্জে শহরে চতুর্দিকে গনহত্যা, লুন্ঠন, মা -বোনের সম্ম্রমহানী, ধর্ষণ, যা আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কম-বেশী অবগত আছি। যখন প্রাণের দায়ে সাধারণ জনগণ নিজের মাতৃভূমি ও পৈত্রিক ভিটেবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে বেছে নিয়েছিল পলায়নের পথ।
শুনেছি, সেই সময় এক হতভাগ্য দরিদ্র কৃষকের পাঁচ বছরের শিশুপুত্র মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ধরে নেওয়া যাক, জনৈক কৃষকের নাম কেষ্টচরণ দাস। তিনি ছিলেন খেটে খাওয়া মানুষ। একজন সাধারণ মজদুর। কিন্তু দুঃখ-দৈনতা তাকে কখনো ঘায়েল করতে পারেনি। তার অসাধারণ মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস ছিল। বাপ-ঠাকুরদার আমলের স্বল্পায়তন জমিতে আনাচপাতির চাষ করতেন। থাকতেন খড়-খুটোর ছাউনি দেওয়া একটি ছোট্ট মাটির ঘরে। যেখানে ছিল রাজ্যের মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড়ের বসবাস। সামান্য বর্ষণে কেঁচো, সাপ-ব্যাঁঙ সব কিলবিল করতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবণতি ঘটলেও তাকে কখনো বিভ্রান্ত করতে পারেনি। কিন্তু রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র শিশু পুত্রকে চিরতরে হারিয়ে তিনি দিশাহীন হয়ে পড়েন। যেদিন পৈত্রিক ভিটেবাড়ি সহ চাষের জমি পরিত্যাগ করতে তাকে এতটুকু পীড়া দেয়নি, অনুশোচনাও হয়নি। বাস্তবের রূঢ়তা, সংকীর্ণতা, অমানবতা এবং হীনমন্যতার ক্ষোভে দুঃখে, শোকে স্ত্রী ও এগারো বছরের কিশোরী কন্যা রজনীর লাজ বাঁচাতে সর্বস্ব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। পুত্রশোক বুকে চেপে ভয়ে-আঁতঙ্কে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে চুপিচুপি গভীর বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাতারাতি যশোর হয়ে এসে পৌঁছায় বেনাপোল সীমান্তে। সেখান থেকে দিনের শেষে দিগন্তের কোলে আঁধার ঢলে পড়লে পূনরায় শুরু করেন যাত্রাভিযান। সীমান্তের কর্দমাক্ত ও কন্টকময় দুর্গমপথ পেরিয়ে ঊষার প্রথম আলোয় বনগাঁও হয়ে সরাসরি গিয়ে আশ্রয় নিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতের রিফিউজি ক্যাম্পে। কি নোংরা, ধূলোবালি ভরা দুর্গন্ধ তাদের গায়ের জামাকাপড়। রুক্ষশুক্ষ এলোকেশ। অবিশ্রান্ত পদযাত্রায় ও বিনিদ্র রজনী পোহায়ে ক্ষিদায় তৃষ্ণায় তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন মাটির তলদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে।
অগত্যা, সময়ের নিমর্মতা কাঁধে চেপে শুরু করেন তাদের নতুন জীবনধারা। বদলে গেল তাদের ধ্যান-ধারণা। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মসূচী। অচেনা অজানা জায়গা। নিত্য নতুন অপরিচিত মানুষের আনা গোনা। ভিন্ন মনোবৃত্তি। অনিয়ম বিশৃক্সক্ষল পরিবেশ। পদে পদে প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অপদস্থ, বিড়ম্বনা। যেখানকার পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানিয়ে চলা তাদের পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুস্কর। নিয়তি যাদের প্রতিনিয়ত উপহাস করে, পরিহাস করে, দুঃখ-দীনতা কখনো যাদের পিছুই ছাড়েনা, সেসব মানুষ সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকেই বা কেমন করে!
একদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রিফিউজি ক্যাম্পেই জীবনাবসান ঘটে কেষ্টচরণের। আর দুঃখের দহনে করুণ রোদনে জীবনপাত করতে রেখে গেলেন, স্ত্রী সুধারানী ও এগারো বছরের কিশোরী কন্যা রজনীকে। তখন ওর বাড়ন্ত শরীর। অপরিণত বয়সেই বাঁধ ভাঙ্গা যৌবনের ঢেউ যেন উপছে পড়তো ওর শরীরে। আর ঐ যৌবনই ছিল রজনীর অভিশাপ। বিপদ অবশ্যম্ভাবী। যা ও’ নিজেও কখনো জানতো না। প্রতিনিয়ত ক্ষুধার্ত হায়নার মতো লোভাতুর কামপ্রিয় পুরুষেরা ওকে ধাওয়া করতো। যখন ভোগের লালসায় নারী দেহের গন্ধে একজন ভোগ-বিলাসী পুরুষ মানুষের মনোবৃত্তিকে কলুষিত করে, অপবিত্র করে। অপকর্মের বীজ রোপণ করে। দূষীত হয় আমাদের সুশীলসমাজ। যখন বাধ্যতামূলকভাবে কতগুলি নীরিহ, অসহায়, সহজ সরল যুবতী মেয়েরা ছদ্মবেশী প্রতারকের প্রলোভনে বশ্যতার স্বীকার হয়ে পতিত হয়, অনিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তাহীন এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার গুহায়। যা আইনত অপরাধ এবং দন্ডনীয়।
কিন্তু এসব গ্রাহ্য করছে কে! এ তো আবহমানকালের মনুষ্য চরিত্রের চিরাচরিত একটি প্রধান বৈশিষ্ঠও বলা যায়। বিশেষতঃ যাদের অন্তরে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধটুকুই থাকেনা। রুচীবোধ থাকেনা, মানবিক মূল্যায়ন করেনা। যারা মান-মর্যাদা ও পাপ-পূন্যের ধার ধারে না। যার অভাবে মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার পরিবর্তে বন্যপশুর মতো অমানবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে তারা নিজেরাই হরণ করে বসে।
রজনী ছিল, অঁজপাড়া গাঁয়ের অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মেয়ে। বয়সের তুলনায় বিবেক-বুদ্ধি একেবারে ছিল না বললেই চলে! লোকজন দেখলে দাঁত বার করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকতো। যার শরীরের গড়ন আর চমকপ্রদ রূপের মুগ্ধ আর্কষণে ভ্রমরের মতো যৌবনের মধু শোষণ করতে উড়ে এসে গেঁঢ়ে বসেছিল, রিফিউজি ক্যাম্পেরই স্বেচ্ছাসেবক নামধারী এক তরুণ যুবক। যেদিন বিপন্ন সময়ের শিকার হয়ে রাতারাতি রিফিউজি ক্যাম্প ছেড়ে শহরের অন্যত্রে গা ঢাকা দিয়ে রজনীকে রক্ষা করেছিলেন ওর গর্ভধারিনী মাতা সুধারানী। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সভ্যসমাজে বাস করবার মতো যোগ্যতা তখন তাদের ছিলনা। না জানতো ভাষা, না জানতো ব্যবহার। শুদ্ধ বাংলাও ভালো বলতে পারতো না। কাপড়-চোপড়ও ঠিক মতো পড়তে জানতো না। বাড়ির বাইরে বের হলে আশেপাশের বখাটে ছেলেরা জটলা বেঁধে ওকে নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করতো, ঠাট্টা-তামাশা করতো। থাকতো গুদাম ঘরের মতো স্যাঁতসেঁতে জায়গায়। যে বাড়িতে মা-মেয়ে দুজনেই ঝি-কাজ করতো। দুইবেলা এঁটো বাসন মাজতো, মশলা বেটে দিতো, জামা-কাপড় কেঁচে দিতো। অবসরে কাগজের ঠোঁঙ্গা বানাতো। তাতে ক’পয়সাই বা আর উপার্জন হতো। ঘর ভাড়া দিয়ে দু’বেলা পেট ভরে অন্নও জুটতো না। বেশীর ভাগ উপবাসেই কাটাতে হতো।
কিন্তু বাইরের পৃথিবীকে যখন জানতে শিখলো, বুঝতে শিখলো, মানবাধিকারের দাবিতে মনুষ্যত্বের দাঁড়িপাল্লায় জীবনের মূল্যায়ন করতে শিখলো, রজনী তখন একুশ বছরের উজ্জ্বল সুদর্শণা পূর্ণ যুবতী। ক্রমাণ্বয়ে দুর্বিসহ জীবনের একটা সুরাহা ও নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিকশিত করবার এক অভিনব ইচ্ছা-আশা-আকাক্সক্ষায় ওকে ক্রমশ উৎসুক্য করে তোলে।
ক্রমে ক্রমে জীবনের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে সদ্য প্রস্ফূটিত ফুলের মতো রূপে, গুণে পারদর্শী হয়ে রজনী কখন যে চাঙ্গা হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুললো, পাড়া-পর্শী কেউ টের পেলনা। বিস্ময়ে সবাই অবাক। যেন এক অজ্ঞাত কূলশীল যুবতী মহিলা।
সকাল সন্ধ্যে দুইবলা মন্ত্রপাঠের মতো পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত বই “বাল্যশিক্ষা” গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করে যেটুকু বিদ্যা অর্জন করেছিল, তাতে শুধু বেশভূষাই নয়, জীবনধারা, চালচলন, কথা বলার আদপ-কায়দা এমনভাবে রপ্ত করে নিয়েছিল, সামাজিক রীতি-নীতির বৈষম্যতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও বেমালুম বদলে গিয়েছিল। যা স্বপ্নেরও অতীত। অবলীলায় সমগ্র অস্থি-মজ্জা ও হৃদয়ের কোণে ঘুমিয়ে থাকা চমকপ্রদ প্রতিভার দক্ষতায় রজনী হাসিল করে নিয়েছিল, সভ্যসমাজে বাস করবার পূর্ণ অধিকার। খুঁজে পায়, জীবনের অস্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, বেঁচে থাকার প্রকৃত অর্থ। সেই সঙ্গে চোখের আলোয় দেখেছিল, অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের একফালি খুশীর ঝলক। জাগ্রত হয়, প্রখর সংগ্রামী মনোভাব। মানবিক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ। বর্দ্ধিত হয়, নিজের উপর ভরসা, আত্মবিশ্বাস।
যেদিন দিগি¦বিজয়ের মশাল তুলে চারদেওয়ালের বদ্ধজীবন থেকে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে এসে ভুলে গিয়েছিল, ওর শৈশব ও কৈশোরের ভাগ্যবিড়ম্বণার চরম দারিদ্রপীড়িত গ্রাম্য জীবনের দুঃখ দীনতার কথা। ভুলে গিয়েছিল, সদ্য স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং পৃথিবীর মানচিত্রে অন্তর্ভূক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ ও নিজের মাতৃভূমিকে। যার সম্মুখে ছিল, এক সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার স্বপ্ন ও আশাতীত সফলতা। ক্রমে ক্রমে যে দেশটি ধনধান্যে পুস্পে ভরে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল, সুখ-সমৃদ্ধশালী এবং আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন বাংলাদেশ।
তা হোক, তবু স্বদেশে আর ফিরে যাবেনা রজনী। মাতৃভূমি কখনো সে স্পর্শ করবে না। সেখানে কেইবা আছে ওর? ছিল একমাত্র ছোটভাই, ওকে ফিরে পাবে কোনদিন? কেউ কি পারবে ওকে ফিরিয়ে দিতে?
চেয়েছিল, নিজের সততা ও কর্ম দক্ষতায় সাবলম্বী হতে, নিজস্ব মাটিতে মাথা উঁচু করে শক্তপায়ে দাঁড়াতে। চেয়েছিল, সুশীলসমাজে অবস্থানকারী আর পাঁচজনের মতো পূর্ণ মান -মর্যাদায় ও সসম্মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মায়ের দুঃখ চিরতরে মুছে দিতে।
কিন্তু বিধি বাম। তা আর বাস্তবায়ীত হয়নি। রজনী পারেনি জীবনকে নিজের ইচ্ছে মতো নতুন রূপে, নতুন রঙে সাজাতে। পারেনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, ওর জীবনের একান্ত কামনা-বাসনাগুলিকে যথাযথ পূরণ করতে।
অবলীলায় মায়ের একান্ত ইচ্ছা ও পীড়াপীড়িতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আনন্দময় জীবনকে উপেক্ষা করে স্বদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল রজনী। ভেবেছিল, দেশে ফেলে আসা স্বল্পবিস্তর জমিটুকু ওরা ফিরে পাবে। ফিরে পাবে নিজের মাতৃভূমিকে। ফিরে পাবে নিজের দেশবাসীকে। যেখানে শেষ করে এসেছিল সেখান থেকেই আবার শুরু হবে ওদের নতুন জীবন।
কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খন্ডাবে কে! পূর্বপরিকল্পিত অনুযায়ী নির্ধারিত দিনের পাতাঝড়া নির্জন দূপুরে যথারীতি যাত্রা শুরু করলে পরদিন সূর্য্যদয়ের পূর্বেই চিরতরে নিভে গেল রজনীর অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল আলোর শিখা।
নব জীবনের আনন্দ-বেদনার অভিজ্ঞতা সাথে নিয়ে রজনী যাত্রা শুরু করেছিল, একটি নতুন দিনের, নতুন সূর্য্যরে প্রত্যাশায়। স্মৃতির উপত্যকায় বসে স্বদেশের শষ্য-শ্যামল গাঁয়ের সবুজ বনভূমি আর ধানভাঙ্গার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়েছিল, রজনী টেরই পায়নি। বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছাতেই একটি রেস্তোরার পাশে ওদের বিশাল যাত্রীবাহী বাসটি হঠাৎ বিনা নোটিশে থেমে যায়। চারদিক জনশূন্য। নিঝুম পরিবেশ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার বিজলীবাতিগুলিও নিভু নিভু প্রায়। স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছিল না। মাঝে মধ্যে দু-একটা গাড়ি দ্রুত গতীতে পাস করে যাচ্ছিল। সেই সময় ক’য়েকজন যাত্রীর সাথে রজনীর মা সুধারানী গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন। গিয়েছিলেন কিছু খাবার কিনে আনতে। যখন দুষ্টচক্রের শিকার হয়ে চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মা-মেয়ে দুজনেই। যেন তীরে এসে তড়ী ডুবে যাবার মতো অবস্থা। যা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান। যাদুমন্ত্রের মতো চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল রজনী।
উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় সুধারানীর তখন শোচনীয় অবস্থা। উন্মাদ-উ™£ান্ত হয়ে একে একে গাড়ির প্রতিটি সীটে হন্যে হয়ে নজর বুলিয়ে দ্যাখে, রজনী কোথাও নেই। কিন্তু ওর সীটে পড়ে থাকা হ্যান্ডব্যাগটা চোখে পড়তেই ভাবলো, নিশ্চয়ই বাইরে গিয়েছে। মুক্ত বাতাসে দম নিচ্ছে। এসে পড়বে ক্ষণ।
কিন্তু কোথায় রজনী? গাড়ির জানালা দিয়ে গলা টেনে দেখতেই বুকটা ধড়াস ওঠে। ধূ ধূ মরুভূমির মতো শূন্য নিবিড় নির্জন ময়দান। আশে-পাশে একটি প্রাণীও কোথাও নেই। মনে হচ্ছে যেন, কোনো বিপদসংকেত অপেক্ষায় করে আছে।
গাড়ি পুনরায় যাত্রা শুরু করলে সুধারানী চিৎকার করে ওঠে,-‘গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও, আমার জনী উঠে নাই গাড়িতে, গাড়ি থামাও!’
রজনীর ব্যাগটা হাতে নিয়ে দ্যাখে, ব্যাগের মধ্যে একটা কাগজের টুকরো। তাতে লেখা,-‘ছোড়ির তালাশ করবি, খালাশ করে দেবো!’
মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়লো সুধারানীর। বুক চাপড়িয়ে চাপা আর্তনাদ করে ওঠে,-‘হে ভগবান! এ আবার কোণ্ সর্বণাশ ঘনিয়ে এলো!’
কারো মুখে কথা নেই। গাড়ির যাত্রিরা সবাই জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ভয়ে-আতঙ্কে সুধারানী র্থর্থ করে কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে যায়। রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠস্বর। জমে হীম হয়ে যায় সারাশরীর। কি কৈফেয়ৎ দেবে সে নিজেকে? কি শান্তনা দেবে নিজেকে? রজনী তো আসতেই চাইছিল না। ওর ইচ্ছাকে উপক্ষো করে, ওর সাথে বিরোধীতা করে একরকম জবরদস্তীই দেশে ফিরে আসতে ওকে বাধ্য করেছিল। রজনী বাঁচতে চেয়েছিল। চেয়েছিল, জীবনকে নিজের মতো করে পরিচালনা করতে। জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে। এ কি সর্বণাশ হলো রজনীর! ওকে কোণ্ নরকে ঠেলে দিলো! কি হবে এর পরিণাম? রজনীকে ফিরে পাবে কোনদিন? চোখের দেখাও কি আর কোনদিন দেখতে পাবে? ওইতো ছিল জীবনের একমাত্র সাহারা। জীবনের শেষ সম্বল। বেঁচে থাকার শক্তি, প্রেরণা। সুধারানী বাঁচবে কি নিয়ে? কাকে নিয়ে? যাকে শান্তনা দেবার মতোও কেউ ছিল না।
ততক্ষণে সব শেষ। সর্বণাশের কিছ্ইু আর অবশিষ্ঠ নেই রজনীর। দুস্কৃতকারীরাই বিষাক্ত ক্যামিকেলের তীব্র ঘ্রাণে সংজ্ঞাহীণ করতে সক্ষম হলে ওকে সরাসরি অন্যত্রে চালান করে দেয়। কিন্তু জলজ্যান্ত একটা যুবতী মেয়ে মন্ত্রের মতো গাড়ি থেকে উধাও হয়ে রাতারাতি গেল কোথায়? ওকে কোথায় নিয়ে গেল? কে নিয়ে গেল? কারা নিয়ে গেল? কেন নিয়ে গেল?
অশ্রুপ্লাবনে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে বাক্যাহত সুধারানী পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে থাকে। চেয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে। কে দেবে এসব প্রশ্নের উত্তর? কে নেবে এসবের দায়িত্ব? কে দেবে তাকে সাহারা?
এ যে চতুর ধূর্ত, দুষ্ট লোকের চক্রান্ত তা বুঝতে দেরী হলোনা সুধারানীর। কিন্তু তখন সে বড় অসহায়, একেলা নিঃসঙ্গ, সম্বলহীন, আশ্রয়হীন, গন্তব্যহীন পথের যাত্রী। তিনি যে কোথায় কোণ্ মোহনায় গিয়ে আঁটকে ছিলেন, কে জানে!
পরবর্তীতে গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে, একদল নির্দয়ী স্বার্থাণ্বেষী মুখোশধারী দেশদ্রোহী বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে সীমান্তের গুপ্তচরের সহায়তায় রজনীকে সঁপে দিয়েছে নারী পিপাসু ব্যভিচারী পাষন্ডদের হাতে। কেউ বলে,-‘আবর দেশের রাজা-বাদশাদের হাতে।’
যেখানে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মাথাকূটে কেঁদে মরে গেলেও কেউ শুনবে না রজনীর আর্তনাদ, অনুনয়-বিনয়, আকুতি-মিনতি। যার কোনো খোঁজখবর আর পাওয়া যায়নি।
(যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী )
পাঠকের মতামত:
- ডুমাইনের ঘটনার দোষীদের বিচারের দাবিতে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের শান্তি মিছিল
- ‘লাল কার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে বেইমানদের শিক্ষা দেবে জনগণ’
- ৩ দিনব্যাপী জালাল মেলার উদ্বোধন, দর্শক ও ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়
- নড়াইলে মাদক মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
- অনির্দিষ্টকালের জন্য চুয়েট বন্ধ ঘোষণা
- ২৮ এপ্রিল খুলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শনিবারও চলবে ক্লাস
- ধামরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রফিকুল আলম রকেট আর নেই
- বাগেরহাটে ডায়রিয়ার প্রকোপ, স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু
- নড়াইলে নবগঙ্গা নদী থেকে প্রতিবন্ধী যুবকের মরদেহ উদ্ধার
- গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সাব স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
- টাঙ্গাইলে পচা মাংস বিক্রি করায় জরিমানা
- ‘এক শ্রেণিতে ৫৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি নয়’
- টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় ঈদগাঁ মাঠে ইস্তিকার নামাজ আদায়
- ‘মানবাধিকার নিয়ে বাংলাদেশের অর্জন স্বীকার করেনি যুক্তরাষ্ট্র’
- টাঙ্গাইলে আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস উদযাপন
- বাগেরহাটে বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার নামাজ আদায়
- মহম্মদপুরে সড়কে দুর্ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের মৃত্যু
- বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে অঝোরে কাঁদলেন মুসুল্লীরা
- সার্বজনীন পেনশন স্কিমের রেজিস্ট্রেশন বুথ উদ্বোধন গৌরনদীতে
- মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ভিপি মিজান সহ ১৪ নেতাকর্মী কারাগারে
- সাজেকে নিহত ঈশ্বরগঞ্জের ৫ শ্রমিকের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম
- গৌরীপুরে ৩ দফা দাবীতে কৃষক সমিতির স্মারকলিপি প্রদান
- গাইবান্ধায় বৃষ্টির জন্য মুসল্লিদের নামাজ আদায়
- দিনাজপুরে নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে পরিকল্পনা কর্মশালা
- কুষ্টিয়ায় নারী চিকিৎসককে হয়রানি, যুবকের কারাদণ্ড
- ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
- বঙ্গোপসাগরে কার্গো জাহাজডুবি, ভাসছেন ১২ নাবিক
- পার্বত্য জেলার এনজিওর বাজেট জানাতে হবে জেলা পরিষদকে
- মন্ত্রী-এমপির আত্মীয়ের কারণে জনগণ জিম্মি: রিজভী
- টিসিবির জন্য কেনা হবে সাড়ে ৬১ কোটি টাকার মসুর ডাল
- মাগুরায় বৃষ্টির জন্য নামাজ ও দোয়া প্রার্থনা
- নড়াইলে বৃষ্টির জন্য ইস্তিস্কার নামাজ
- শয্যা সংকটে ফ্লোরসহ এক বেডে থাকছে দুই থেকে তিন শিশু
- বেনজীর ও তার পরিবারের নগদ অর্থের তথ্য চেয়ে বিএফআইইউতে দুদকের চিঠি
- প্রমাণে ব্যর্থ রাষ্ট্রপক্ষ, অস্ত্র মামলায় খালাস ‘গোল্ডেন মনির’
- জিআই স্বীকৃতির সঙ্গে পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে: শিল্পমন্ত্রী
- যশোর পৌরসভায় তাপদাহে চাহিদার তুলনায় কমেছে পানি সরবরাহ
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন
- নড়াইলে খুনের ঘটনার ৫ মাস পরেও থামছে না বাড়িঘর ভাঙচুর-লুটপাট, আতঙ্কে গ্রামছাড়া মানুষ
- পাংশায় মাদক ব্যবসায়ীসহ পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার
- সোনার দাম আরও কমলো, ভরি ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৬১ টাকা
- চলতি বছর থাইল্যান্ডে হিটস্ট্রোকে ৩০ জনের মৃত্যু
- নিরাপদ সড়কের প্রয়োজনীয়তা
- তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তির আশায় সরিষাবাড়ীতে বিশেষ নামাজ আদায়
- ফরিদপুরে বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার নামাজ আদায়
- টঙ্গীবাড়িতে ভাই-ভাতিজার হাতে ভাই খুন
- পুতুল পোড়াতে গিয়ে আগুনে দগ্ধ শিশু রিয়ার মৃত্যু
- বড়াইগ্রামে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ভ্যান চালকের মৃত্যু
- বহিস্কার করেও ভোটমুখী নেতাদের বাগে আনতে পারছে না বিএনপি
- ফুলপুরে ট্রাক চাপায় নিহত ১
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- এবারও মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ফাঁদে শিক্ষার্থীরা
- এবারও মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ফাঁদে শিক্ষার্থীরা
- সিলেটের ভ্রমণ কাহিনী
- শুধু প্রভাবশালীদের পক্ষেই আইন!
- অম্ল-মধুর যন্ত্রণায় অপু বিশ্বাস
- লাইন ধরে খেতে হয় লিখনের জগা খিচুড়ি !
- আমার বোন শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি : চিনে নিন কে এই বরকত!
- 'ইতিহাসের ইতিহাস'
- ধনী হওয়ার আট কার্যকর উপায়
- মেয়ে পটানোর কৌশল!
- লক্ষাধিক রাখাইন জনগোষ্ঠী আড়াই হাজারে নেমে এসেছে
- উত্তরাধিকার ৭১ নিউজের নতুন যাত্রা ১ বৈশাখ
- লোভী মানুষ চেনার সহজ উপায়
- আমায় ক্ষমা কর পিতা : পর্ব ১৪'তোমার সহজাত উদারতা তোমাকে আকাশের সীমানায় উন্নীত করলেও তোমার ঘনিষ্ঠ অনেকের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ তোমার নৃশংস মৃত্যুর পথে কোনই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি'
- বাংলা বই পড়ার ওয়েবসাইট
- শাকিবের নায়িকা শ্রাবন্তী, অপুর নায়ক জিৎ
- মঠবাড়িয়ায় ৯ বছরের শিশুকে পাশবিক নির্যাতনের পর হত্যা
- হুমায়ূনের মৃত্যুর কারণ মদের পার্টি !
- দেশে ফিরছেন তারেকস্ত্রী জোবায়দা রহমান
- বোরকা পরা মেয়ের গণধর্ষণের ভিডিও নিয়ে সিলেটে তোলপাড়
- ইউটিউবে নায়লার আত্মপ্রকাশ
- নেপালের ভূমিকম্প প্রাকৃতিক নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি !
- বিএনপির আন্দোলন হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে !
-1.gif)