নির্বাচন: গণতন্ত্র না গণ-দূরত্ব?

মীর আব্দুল আলীম
বাংলাদেশ আজ আরেকটি সঙ্কটজনক ভোটের দ্বারপ্রান্তে। দেশের রাজনীতি যেন এখন এক দিকহারা জলযানের মতো-সমুদ্র আছে, ঢেউ আছে, খোলা আকাশও আছে-কিন্তু নেই দিকদর্শন। সেই ঢেউয়ের নাম আজ “নির্বাচন”। কিন্তু এই নির্বাচন কার জন্য? কার স্বার্থে? এবং কোন কাঠামোর ভিতর দাঁড়িয়ে? এই প্রশ্নগুলো এখন আর কেবল রাজনৈতিক তর্ক নয়, বরং জাতিগত অস্তিত্বের গভীর সংকেত।
গণতন্ত্রের কথা বলে যারা নির্বাচন চাইছেন, তারা বলছেন-“ভোটাধিকারই গণতন্ত্রের প্রাণ, একে উপেক্ষা করা মানেই জনগণকে অস্বীকার করা।” আবার আরেকটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ধারা বলছে, “এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নির্বাচন মানেই পুরনো মুখ, পুরনো নাটক, পুরনো বঞ্চনা।” এ দ্বন্দ্ব এখন কেবল পথ বেছে নেওয়ার দ্বিধা নয়, বরং একটি সিস্টেম পরিবর্তনের ডাক। যেখানে স্পষ্টভাবে উঠে আসছে-প্রতিনিধিত্বের নতুন রূপ, অর্থাৎ Proportional Representation বা আনুপাতিক ভোট পদ্ধতি। জাতীয় সরকার হোক বা পিআর পদ্ধতি, সবই তখনই অর্থবহ, যদি তার পেছনে থাকে জনগণের ইচ্ছা ও সর্বদলীয় সম্মতি। নচেৎ এগুলো কেবল স্লোগান বা ছলচাতুরী হয়ে থাকবে। ভোট কেবল ভোট না-এটা হলো দেশের ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণ। তাই গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে সংযমী, সংলাপমুখী এবং সর্বোপরি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে। নইলে সামনে যে অন্ধকার, তা শুধু রাজনীতির জন্য নয়-গোটা জাতির জন্যই হুমকিস্বরূপ।
বর্তমান ব্যবস্থায়, যেখানে মাত্র ৩০-৩৫ শতাংশ ভোট পেলেও একটি দল সংসদের ৭০-৮০ শতাংশ আসন পায়, সেখানে বিরোধী দলগুলোর ভোট এক প্রকার অপচয় হয়ে যায়। ফলে সরকার হয়ে ওঠে অপ্রতিনিধিত্বমূলক। পিআর পদ্ধতির দাবি এ কারণেই জোরালো—কারণ এতে ভোটের অনুপাতেই আসন বণ্টিত হয়, ফলে সবাই অংশ নেয়, এবং কোয়ালিশনের মাধ্যমে একক আধিপত্যের সংস্কৃতি ভেঙে নতুন রাজনৈতিক ভারসাম্য গড়ে ওঠে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বদলে কোয়ালিশন সরকার মানে প্রতিনিয়ত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ-জবাবদিহিতার অভ্যাস গড়ে ওঠা। তবেই তো জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি তৈরি হয়। কোয়ালিশনের মানে এই নয় যে সরকার দুর্বল হবে; বরং এর অর্থ—কোনো একক গোষ্ঠী নয়, বিভিন্ন মতের ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান। এটাই পরিণত গণতন্ত্রের চিহ্ন।
তাই প্রশ্নটি এখন শুধু “নির্বাচন কবে”তা নয়। বরং কী ধরনের নির্বাচন, কী ধরনের কাঠামো, এবং কোন প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে সেই নির্বাচন হবে? এটি ঠিক যে, নির্বাচন একটি রাষ্ট্রের গন্তব্য নয়-তবে এটি সেই পথের দিকচিহ্ন। যদি সে পথই ভুল হয়, কিংবা যদি সেই পথের মানচিত্র তৈরিই হয় একতরফাভাবে-তাহলে যে গন্তব্যেই পৌঁছানো হোক, তা হবে রাষ্ট্রীয় শ্বাসরুদ্ধতা ও আরেকটি রাজনৈতিক অচলাবস্থার নামমাত্র। তাই আজ নির্বাচন নয়, আমাদের দরকার বিশ্বাসযোগ্য কাঠামো, অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি, এবং সবার অংশগ্রহণের ভিত্তি। নইলে-আবারও এক দলের প্রাসাদে গড়া হবে গণতন্ত্রের প্রতিমূর্তি, আর জনগণ দাঁড়িয়ে থাকবে প্রাচীরের ওপারে—তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু ঠাঁই পাবে না।
রাজনৈতিক দলগুলো গলা উঁচিয়ে বলছে- “নির্বাচনই একমাত্র পথ, একমাত্র সমাধান।” তাদের যুক্তি-গণতন্ত্রের চাকা সচল রাখতে হলে জনগণের ভোটাধিকারকে সামনে আনতেই হবে। অন্যদিকে আরেকটি শক্ত অবস্থান: অনন্তবর্তীকালনি ইউনুস সরকার বলছে-“এই রাষ্ট্র কাঠামোতেই যদি নির্বাচন হয়, তবে ফল হবে পূর্বের পুনরাবৃত্তি মাত্র। আগে চাই গভীর রাষ্ট্র সংস্কার, তারপরই হতে পারে একটি অর্থবহ নির্বাচন।” এ নিয়ে চারদিকে প্রশ্ন, উদ্বেগ আর সংশয়ের ছায়া। যে পথেই দেশ যাক, তার প্রান্তে যদি না থাকে জনগণের আস্থা, ন্যায়বিচার আর জবাবদিহি-তবে সে পথ হয়তো আরেকটি রাজনৈতিক যাত্রাবিরতির নাম হবে, সমাধানের নয়।
সময়ের ঢেউ আজ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। চারদিক থেকে যে শব্দ ভেসে আসছে, তা কেবলই সংঘাত, দাবি আর বিপরীত মতের গুঞ্জন। একদিকে দেশের প্রথাগত রাজনৈতিক শক্তিগুলো বলছে- “সমাধান একটাই-নির্বাচন। এই পথেই জনগণ রায় দেবে, দেশ পাবে নেতৃত্ব, রাষ্ট্র পাবে গতি।” তারা যুক্তি দিচ্ছে, নির্বাচন ছাড়া আর কোনো পদ্ধতিই গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সংহত করতে পারে না। গণতন্ত্র মানে ভোট, আর ভোট মানেই নির্বাচন-এটাই তাদের অবস্থান। অন্যদিকে, এক নতুন ভাবনার ধারা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। অনন্তবর্তীকালনি ইউনুস সরকারসহ একটি অংশ বলছে, “রাষ্ট্র যদি ভাঙা, দুর্বল ও বিকলাঙ্গ হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে কোনো প্রকৃত নির্বাচনই সম্ভব নয়। আগে চাই মৌলিক রাষ্ট্র সংস্কার-প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, আর তারপরই হতে পারে সত্যিকারের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন।”
এই দ্বিমুখী স্রোতের মাঝখানে আজ দুলছে রাষ্ট্রের নৌকা। মনে হচ্ছে, এক অনির্ধারিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান এক ক্লান্ত জাতি। সরকার ও বিরোধী পক্ষের টানাপোড়েন, প্রশাসনিক স্তরে দ্বিধা, বিচারব্যবস্থায় প্রশ্নবিদ্ধতা এবং সাধারণ জনগণের মাঝে ক্রমবর্ধমান হতাশা-সব মিলে এক দোলাচলপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কেউ জানে না-এই অস্থিরতা কোথায় গিয়ে থামবে, অথবা আদৌ কোনো সমাধানে পৌঁছানো যাবে কিনা। মানুষ আজ এক নিরুত্তর প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে-এ দেশ যাবে কোন দিকে? সামনে নির্বাচন নামক পথ থাকলেও, তার পাশে দেখা দিচ্ছে সংস্কার নামক গভীর খাদ। কেউ চায় চটজলদি ভোট, কেউ চায় মূলভিত্তির শুদ্ধি। কিন্তু এর মাঝেই হারিয়ে যাচ্ছে জনগণের আশা, তাদের আস্থার বিন্দু বিন্দু জলরেখা। রাষ্ট্র যেন আজ এক অস্পষ্ট ছন্দে দুলছে-কখনো উত্তাল, কখনো স্তব্ধ, কখনো বিক্ষুব্ধ। অথচ প্রশ্ন একটাই-এই দুলুনি যদি চলে দীর্ঘদিন, তবে কোথায় গিয়ে ঠেকবে এই জাতির ভবিষ্যৎ? সমাধান কি আদৌ আছে, নাকি কেবলই অনিশ্চয়তার অসীম চক্রে ঘুরপাক খাবে ইতিহাস?
‘অনন্তবর্তীকাল’ নামেই সংকেত? সরকারের ধরনেই সংকেত রয়েছে-কোনো স্থায়িত্ব নয়, বরং অনির্দিষ্ট কালের এক ধোঁয়াশা। ‘অন্তর্বর্তীকালীন’ শব্দের ধারণাটি সাধারণত সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত সরকারকে বোঝায়, যার মূল কাজ হলো সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন। কিন্তু ইউনুস সরকারের ‘অনন্তবর্তীকাল’ নামক ছায়া-পরিচয় বাস্তবে একটি সীমাহীন শাসনের ইঙ্গিত দেয়। এই সরকার নিজের মেয়াদ নির্ধারণে স্বচ্ছ নয়, বরং কখনো ‘স্থিতিশীলতা’, কখনো ‘প্রশাসনিক সংস্কার’, কখনো ‘বিরোধীদের অযোগ্যতা’কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে সময় পার করছে।
নির্বাচন অনিশ্চয়তা, রোডম্যাপ নেই- সরকার বারবার বলছে-২০২৬ সালের মধ্যে নির্বাচন হবে। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ নেই। নির্বাচন কমিশন এখনো পূর্ণ ক্ষমতায় কার্যকর নয়, কমিশনের গঠন নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিরোধীরা বলছে, সরকার যদি নির্বাচন আয়োজনেই আন্তরিক হয়, তাহলে কেন নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করা হচ্ছে না? এই অনিশ্চয়তা জনগণের আস্থাকে নষ্ট করছে এবং রাজনৈতিক উত্তেজনাকে দীর্ঘায়িত করছে। সংস্কারের নামে সময়ক্ষেপণ? সরকার একটি রাষ্ট্রপুনর্গঠন কমিশন গঠন করেছে, যার মূল কাজ ছিল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সংস্কার। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরও তারা কোনো বাস্তবমুখী সুপারিশ দিতে পারেনি। কিছুটা বিমূর্ত ভাষায় বলা হচ্ছে-”ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সংস্কার চলবে।” প্রশ্ন হলো-ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাম করে কি বর্তমান প্রজন্মকে গণতন্ত্রহীন রাখা হচ্ছে? বিরোধীরা এটিকে একটি ‘ধীর গতি কৌশল’ বলেই মনে করছে।
রাজনৈতিক সংলাপের যেন অপমৃত্যু না হয় এদিকে সবাইকে খেয়াল রাথতে হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংলাপ একটি রাষ্ট্রীয় সুরাহার প্রথম ধাপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, আর তা নিশ্চিত করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়া অত্যাবশ্যক। তাই ‘সহনশীলতার শর্ত’ যুক্ত করে বারবার সংলাপ আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে মতবিরোধের অবসান ঘটে এবং একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে, তাতে আন্তবর্তীকালীন (অন্তর্বর্তীকালীন) সরকারের ধারণা নিয়ে ধারাবাহিক সংলাপ চালিয়ে যাওয়া সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয়। এই ধরনের সংলাপ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব কমাতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পথ তৈরি করে। একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত বা সংঘাত নয়, বরং আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য দূর করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনই হতে পারে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার প্রধান ভিত্তি। তাই এখনই সময়, সংলাপকে কেন্দ্র করে সহনশীলতা ও বাস্তবতার আলোকে এগিয়ে যাওয়ার।
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ভূমিকা যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতীক হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব চিত্র অনেকটাই বিপরীত। সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডে এক ধরনের অস্পষ্টতা ও দোদুল্যমানতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা শুধু জনমনে সংশয়ই তৈরি করছে না, বরং দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর আস্থার সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে। ইসি বারবার বলছে ‘আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি’-কিন্তু তাদের কথায় নেই কোনো সুস্পষ্ট সময়সীমা, নেই একটি শক্তিশালী রোডম্যাপ। ফলে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই প্রশ্ন উঠছে: কমিশন আসলে কার জন্য, কার ইচ্ছায় ও নির্দেশে কাজ করছে? ইসির কর্মকাণ্ডে যদি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার বদলে কারো প্রতি আনুগত্যের ছাপ পাওয়া যায়, তাহলে গণতান্ত্রিক কাঠামো মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়ে। নির্বাচন কমিশন যদি সরকারের সংকেতে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহলে নির্বাচনের প্রকৃত স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না।
এটাও সত্য নির্বাচনপূর্ব সংস্কার ছাড়া একটি গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব নয়- এটি আজ সর্বজনবিদিত ও বাস্তবভিত্তিক সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো-সংস্কার হবে কীভাবে, কাদের নিয়ে, কতদূর পর্যন্ত, এবং কত দ্রুত? সরকার বলছে, তারা একটি আধুনিক, উন্নয়নমুখী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পথে রয়েছে। এই ভিত্তিগুলো গড়তে হলে প্রয়োজন নির্বাচনপূর্ব কাঠামোগত সংস্কার-যা শুধু সময়ের দাবি নয়, বরং গণতন্ত্র বাঁচানোর জরুরি শর্ত।
অবশ্য এ সংস্কার প্রশ্নে সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা নেই। সংস্কারের নামে ‘দেখনদারি’ বা সময়ক্ষেপণ করলে তা হবে প্রতারণার শামিল। কাগজে-কলমে কিছু সংশোধন করে অথবা নামমাত্র পরিবর্তন দেখিয়ে মূল সমস্যাগুলো আড়াল করলে নির্বাচন ব্যবস্থা আরও দুর্বল ও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সংস্কার হতে হবে কার্যকর, বাস্তবভিত্তিক এবং সর্বপক্ষের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে-যাতে সব রাজনৈতিক শক্তি নিজেকে নির্বাচনী ব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে।
বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য জরুরি কয়েকটি মূল সংস্কার হচ্ছে: নিরপেক্ষ ও সাহসী নির্বাচন কমিশন, প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ, সেনা মোতায়েনসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর স্বাধীন ভূমিকা, নিরপেক্ষ তদারকি ও পর্যবেক্ষণ, এবং নির্বাচনী সহিংসতা প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ। এসব সংস্কার না হলে জনগণের আস্থা ফিরবে না, রাজনৈতিক সংঘাত বাড়বে, এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। অতএব, নির্বাচনপূর্ব সংস্কার কোনো বিলাসিতা নয়-এটি সময়ের দাবি, রাষ্ট্র ও সমাজের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। সংস্কারের নামে কালক্ষেপণ না করে এখনই সাহসী ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, নইলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।
বাংলাদেশ এখন এক সংবেদনশীল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সামনে আছে নির্বাচন, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রশ্ন-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোবে? রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত এখন ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং দেশ ও জনগণের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দায়িত্বশীল আচরণ করা। একটি গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও সময়নির্ধারিত নির্বাচনী রূপরেখা তৈরি না হলে যে বিশৃঙ্খলা ও হতাশা সামনে অপেক্ষা করছে, তা কেবল গণতন্ত্র নয়-সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই ‘অনন্তবর্তীকাল’ যেন অনির্দিষ্টতার প্রতীক না হয়ে ওঠে, বরং তা হোক একটি বাস্তবমুখী রাজনৈতিক সমঝোতার সূচনা। যদি সরকার গা-ছাড়া মনোভাব দেখায় এবং রাজনৈতিক দল কৌশলহীন আন্দোলনে লিপ্ত হয়, তাহলে এ দেশ শুধু রাজনৈতিক সংকটে নয়-গৃহসংঘাত, অর্থনৈতিক ধস এবং আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকিতেও পড়বে। এখনই সময়-সকল পক্ষের জন্য আত্মজিজ্ঞাসার, আলাপ-আলোচনার টেবিলে ফেরার, এবং জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার। এই সংকটে জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্বের। তারা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাদের কখনই ক্ষমা করবে না।
জানি নির্বাচন হবে, তবু প্রশ্ন রয়েই যায়: এই ভোট কার জন্য? কে পাবে কতটুকু জায়গা, আর কতটুকু ছলনা থাকবে তার পেছনে? বাংলাদেশের রাজনীতি আজ এক অদ্ভুত অচলায়তনে বন্দি। নির্বাচন ঘিরে দলগুলো মুখর, অথচ জনমনে সংশয় কাটছে না। ভোট হবে ঠিকই-কিন্তু সেই ভোট কি আগের মতই? ফল কি আবারও একতরফা? নাকি এবার বদলাবে পদ্ধতি, বদলাবে কাঠামো? এক দল বলছে, “ভোটেই মুক্তি”, আরেক পক্ষ বলছে, “এই কাঠামোতে ভোট মানেই নাটকের রিপিট টেলিকাস্ট!” এ অবস্থায় জোরালো হচ্ছে আনুপাতিক ভোটপদ্ধতির (চজ) দাবি। যেখানে যে দল যত ভোট পাবে, আসন পাবে ততটাই—তা হলে আর ভোট হারানোর ভয় থাকবে না, জনগণের রায়ও হবে স্পষ্ট। আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বদলে যদি আসে কোয়ালিশন সরকার-তাহলে রাজনীতি হবে আলোচনার, একচ্ছত্র দখলের নয়। হয়তো তখনই সত্যিকারের গণতন্ত্রের পথে হাঁটবে দেশ।
নির্বাচন হবে-হয়তো ঢাকঢোল পিটিয়ে, হয়তো বিদেশি পর্যবেক্ষক রেখে, হয়তো নতুন মুখ বসিয়ে। কিন্তু প্রশ্নটা আজ নির্বাচন নিয়ে নয়, বরং নির্বাচন মাধ্যমে কী বদলাবে-তা নিয়ে। ভোটের লাইন লম্বা হলেই গণতন্ত্র হয় না, আর ব্যালট বাক্স ভরলেই জনগণের আস্থা ফিরে আসে না। পদ্ধতি যদি বেইমান হয়, কাঠামো যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়-তবে নির্বাচন মানে শুধু মুখ বদলের আয়োজন, শাসনের চরিত্রের নয়। আজ দরকার এমন এক রাজনৈতিক ছক, যেখানে ভোট না শুধু গণনা হবে-ভোটের মানেও গণ্য হবে। যেখানে একক দল নয়, সমঝোতার সরকার গড়ে তুলবে সমতার রাষ্ট্র। তবেই বলব, হ্যাঁ-এবারের নির্বাচন, শুধু তারিখের লড়াই নয়-ভবিষ্যতের গতিপথের সিদ্ধান্ত। এ দেশের মানুষ একদিন নিশ্চয় ভোট দেবে। প্রশ্ন হলো-সেই ভোট কি গড়বে ভবিষ্যৎ, না আবারও ফিরিয়ে আনবে অতীতেরই ছায়াপাত?
লেখক: সাংবাদিক, সমাজ গবেষক, মহাসচিব-কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ।
পাঠকের মতামত:
- ‘বিএনপির সঙ্গে জোট করার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি’
- ধামরাইয়ে রাতের আঁধারে কৃষকের এক বিঘা জমির লাউ গাছ কাটল দুর্বৃত্তরা
- ফরিদপুরে মসজিদের ভেতরে কন্যাশিশু ধর্ষণকারী ইমাম জেল হাজতে
- দেশজুড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর ও স্মৃতিচিহ্নে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থীদের
- ফরিদপুরে মাদক মামলায় সাজা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব
- 'ভারতীয় ব্রিগেট জামালপুরের উপর আক্রমণ চালায়'
- কর্ণফুলীতে ন্যাশনাল সিমেন্ট মিলসের স্পোর্টস কার্নিভাল অনুষ্ঠিত
- খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় রাইখালী সার্বজনীন লোকনাথ মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা
- ‘আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বদলি হলেও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবো না’
- মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ডিএফপিতে রক্তদান কর্মসূচি
- কাপাসিয়ায় নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
- ঝালকাঠি ও নলছিটি মুক্ত দিবস বিজয়োল্লাসের এক অবিস্মরণীয় দিন
- ঘোষণার ৬ মাস পর টুঙ্গিপাড়ায় এনসিপির সমন্বয় কমিটি
- ভক্তদের পদচারনায় আনন্দমুখর ছোট কুমার দিয়া কালী মন্দির
- ভৈরব পৌরসভার আয়োজনে নাগরিক সুবিধার্থে এই প্রথম ভিন্নধর্মী মেলা
- সোনারগাঁয়ের সাংবাদিকদের সাথে ইউএনও'র মতবিনিময় সভা
- জামায়াত প্রার্থী শিশির মনিরের নামে মামলা
- টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়নে পরিবর্তন চায় তৃণমূল
- সোনাতলায় আইনশৃঙ্খলা মিটিং ও বিজয় দিবসের প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত
- ফেরদৌসের পর এবার পপিকে বাদ দিলেন নির্মাতা
- বিটিভি-বেতারকে তফসিল রেকর্ড করতে প্রস্তুত থাকতে বললো ইসি
- লোহাগড়ায় হানাদার মুক্ত দিবস পালিত
- পাংশায় আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
- ৮ ডিসেম্বর লোহাগড়া হানাদার মুক্ত দিবস
- সখিনাকে খুঁজছেন আবুল হায়াত
- ভণ্ডামি আর নাটক থেকে মুক্তি চান আঁখি আলমগীর
- নরসিংদীতে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ৫
- ভোলায় ১৩ জেলে নিয়ে ট্রলারডুবি, নিখোঁজ ৮
- বরাদ্দ সংকটে বরগুনার ৪৭৭ কি.মি. সড়ক, চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা
- কক্সবাজারে পাহাড় ধসে শিশুসহ ৪ মৃত্যু
- ‘ক্ষমতা ছেড়ে দিন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবো’
- আবদুল হামিদ মাহবুব'র একগুচ্ছ লিমেরিক
- বরগুনায় আওয়ামীলীগের ২৪ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা
- চুয়াডাঙ্গায় দুই আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত
- বই পড়ার অভ্যাসে তলানিতে বাংলাদেশ, বছরে পড়ে ৩টিরও কম
- পঞ্চগড়ে ভাষা সৈনিক সুলতান বইমেলায় নতুন তিনটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
- সিলেটে কমছে বন্যার পানি, দেখা মিলেছে রোদের
- শেখ হাসিনার সাথে মুঠোফোনে কথা বলায় গ্রেফতার আ.নেতা জাহাঙ্গীর
- একদিনে ডেঙ্গুতে ১০ জনের মৃত্যু
- নোয়াখালীর বানভাসিদের পাশে শরীয়তপুরের শিক্ষার্থীরা
- মহম্মদপুরে শহীদ আবীর পাঠাগারসহ মুক্তিযোদ্ধাদের স্থাপনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি
- সন্ত্রাসীদের ঠাঁই নাই
- অনলাইন সাংবাদিকতায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল ‘চট্টগ্রাম জার্নাল’
- 'নির্লজ্জ বেহায়া হতেই কী আমরা তোমাকে খুন করেছি কিংবা তোমাকে রক্ষা করিনি?'
- 'তোমার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম যে ব্যক্তিটি খুনি মোশতাককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তিনি মাওলানা হামিদ খান ভাসানী, যাকে তুমি পিতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে'
-1.gif)
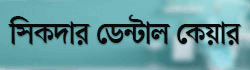

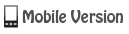































-2.jpg&w=60&h=50)























.jpg&w=60&h=50)


-1.jpg&w=60&h=50)




