ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে বাংলাদেশ: করণীয় ও প্রস্তুতি

মীর আব্দুল আলীম
১৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৯, উৎপত্তিস্থল ভারতের আসাম। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS) জানিয়েছে, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তত ছয়টি দেশে কম্পন অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছে, এই ভূমিকম্প ক্ষুদ্র হলেও বড় বিপদের পূর্বাভাস হতে পারে।
বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন শিলং প্লেটের ৮.৭ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্পে সমগ্র আসাম ও সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করছেন যে ১০০ বছরের ব্যবধানে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকে যায়। তাই বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের ভূমিকম্প এখন শুধু সম্ভাবনা নয়, বরং সময়ের ব্যাপার। এ অবস্থায় আমাদের সচেতনতা ও প্রস্তুতির বিকল্প নেই। এ অবস্থায় কি করতে হবে আমাদের। ভূমিকম্প মোকাবিলায় ১২ দফা সতর্কতা ও দিকনির্দেশনা জরুরী।
১. বিল্ডিং কোড মানা বাধ্যতামূলক করা: বাংলাদেশে ভবন নির্মাণে জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) বিদ্যমান থাকলেও তা কার্যত উপেক্ষিত। অধিকাংশ ভবন ঠিকমতো ভূমিকম্প সহনীয় নিয়ম মেনে তৈরি হয়নি। রাজধানীতে উচ্চ ভবনের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, কিন্তু নির্মাণ তদারকি নেই বললেই চলে। ফলে সামান্য মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পও বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এজন্য সরকারকে অবশ্যই বিল্ডিং কোডের কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে, লাইসেন্স ছাড়া কোনো নির্মাণকাজ অনুমোদন দেওয়া যাবে না এবং নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
২. পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিতকরণ: ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে হাজার হাজার পুরনো ও অনিরাপদ ভবন রয়েছে। যেগুলো ভূমিকম্পে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তৈরি করবে। সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে চিহ্নিত করে সংস্কার অথবা ভেঙে ফেলা দরকার। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আবাসিক ভবন ও বাজারগুলো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন করে না তোলা হলে, এক মুহূর্তেই সেগুলো ধসে শত শত প্রাণহানি ঘটাতে পারে।
৩. রাষ্ট্রীয় বাজেটে বাড়তি বরাদ্দ: প্রতিটি বাজেটে ভূমিকম্প মোকাবিলায় যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তা অত্যন্ত সামান্য। অথচ বিপর্যয় ঘটলে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয় এবং হাজারো প্রাণহানি ঘটে। তাই এ খাতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা জরুরি। উদ্ধার কার্যক্রম, জরুরি চিকিৎসা, সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পুনর্বাসনের জন্য আলাদা তহবিল তৈরি করতে হবে।
৪. জরুরি উদ্ধারকারী দল গঠন: ভূমিকম্প হলে প্রথম মুহূর্তে উদ্ধার কার্যক্রম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশে পেশাদার উদ্ধারকারী দল পর্যাপ্ত নেই। প্রতিটি বিভাগ, জেলা, এমনকি উপজেলা পর্যায়ে দমকল বাহিনী, সেনা ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে আধুনিক সরঞ্জামসহ প্রশিক্ষিত দল গঠন করতে হবে। প্রতি বছর নিয়মিত মহড়া চালু করলে মানুষ প্রস্তুত থাকবে।
৫. হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা: ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসা করাই হবে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের হাসপাতালে জরুরি শয্যা, ট্রমা সেন্টার, পর্যাপ্ত ওষুধ ও রক্তের মজুদ রাখতে হবে। বিশেষ করে রাজধানীর বড় হাসপাতালগুলোতে ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি সামলানোর আলাদা পরিকল্পনা থাকতে হবে। শুধুমাত্র সরকারি নয়, বেসরকারি হাসপাতালগুলোকেও এতে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৬. জনসচেতনতা কর্মসূচি: ভূমিকম্প মোকাবিলায় সচেতনতা তৈরি না হলে কোনো উদ্যোগই কার্যকর হবে না। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়মিত মহড়া চালু করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভূমিকম্পের সময় করণীয় শিখানো উচিত। কর্মক্ষেত্র, বাজার ও আবাসিক এলাকায় সচেতনতামূলক সভা, লিফলেট, প্রচারণা চালানো দরকার।
৭. শিশু ও প্রবীণদের সুরক্ষা পরিকল্পনা: ভূমিকম্পে শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীরা সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকে। তাদের জন্য আলাদা উদ্ধার পরিকল্পনা থাকতে হবে। যেমন- অটিজম শিশুদের নিরাপদে বের করে আনার মহড়া, বৃদ্ধাশ্রমে জরুরি সরঞ্জাম রাখা, ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা সাপোর্ট সিস্টেম গড়ে তোলা।
৮. গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ব্যবহার: ভূমিকম্পের আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া সম্ভব না হলেও কম্পনের পরপরই দ্রুত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া যায়। টেলিভিশন, রেডিও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা দেওয়া জরুরি। মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে ফ্রি জরুরি এসএমএস সেবা চালু করা উচিত।
৯. গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ: বাংলাদেশে ভূমিকম্প বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম এখনো সীমিত। ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সংখ্যা বাড়াতে হবে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় গবেষণা চালাতে হবে। কোথায় সক্রিয় ফল্ট লাইন রয়েছে, কোন অঞ্চলে কতটা ঝুঁকি এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করে জনসাধারণকে জানানো জরুরি।
১০. উদ্ধার সরঞ্জামের আধুনিকায়ন: বর্তমানে দমকল বাহিনী ও সিভিল ডিফেন্সে যে সরঞ্জাম রয়েছে, তা বড় ভূমিকম্পের সময় অপ্রতুল হবে। উদ্ধারকাজের জন্য ক্রেন, এক্সকাভেটর, হাইড্রোলিক যন্ত্রপাতি, ভূমিকম্প শনাক্তকরণ যন্ত্র, রোবটিক ডিভাইস সংগ্রহ করতে হবে। পাশাপাশি এসব ব্যবহারে জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
১১. স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা: কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয়, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা থাকা জরুরি। প্রতিটি পৌরসভা ও ইউনিয়নে স্থানীয় সরকারকে যুক্ত করতে হবে। মহড়া, উদ্ধার মহড়ায় ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম্য সংগঠন ও স্থানীয় এনজিওগুলোকে যুক্ত করা উচিত। এতে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়বে।
১২. সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ: ভূমিকম্প মোকাবিলা শুধু সরকারি দায়িত্ব নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতাও বটে। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, সামাজিক সংগঠন, ক্লাব সবখান থেকেই স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তুলতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জরুরি অবস্থায় কাজে লাগানো যাবে। একই সঙ্গে নাগরিক সমাজ ও তরুণদের নেতৃত্বে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।
বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে। বারবার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ১৪ই সেপ্টেম্বরের ভূমিকম্প আমাদের আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। এখনই প্রস্তুতি না নিলে বড় ভূমিকম্প হলে ভয়াবহ বিপর্যয় আমাদের মাথায় আসবে।
লেখক :সাংবাদিক, কলামিস্ট।
পাঠকের মতামত:
- গোপালগঞ্জে ভুয়া চিকিৎসককে ৩ মাসের কারাদণ্ড, ১ লাখ টাকা জরিমানা
- সুন্দরবনে নদী থেকে উদ্ধার পর্যটকের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর
- বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহালের দাবিতে চলছে সকাল-সন্ধ্য হরতাল, মহাসড়ক অবরোধ
- এসিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব প্রতিবেদন পাঠানোর অভিযোগ
- মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে মাদকসেবীদের আড্ডা
- কাপ্তাইয়ে আত্মপ্রকাশ করল মানবিক সংগঠন ‘বি পজেটিভ’
- সালথায় বিভাগদী শহীদস্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত
- লোহাগড়া সরকারি আদর্শ কলেজে নবাগত শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা
- কাপ্তাইয়ে তথ্য অফিসের আয়োজনে নারী সমাবেশ
- ভাঙ্গায় থানা ঘেরাও, গাড়ী ভাঙচুর, উপজেলা অফিসে হামলা, আগুন
- ‘ভারত থেকে কেনা হবে রেলের ২০০ নতুন কোচ’
- কোনো কিছুতেই থামানো যাচ্ছেনা ভাঙ্গার অবরোধ
- বাংলাদেশকে গ্রাসের ষড়যন্ত্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দ্বিমুখী আগ্রাসন
- ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে বাংলাদেশ: করণীয় ও প্রস্তুতি
- পৃথিবীর সুরক্ষা: ওজোন স্তর রক্ষার বিশ্বব্যাপী আহ্বান
- বিশ্ব লিম্ফোমা সচেতনতা দিবস: জানুন, বুঝুন, প্রতিরোধ করুন
- ‘শেখ হাসিনা বিরোধীপক্ষকে হিটলারের মতো দমন করতেন’
- গোপালগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনায় ভাইদের হাতে ভাই খুন
- ‘পশুরাও আমাদের চেয়ে ভালো জীবন কাটাচ্ছে’
- নেপালে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে আবারও রাস্তায় জেন জি
- টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, ওসিসহ আহত ২০
- পাংশা উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
- বাঁশবোঝাই ট্রাকে বাসের ধাক্কা, প্রাণ গেল পুলিশের এসআইসহ ৩ জনের
- ঈশ্বরদীতে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা তৈরিতে শিল্পীরা ব্যস্ত
- আইটেম গানে সামিরা খান মাহি
- ৩১ বছর পর আবার মুক্তি পেলো সালমান-মৌসুমীর ‘অন্তরে অন্তরে’
- ঠাকুরগাঁওয়ে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে মহিলা দলের মিছিল
- কুমিল্লায় ট্রেনে কাটা পড়ে তিন স্কুলছাত্রী নিহত
- পৃথিবীর সুরক্ষা: ওজোন স্তর রক্ষার বিশ্বব্যাপী আহ্বান
- দুঃসাহসী এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ও কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধের কথা
- রাজবাড়ীতে ৯ মাস নয় ৩ মাসেই পচছে পেঁয়াজ
- মৌলভীবাজার হানাদার মুক্ত দিবসে লাল-সবুজের বিজয় মিছিল
- ধন্য সেই পুরুষ
- কুমিল্লার নতুন মেয়র নৌকার রিফাত
- ঢাকার বিমানবন্দর থেকেই রোমিং সেবা পাবেন গ্রামীণফোন গ্রাহকরা
- চীন সফরে বাংলাদেশ সিডস ফর দ্য ফিউচার বিজয়ীরা
- সালথায় সাদা শাপলার সৌন্দর্যে মন কেড়েছে সবার
- এসএসসিতে গোপালগঞ্জ জেলার সেরা রাবেয়া-আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ
- ‘ক্ষমতা ছেড়ে দিন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবো’
- ‘আমার ছবিতে পচা জুতা নিক্ষেপ করো’
- ট্রাম্প প্রশাসনের দায়িত্ব ছাড়ছেন ইলন মাস্ক
- একাত্তরের কথা
- আটলান্টায় ফোবানা সম্মেলন পরিণত হলো পারিবারিক অনুষ্ঠানে
- মজাদার তালের বড়া বানাবেন যেভাবে
- মে দিবসের কবিতা
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
- ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে বাংলাদেশ: করণীয় ও প্রস্তুতি
- বিশ্ব লিম্ফোমা সচেতনতা দিবস: জানুন, বুঝুন, প্রতিরোধ করুন
-1.gif)
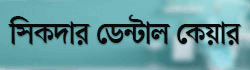

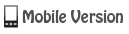






.jpg&w=60&h=50)
=.jpg&w=60&h=50)
.jpg&w=60&h=50)










.jpg&w=60&h=50)
-4.jpg&w=60&h=50)














-1.jpg&w=60&h=50)

-12.07.25.jpg&w=60&h=50)


.jpg&w=60&h=50)






















