বৈশ্বিক দারিদ্র্যের বাস্তব চিত্র: একুশ শতকের উন্নয়ন কি সবার জন্য?

ওয়াজেদুর রহমান কনক
বিশ্বে এমন এক দিন আছে, যার উদ্দেশ্য মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন ও গভীরতম সংকট—দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিজ্ঞা পুনরুজ্জীবিত করা এই দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয়, দারিদ্র্য শুধু অর্থনৈতিক অভাব নয়; এটি মানবিক মর্যাদা, ন্যায়, ও সামাজিক অংশগ্রহণের অভাবের প্রতীক। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আজও ক্ষুধা, অশিক্ষা, অনিরাপদ আশ্রয়, এবং বৈষম্যের ভার বহন করছে।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাই এই দিনে একত্র হয়ে দারিদ্র্যের মূল কারণসমূহ যেমন—অসাম্য, বঞ্চনা, সামাজিক বৈষম্য, ও জলবায়ুজনিত সংকট—এসব বিষয়ে নতুন করে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং টেকসই সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই দিনটির উদ্দেশ্য শুধু দরিদ্র মানুষের কষ্ট তুলে ধরা নয়, বরং তাদের মর্যাদা, কণ্ঠস্বর ও অধিকারকে বিশ্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা। এটি নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি আহ্বান—যেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল কেবল সংখ্যায় সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য হ্রাস দিবসের গুরুত্ব গভীর ও বহুমাত্রিক। এই দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক পালন নয়, বরং এটি বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি, নীতি-প্রণয়ন এবং মানবিক উন্নয়নের ধারাকে নতুন করে ভাবার এক ঐতিহাসিক আহ্বান। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ দারিদ্র্যকে রাষ্ট্রীয় নীতির কেন্দ্রে রেখেছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিসরে এই দিবস বাংলাদেশের অর্জন ও চ্যালেঞ্জকে তুলনামূলকভাবে মূল্যায়নের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।
বাংলাদেশ এক সময় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৭০-এর দশকে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১০০ ডলারের নিচে, আর দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের “দারিদ্র্যকে শত্রু” হিসেবে ঘোষণা সেই সময়ের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। এরপর থেকে কৃষি বিপ্লব, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, নারী অংশগ্রহণ, শিল্পায়ন ও রেমিট্যান্স—সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের পথে দৃঢ়ভাবে এগোচ্ছে। কিন্তু এই যাত্রা এখনো অসম্পূর্ণ, এবং এই দিবস আমাদের সেই অসম্পূর্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য হ্রাস দিবস বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি বার্তা বহন করে—দারিদ্র্য কেবল আর্থিক আয় নয়, বরং এটি জীবনযাত্রার মান, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মর্যাদার বিষয়। আজও দেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে মৌসুমি দারিদ্র্য বা মঙ্গার বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলে নতুন করে দারিদ্র্যের বিস্তার ঘটছে, যেখানে নদীভাঙন ও লবণাক্ততা কৃষিনির্ভর জীবিকাকে ধ্বংস করছে।
এই দিবস বাংলাদেশকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি দারিদ্র্য পুনরুত্পাদনের কাঠামোগত কারণগুলোও দূর করতে হবে। যেমন, শিক্ষা খাতে বৈষম্য, নারী শ্রমের অবমূল্যায়ন, স্বাস্থ্যসেবায় অনুপ্রবেশের ঘাটতি এবং কর্মসংস্থানে অনিশ্চয়তা—এসব বিষয় না বদলালে অর্জিত অগ্রগতি টেকসই হবে না। আজও প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ খাদ্যনিরাপত্তাহীন অবস্থায় বাস করে এবং শিশু পুষ্টিহীনতার হার ২৮ শতাংশের কাছাকাছি। ফলে এই দিবস সরকারের জন্য একটি নীতিগত প্রতিফলনের সুযোগ, যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা জালের কার্যকারিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বাস্তব প্রয়োগ বিশ্লেষণ করা হয়।
বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় নারী উদ্যোক্তা, এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ভূমিকা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য হ্রাস দিবস এই অর্জনগুলোকে শুধুমাত্র উদযাপন নয়, বরং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা হিসেবেও উপস্থাপন করে। বিশেষ করে ডিজিটাল অর্থনীতি, গ্রামীণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন পথ খোঁজা—এই দিবস সেই প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই দিবস নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, গবেষক, তরুণ প্রজন্ম এবং নীতিনির্ধারক—সবার জন্য আত্মসমালোচনার সুযোগ তৈরি করে। আমরা কতটা ন্যায্যভাবে উন্নয়নের সুফল বণ্টন করছি, কতটা পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পথে অগ্রসর হচ্ছি, এবং কতটা মানুষ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারছি—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজাই দিবসটির মূল অর্থ।
অতএব, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য হ্রাস দিবস কোনো আনুষ্ঠানিক পালন নয়; এটি হলো এক চলমান মানবিক ও নৈতিক প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন, যেখানে প্রতিটি মানুষ মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হওয়ার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়।
আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য হ্রাস দিবস প্রতি বছর ১৭ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় মানবজাতির এক প্রাচীনতম ও গভীরতম সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এই দিবসের সূচনা হয় ১৯৮৭ সালের ১৭ অক্টোবর, যখন ফ্রান্সের প্যারিসে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার চত্বরে প্রায় এক লক্ষ মানুষ সমবেত হয়ে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটিকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য দূরীকরণে বৈশ্বিক সংহতি গড়ে তোলা এবং এমন নীতিনির্ধারণে জোর দেওয়া যা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে পারে।
বিশ্ব দারিদ্র্যের বাস্তব চিত্র একবিংশ শতাব্দীতেও গভীর উদ্বেগের বিষয়। বিশ্বব্যাংকের ২০২4 সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে এখনো প্রায় ৬৫ কোটি মানুষ দৈনিক ২ দশমিক ১৫ ডলারের কম আয়ে জীবনযাপন করছে, যা চরম দারিদ্র্যের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে এই হার সবচেয়ে বেশি—এখানে জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ এখনো দারিদ্র্যের ফাঁদে বন্দি। দক্ষিণ এশিয়াতেও দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য, যদিও গত দুই দশকে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মতো দেশগুলো দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে নেমে এসেছে প্রায় ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে, আর চরম দারিদ্র্য মাত্র ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন, তবে এখনো প্রায় তিন কোটি মানুষ বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়ছে।
দারিদ্র্যের মূল কারণ শুধু আয়ের ঘাটতি নয়, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, লিঙ্গ বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং সামাজিক নিরাপত্তার ঘাটতির মতো জটিল কাঠামোগত বিষয়গুলোর সঙ্গে এটি গভীরভাবে জড়িত। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-1) দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রথম অগ্রাধিকার দিয়েছে—“No Poverty”—যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারি ও চলমান যুদ্ধবিগ্রহ, বিশেষত ইউক্রেন যুদ্ধ এবং গাজা সংকট, এই অগ্রগতিতে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। শুধু কোভিড-১৯ এর প্রভাবে প্রায় ১২ কোটি মানুষ পুনরায় দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে গিয়েছে বলে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে।
অর্থনৈতিক বৈষম্যও দারিদ্র্যের পুনরুত্পাদনে বড় ভূমিকা রাখছে। অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের ২০২৪ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনী জনগোষ্ঠীর হাতে রয়েছে বৈশ্বিক সম্পদের ৪৫ শতাংশ, আর নীচের ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ০.৭৫ শতাংশ। এই বৈষম্য দারিদ্র্যের সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে তুলছে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ, এনজিও কার্যক্রম, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি, রেমিট্যান্স, এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের মতো সংস্থা বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনের মডেল হিসেবে স্বীকৃত। সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেমন বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, এবং “একটি বাড়ি একটি খামার” প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে কাজ করছে। তবু জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষত উপকূলীয় এলাকা ও নদীভাঙন প্রবণ অঞ্চলে নতুন করে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অভ্যন্তরীণ জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।
শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য এখন নতুন চ্যালেঞ্জ। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার মতো নগরীতে বস্তি-নির্ভর জীবনযাপনকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। এদের মধ্যে অধিকাংশই দিনমজুর, গার্মেন্ট শ্রমিক বা অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ প্রায় অনুপস্থিত। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে যদি যথাযথ নীতি ও বিনিয়োগ না করা হয়, তবে নগর দারিদ্র্য গ্রামীণ দারিদ্র্যের চেয়েও জটিল আকার ধারণ করবে।
আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য হ্রাস দিবসের ২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য হচ্ছে “Decent Work and Social Protection: Putting Dignity in Practice for All,” অর্থাৎ “মর্যাদাপূর্ণ কাজ ও সামাজিক সুরক্ষা—সবার জন্য মর্যাদার বাস্তবায়ন।” এই প্রতিপাদ্যের মধ্যে দিয়ে জাতিসংঘ দারিদ্র্যকে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বরং মানব মর্যাদার প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছে।
দারিদ্র্য বিমোচন শুধু সরকারি বা আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্ব নয়; এটি মানবিক সহমর্মিতা, সমতা এবং ন্যায্যতার একটি বৈশ্বিক আন্দোলন। প্রতিটি নাগরিক, উদ্যোক্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক কিংবা গবেষকের উচিত সমাজে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। কারণ দারিদ্র্য কেবল অর্থনৈতিক পরিমাপ নয়—এটি একটি সামাজিক সংকট, যা মানবতার নৈতিক ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করে।
১৭ অক্টোবর—আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যহ্রাস দিবস, বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীকী দিন হিসেবে পালিত হয়। এই দিবসের ইতিহাস শুরু ১৯৮৭ সালের ১৭ অক্টোবর, যখন ফ্রান্সের প্যারিসে ট্রোকাডেরো প্লাজায় প্রায় এক লক্ষ মানুষ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, সহিংসতা ও ভয়ের শিকারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হয়েছিলেন। তারা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের বার্তা দিতে একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন করেছিলেন। এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন মানবাধিকারকর্মী জোসেফ রেসিনস্কি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা “ATD Fourth World”-এর কর্মীরা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মানবমর্যাদা, ন্যায্যতা ও সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রতিজ্ঞা শুরু হয়।
১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ রেজুলেশন ৪৭/১৯৬ গৃহীত করে ১৭ অক্টোবরকে “আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস” হিসেবে ঘোষণা করে। এ দিনটি পালনের মাধ্যমে জাতিসংঘ চায় বিশ্বের দেশগুলো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করুক, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দিক, এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করুক। ২০২৪ সালের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল “Ending Social and Institutional Maltreatment: Acting Together for Just, Peaceful and Inclusive Societies” — অর্থাৎ সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্ব্যবহার বন্ধ করে ন্যায্য, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে একসাথে কাজ করা। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্যের শিকার মানুষদের অভিজ্ঞতা শোনা, সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংলাপ গড়ে তোলা এবং বৈষম্যহীন উন্নয়নের আহ্বান জানানো।
বর্তমানে বিশ্বের দারিদ্র্য চিত্র একটি জটিল বাস্তবতা তুলে ধরে। বিশ্বব্যাংকের ২০২৪ সালের “Poverty, Prosperity and Planet” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখনো প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ—অর্থাৎ পৃথিবীর ৮.৫ শতাংশ জনগণ—প্রতিদিন ২.১৫ ডলারের কম আয়ে জীবনযাপন করে, যা চরম দারিদ্র্যরেখার নিচে পড়ে। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিছুটা হলেও, দারিদ্র্য হ্রাসের গতি গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে ধীর হয়ে গেছে। সাব-সাহারান আফ্রিকা এখনো চরম দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় ভার বহন করছে, যেখানে দারিদ্র্যরেখার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা বিশ্বের অন্য যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি।
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)-এর বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (MPI) অনুসারে, ১.১ বিলিয়ন মানুষ বিশ্বের ১১৩টি দেশে নানা ধরনের বঞ্চনার মধ্যে বাস করছে। এই সূচক অনুযায়ী দারিদ্র্য কেবল আয়নির্ভর নয়; বরং পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, বিদ্যুৎ ও আবাসন সুবিধা থেকেও বঞ্চনা এর অংশ। তাই দারিদ্র্যকে একটি বহুমাত্রিক সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা অর্থনৈতিক অবস্থা ছাড়াও জীবনমানের মানদণ্ড দ্বারা নির্ধারিত হয়।
বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসে গত দুই দশকে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে (প্রতিদিন ২.১৫ ডলার আয়) ২০১৬ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ১৩.৪৭ শতাংশ, যা ২০২২ সালে কমে দাঁড়ায় ১০.৪৪ শতাংশে। ২০১৬/১৭ সালের সরকারি জরিপ অনুযায়ী, ২৪.৩ শতাংশ মানুষ সাধারণ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং ১২.৯ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার কমে ১৮.৭ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্য ৫.৬ শতাংশে নেমে আসে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৬ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ, ২০২২ সালে তা নেমে এসেছে ১৮.৭ শতাংশে; চরম দারিদ্র্য ২৫.১ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।
তবে ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক চাপ, মূল্যস্ফীতি ও বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার সামান্য বেড়ে ২০.৫ শতাংশ থেকে ২০২৫ সালে ২২.৯ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। বিশেষত গ্রামীণ ও উত্তরাঞ্চলে “মঙ্গা” নামে পরিচিত মৌসুমী খাদ্যসংকট এখনো দারিদ্র্য সমস্যার বাস্তব রূপকে নির্দেশ করে, যা “মরা কার্তিক” নামে পরিচিত সেপ্টেম্বর–নভেম্বর সময়ে প্রকট আকার ধারণ করে।
দারিদ্র্য কেবল অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা নয়; এটি একটি সামাজিক ও কাঠামোগত সমস্যা। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ, নিরাপদ পানি, বিদ্যুৎ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বিচারপ্রবণতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে তোলে। COVID-19 মহামারী, যুদ্ধ, বৈশ্বিক ঋণ সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহ চেইনের বিঘ্ন বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যহ্রাসের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। অনেক দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও এর সুফল সমভাবে বণ্টিত হচ্ছে না, ফলে আয়-বৈষম্য বাড়ছে। দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো, বাজেট ঘাটতি, দুর্নীতি ও সামাজিক বৈষম্য এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।
জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (SDG) প্রথম লক্ষ্য “দারিদ্র্য বিমোচন” বা “No Poverty”—যার উদ্দেশ্য ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করা, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের জন্য উপযোগী প্রোগ্রাম তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, প্রশাসনিক জবাবদিহি, দুর্নীতি দমন ও বৈষম্য হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। একইসঙ্গে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সবুজ ও টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, দাতা সংস্থার অংশীদারিত্ব এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্যহীন সমাজ গঠনই এই দিবসের মূল লক্ষ্য ও চূড়ান্ত প্রত্যাশা।
বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য হ্রাসের সংগ্রাম এক অনন্য কিন্তু জটিল প্রক্রিয়া। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪ সালে বৈশ্বিকভাবে প্রায় *৭০০ মিলিয়ন মানুষ* প্রতিদিন *২.১৫ মার্কিন ডলারের কম আয়ে* বেঁচে আছে—অর্থাৎ তারা এখনো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। বৈশ্বিক জনসংখ্যার প্রায় *৮.৫ শতাংশ* এই চরম দারিদ্র্যের ফাঁদে আবদ্ধ, যার অর্ধেকেরও বেশি সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে। “Multidimensional Poverty Index (MPI)” অনুযায়ী, প্রায় *১.১ বিলিয়ন মানুষ* বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও বাসস্থান) শিকার হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে ২০২০–২০২3 সালের মধ্যে করোনা মহামারি, রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ, এবং জলবায়ুজনিত দুর্যোগ দারিদ্র্য হ্রাসের গতি নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দিয়েছে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই পরিসংখ্যানও একটি সতর্ক সংকেত বহন করে। ২০০৬ সালে দেশের দারিদ্র্যের হার ছিল *৪১.৫ শতাংশ, যা ২০২২ সালে কমে দাঁড়িয়েছে **১৮.৭ শতাংশে, এবং চরম দারিদ্র্যের হার **২৫.১ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৫.৬ শতাংশে। এই অগ্রগতি প্রশংসনীয় হলেও, এখনো প্রায় **তিন কোটি মানুষ* বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করছে। শহর ও গ্রামের আয়বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে; বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের *শীর্ষ ১০ শতাংশ জনগণ ভোগ করছে মোট সম্পদের প্রায় ৪২ শতাংশ, যেখানে **নিম্ন ৪০ শতাংশ জনগণ ভাগ পাচ্ছে মাত্র ১৫ শতাংশেরও কম*।
অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, এবং উত্তরাঞ্চলে মৌসুমি খাদ্যসংকট—সব মিলিয়ে নতুন করে দারিদ্র্যের ঝুঁকি তৈরি করছে। জাতিসংঘের পূর্বাভাস অনুযায়ী, *২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য সম্পূর্ণ নির্মূলের লক্ষ্য (SDG 1)* অর্জনের পথে বাংলাদেশকে বছরে অন্তত *৬–৭ শতাংশ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি* বজায় রাখতে হবে।
তবে এই সংগ্রাম শুধু পরিসংখ্যানের নয়—এটি মানব মর্যাদার, সামাজিক ন্যায়বিচারের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নৈতিক দায়িত্বের বিষয়। তাই বৈশ্বিক পরিসরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যতই বাড়ুক না কেন, যদি তার সুফল মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে না পৌঁছায় , তবে উন্নয়ন কেবল সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই উপলব্ধিই এই দিনের চূড়ান্ত বার্তা—যেখানে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পরিবার, দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার অর্জন করতে পারে।
লেখক : গণমাধ্যমকর্মী।
পাঠকের মতামত:
- এলজিইডির উন্নয়ন কাজে বদলে গেছে গ্রামীণ জনপদ
- যশোরে ২৫ কোটি টাকার শীতকালীন সবজির চারা বিক্রির লক্ষ্য
- হিলি বন্দর দিয়ে ফের পেঁয়াজ জামদানি শুরু, কমেছে দাম
- বালিয়াকান্দিতে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে চা-দোকানী গ্রেফতার
- মুক্তিপণের দাবিতে সুন্দরবনে কর্মরত থেকে ৭ জেলেকে অপহরণ
- তারেক রহমানের পক্ষ থেকে বাগেরহাটে ভিক্ষক পরিবারকে টিনসেড ঘর উপহার
- দিনাজপুরে হাসপাতালে ফেলে যাওয়া সেই শিশুটি স্থান পেলো এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে
- রাজবাড়ীতে আমন ধানের ফলন ভালো হলেও দাম নিয়ে হতাশ কৃষক
- দরপত্র ছাড়া বিদ্যালয়ের টিনসেড ঘর বিক্রি, তদন্তে কমিটি
- যথাযোগ্য মর্যাদায় সাতক্ষীরা মুক্ত দিবস পালিত
- সুন্দরবন থেকে ট্রলারসহ ৭ জেলে আটক
- সাতক্ষীরায় সাংবাদিকদের সাথে নবাগত পুলিশ সুপারের মতবিনিময়
- কমিটি গঠনের ৬ দিনের মাথায় কোটালীপাড়ায় জামায়তের হিন্দু শাখার ৯ নেতাকর্মীর পদত্যাগ
- শীতের তীব্রতায় ব্যস্ততা বেড়েছে লেপ-তোশক কারিগরদের
- নগরকান্দায় ধর্মীয় অনুভূতি অবমাননার অভিযোগে প্রতিবাদ সমাবেশ
- ফরিদপুরে ডিবি পুলিশের হাতে ১ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১
- ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কানাডা-আলাস্কা সীমান্ত এলাকা
- কবিরহাটে রোহান দিবা-রাত্রি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত
- পাংশায় মুক্তিযোদ্ধাদের কববের জন্য নির্ধারিত স্থানের আগুন
- চলচ্চিত্র উৎসবের নারী নির্মাতা বিভাগে বিচারক আফসানা মিমি
- আমিরাতের লিগে অভিষেকে উজ্জ্বল মোস্তাফিজ
- ‘বিএনপি সবসময়ই প্রতিশ্রুতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী’
- নড়াইলে পুকুর পাড় থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার
- শেখ হাসিনাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ
- রবিবার থেকে সীমিত আকারে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি
- প্রাণ
- উখিয়ার লাল পাহাড়ে র্যাবের অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক ২
- বিবস্ত্র করে মারপিট, লজ্জায় কলেজছাত্রীর আত্মহত্যা
- ভণ্ডামি আর নাটক থেকে মুক্তি চান আঁখি আলমগীর
- নরসিংদীতে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ৫
- ভোলায় ১৩ জেলে নিয়ে ট্রলারডুবি, নিখোঁজ ৮
- ‘ক্ষমতা ছেড়ে দিন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবো’
- কক্সবাজারে পাহাড় ধসে শিশুসহ ৪ মৃত্যু
- বরাদ্দ সংকটে বরগুনার ৪৭৭ কি.মি. সড়ক, চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা
- বরগুনায় আওয়ামীলীগের ২৪ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা
- আবদুল হামিদ মাহবুব'র একগুচ্ছ লিমেরিক
- সিলেটে কমছে বন্যার পানি, দেখা মিলেছে রোদের
- শেখ হাসিনার সাথে মুঠোফোনে কথা বলায় গ্রেফতার আ.নেতা জাহাঙ্গীর
- পঞ্চগড়ে ভাষা সৈনিক সুলতান বইমেলায় নতুন তিনটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
- মহম্মদপুরে শহীদ আবীর পাঠাগারসহ মুক্তিযোদ্ধাদের স্থাপনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি
- বই পড়ার অভ্যাসে তলানিতে বাংলাদেশ, বছরে পড়ে ৩টিরও কম
- একদিনে ডেঙ্গুতে ১০ জনের মৃত্যু
- সন্ত্রাসীদের ঠাঁই নাই
- 'নির্লজ্জ বেহায়া হতেই কী আমরা তোমাকে খুন করেছি কিংবা তোমাকে রক্ষা করিনি?'
- তারেক রহমানের পক্ষ থেকে বাগেরহাটে ভিক্ষক পরিবারকে টিনসেড ঘর উপহার
-1.gif)
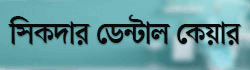

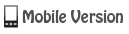










.jpg&w=60&h=50)



















-2.jpg&w=60&h=50)





-1.jpg&w=60&h=50)




.jpg&w=60&h=50)













.jpg&w=60&h=50)


-1.jpg&w=60&h=50)




