জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন: বৈশ্বিক নীতি ও স্থানীয় বাস্তবতা

ওয়াজেদুর রহমান কনক
পৃথিবী আজ এমন এক সঙ্কটময় সময় অতিক্রম করছে, যখন জলবায়ু পরিবর্তন কেবল পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে না—বরং মানুষের জীবিকা, স্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনীতি ও বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের কাঠামোকেও গভীরভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছে। এটি এখন মানবজাতির টিকে থাকার লড়াই, যেখানে টেকসই উন্নয়নই একমাত্র কার্যকর সমাধানের পথ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য SDG 13: Climate Action এবং ২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব সম্প্রদায় একমত হয়েছে যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী সেই লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারছে না; বরং পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে।
World Meteorological Organization (WMO)-এর ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা শিল্পবিপ্লব-পূর্ব সময়ের তুলনায় ইতিমধ্যেই ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে—যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নজিরবিহীন পরিবর্তন। এই উষ্ণায়নের মূল কারণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ, যা ২০২৪ সালে ৩৭ বিলিয়ন টন CO₂–এর নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে (IEA, 2024)। উন্নত দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবে মোট নিঃসরণের প্রায় ৭৫ শতাংশের জন্য দায়ী হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো। IPCC-এর সর্বশেষ বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে, যা বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০ কোটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করবে।
বাংলাদেশ এই বৈশ্বিক বাস্তবতার করুণ উদাহরণ। বিশ্বের কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ০.৪৭ শতাংশ, কিন্তু জলবায়ু ঝুঁকির তালিকায় দেশটি শীর্ষ পাঁচের মধ্যে। Global Climate Risk Index 2024 অনুসারে, দক্ষিণাঞ্চলে গত এক দশকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ উপকূলীয় ভূমি বিলীন হতে পারে, এবং দুই কোটিরও বেশি মানুষ জলবায়ু শরণার্থী হয়ে পড়তে পারে। কৃষি, মৎস্য ও পানিসম্পদ—যা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও খাদ্যনিরাপত্তার মূল ভিত্তি—সবচেয়ে বড় আঘাত পাচ্ছে। FAO-এর তথ্যমতে, লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ধান উৎপাদন ২০ বছরের ব্যবধানে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমেছে, যা খাদ্যনিরাপত্তার জন্য এক গুরুতর সংকেত।
অন্যদিকে, বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু নীতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। প্যারিস চুক্তির সময় উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু সহায়তা দেবে। কিন্তু OECD 2024-এর তথ্যমতে, বাস্তবে এই অর্থ এখনো মাত্র ৮৩.৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই ঋণ—অনুদান নয়। ফলে দরিদ্র দেশগুলো এক নতুন “জলবায়ু ঋণ–ফাঁদে” পড়ছে।
বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে “Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)” গ্রহণ করে। পরবর্তীতে “Mujib Climate Prosperity Plan 2022–2041” নামে দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প ঘোষণা করা হয়, যার উদ্দেশ্য শুধু অভিযোজন নয়, বরং “Adaptation to Prosperity”— অর্থাৎ জলবায়ু সহনশীলতা থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য শক্তির অংশগ্রহণ ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে মাত্র ৪.৩ শতাংশ।
তবে বাস্তবে এখনো বহু বাধা রয়ে গেছে। দ্রুত নগরায়ন, বায়ুদূষণ, বন উজাড়, নদী দখল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। IQAir 2025-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার বায়ুতে PM2.5 মাত্রা ৮৩.৫ µg/m³, যা WHO মানদণ্ডের তুলনায় প্রায় ১৬ গুণ বেশি। এই দূষণের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছে (Institute for Health Metrics, 2024)।
তবুও ইতিবাচক দিকও রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু অভিযোজন–নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃত। দেশে বর্তমানে ৭,০০০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ২০০টির বেশি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, এবং ৮০০টির বেশি ক্লাইমেট স্মার্ট স্কুল কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। নারী নেতৃত্বাধীন Climate Resilient Entrepreneurship এবং তরুণদের অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য শক্তি উদ্যোগগুলো নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।
বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কেবল পরিবেশগত সংকট নয়, এটি অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা, শ্রমবাজার ও মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলছে। IPCC–এর ২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৫০ বছরে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই উষ্ণায়নের প্রধান কারণ মানবসৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ—যার ৭৫ শতাংশের বেশি এসেছে শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে। এর ফলেই দেখা দিয়েছে হিমবাহ গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, খরা ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা।
বাংলাদেশ, যদিও বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে মাত্র ০.৪৭ শতাংশ অবদান রাখে (World Bank, 2024), তবুও এটি জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। Global Climate Risk Index 2024 অনুযায়ী, গত দুই দশকে জলবায়ুজনিত দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ বছরে গড়ে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছরে গড়ে ৩.৮ মিলিমিটার করে বাড়ছে, যার ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে (World Bank, South Asia Climate Roadmap, 2023)।
কৃষি খাত, যা বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০ শতাংশের জীবিকা নির্ভর করে, জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে ধান, মাছ ও সবজি উৎপাদন ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলে খরা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ফসলের উৎপাদন চক্রে বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)-এর তথ্যানুসারে, ২০৪০ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদন ১৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে যদি বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকে।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য SDG 13—“Climate Action”—এই সংকট মোকাবিলার নীতি কাঠামো তৈরি করেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতায় ভুগছে। প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিলের আওতায় প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তার কথা থাকলেও, OECD (২০২৩)-এর তথ্যানুযায়ী এখন পর্যন্ত গড়ে মাত্র ৮৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছে, যার বেশিরভাগই ঋণ। ফলে দরিদ্র ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো নতুন ঋণের ফাঁদে পড়ছে।
বাংলাদেশ সরকার এ পরিস্থিতিতে ২০০৯ সালে BCCSAP গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে “Mujib Climate Prosperity Plan 2022–2041” প্রণয়ন করে একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করেছে। এর লক্ষ্য কেবল অভিযোজন নয়, বরং জলবায়ু সহনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা। পরিকল্পনাটির আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৪০ শতাংশ পূরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের হার মাত্র ৪.৩ শতাংশ, যেখানে সৌরবিদ্যুৎ প্রধান উৎস।
তবে নীতিগত এই অগ্রগতি বাস্তবে এখনো বড় চ্যালেঞ্জের মুখে। নগরায়নের অনিয়ম, নদী ভরাট, বনভূমি ধ্বংস ও শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করছে। ঢাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বের শীর্ষ তিন দূষিত শহরের তালিকায় রয়েছে (IQAir, ২০২৫)। একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হচ্ছে—এই দ্বৈত চাপে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন নীতিগুলো এক জটিল ভারসাম্য রক্ষার লড়াইয়ে আছে।
তবুও আশার আলো আছে। বাংলাদেশের উপকূলে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ২০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, এবং ৭০০টির বেশি ক্লাইমেট স্মার্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী ও স্থানীয় সম্প্রদায়কে জলবায়ু অভিযোজন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা, কাঁকড়া ও লবণ সহনশীল ফসল চাষ, মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প জীবিকা প্রশিক্ষণ—এসব উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা এনেছে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক বাস্তবতা। কেবল আন্তর্জাতিক নীতি নয়, স্থানীয় বাস্তবায়নই এর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন জলবায়ু নীতি শুধু পরিবেশ নয়, বরং কৃষি, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের অবস্থান আজ আর “জলবায়ু ভুক্তভোগী” নয়—বরং “জলবায়ু যোদ্ধা”—যে লড়ছে অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি এক টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য।
Bangladesh এই বৈশ্বিক বাস্তবতার এক করুণ উদাহরণ। বিশ্বের কার্বন নিঃসরণে দেশের অবদান মাত্র প্রায় ০.৪৭ শতাংশ হলেও, জলবায়ু ঝুঁকির তালিকায় এটি শীর্ষ পাঁচের মধ্যে রয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে গত এক দশকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ উপকূলীয় ভূমি বিলীন হতে পারে এবং দুই কোটিরও বেশি মানুষ জলবায়ু শরণার্থী হয়ে পড়তে পারে। কৃষি, মৎস্য ও পানিসম্পদ—যা দেশের অর্থনীতি ও খাদ্যনিরাপত্তার মূল —এগুলোর ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত পড়ছে; বিশেষ করে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ধান উৎপাদন গত ২০ বছরের ব্যবধানে প্রায় ৩০–৪০ শতাংশ কমেছে।
নতুন তথ্য অনুযায়ী, ওই দেশে শুধুমাত্র গত বছরে থার্মাল হিট বা তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে প্রায় ৪৪ টি অতিরিক্ত (extra) উষ্ণ দিনের মুখোমুখি হয়েছ—২০২৪ সালের মে থেকে ২০২৫ সালের মে সময়ের মধ্যে। এ সময়কালে দেশের কিছু অঞ্চলে স্কুল বন্ধ করতে হয়েছে অত্যধিক তাপের কারণে। এছাড়া একটি ২০২৫ সালের গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের অন্তরর্ত্রাল (internal) জলবায়ু–রূপে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে ২২০০ লক্ষ বা তারও বেশি হতে পারে। এ ছাড়াও একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ২০২৪ সালে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (প্রায় ০.৪ শতাংশ জিডিপি) ক্ষতি হয়েছে। এই তথ্যগুলো স্পষ্ট নির্দেশ দেয় যে, শুধু ভবিষ্যতের জন্য নয় — বর্তমানেও জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অবকাঠামোকে সঙ্কটে দিচ্ছে।
বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে “Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)” গ্রহণ করেছে। পরে “Mujib Climate Prosperity Plan 2022–2041” নামে দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প ঘোষণা করা হয়, যার উদ্দেশ্য শুধু অভিযোজন নয়, বরং “Adaptation to Prosperity”—অর্থাৎ জলবায়ু-সহনশীলতা থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য শক্তির অংশগ্রহণ ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে মাত্র ৪.৩ শতাংশ। এছাড়া নতুন শিক্ষা উদ্যোগ হিসেবে দেশের একটি “Climate Smart Education Systems Initiative” চালু করা হয়েছে যেটি শিক্ষা নীতিতে জলবায়ু সহনশীলতা ও টেকসইতা অন্তর্ভুক্ত করার দিকে কাজ করছে।
তবে বাস্তবায়নে এখনও বড় বাধা রয়ে গেছে। দ্রুত নগরায়ন, বায়ুদূষণ, বন উজাড়, নদী ভরাট ও দখল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা টেকসই উন্নয়নকে প্রতিবন্ধক করে তুলেছে। যেমন, ঢাকার বায়ুতে PM2.5 মাত্রা WHO-র মানদণ্ডের তুলনায় প্রায় ১৬ গুণ বেশি। তবে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলো, শুধু ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা নয় — একটি নতুন বিপদ হিসেবে উঠে এসেছে বাড়তি তাপপ্রবাহ ও অস্বাভাবিক উষ্ণতা। এই কারণে মানবদেহ ও জীবিকা সর্বস্তরে প্রভাব পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায়, অফিস পরিস্থিতিতে, কৃষিতে — সবখানেই দেখা দিয়েছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব।
তবুও আশার আলো রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু অভিযোজন-নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃত ও তেমনভাবে কাজ করছে। দেশে ইতিমধ্যে প্রায় ৭,০০০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ২০০টির বেশি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, এবং ৮০০টির বেশি “ক্লাইমেট স্মার্ট স্কুল” কার্যকরভাবে চালু হয়েছে। নারী নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ ও তরুণদের অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য শক্তি, সহনশীল কৃষি ও উদ্যোগ সৃষ্টিতে ইতিবাচক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।
জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন এখন একে অপরের পরিপূরক বাস্তবতা। এটি শুধু পরিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্ন নয়; এটি মানবিক টিকে থাকার, অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। বৈশ্বিক নীতির সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোগের মেলবন্ধনই দিয়ে পারে এই সংকটকে সম্ভাবনায় রূপ দিতে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দেখায় — সীমিত সম্পদ, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, পরিকল্পিত অভিযোজন, মানবিক সংহতি এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থায়ন নিশ্চিত করা গেলে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু একটি বিপর্যয় নয়, এক টেকসই উন্নয়নের নতুন অধ্যায় রচনা করতে পারে।
বাংলাদেশ এই বৈশ্বিক বাস্তবতার করুণ উদাহরণ। বিশ্বের কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ০.৪৭ শতাংশ, কিন্তু জলবায়ু ঝুঁকির তালিকায় দেশটি শীর্ষ পাঁচের মধ্যে। Global Climate Risk Index 2024 অনুসারে, দক্ষিণাঞ্চলে গত এক দশকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ উপকূলীয় ভূমি বিলীন হতে পারে, এবং দুই কোটিরও বেশি মানুষ জলবায়ু শরণার্থী হয়ে পড়তে পারে। কৃষি, মৎস্য ও পানিসম্পদ—যা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও খাদ্যনিরাপত্তার মূল ভিত্তি—সবচেয়ে বড় আঘাত পাচ্ছে। FAO-এর তথ্যমতে, লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ধান উৎপাদন ২০ বছরের ব্যবধানে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমেছে, যা খাদ্যনিরাপত্তার জন্য এক গুরুতর সংকেত।
অন্যদিকে, বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু নীতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। প্যারিস চুক্তির সময় উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু সহায়তা দেবে। কিন্তু OECD 2024-এর তথ্যমতে, বাস্তবে এই অর্থ এখনো মাত্র ৮৩.৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই ঋণ—অনুদান নয়। ফলে দরিদ্র দেশগুলো এক নতুন “জলবায়ু ঋণ–ফাঁদে” পড়ছে।
বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে “Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)” গ্রহণ করে। পরবর্তীতে “Mujib Climate Prosperity Plan 2022–2041” নামে দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প ঘোষণা করা হয়, যার উদ্দেশ্য শুধু অভিযোজন নয়, বরং “Adaptation to Prosperity”— অর্থাৎ জলবায়ু সহনশীলতা থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য শক্তির অংশগ্রহণ ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে মাত্র ৪.৩ শতাংশ।
তবে বাস্তবে এখনো বহু বাধা রয়ে গেছে। দ্রুত নগরায়ন, বায়ুদূষণ, বন উজাড়, নদী দখল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। IQAir 2025-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার বায়ুতে PM2.5 মাত্রা ৮৩.৫ µg/m³, যা WHO মানদণ্ডের তুলনায় প্রায় ১৬ গুণ বেশি। এই দূষণের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছে (Institute for Health Metrics, 2024)।
তবুও ইতিবাচক দিকও রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু অভিযোজন–নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃত। দেশে বর্তমানে ৭,০০০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ২০০টির বেশি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, এবং ৮০০টির বেশি ক্লাইমেট স্মার্ট স্কুল কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। নারী নেতৃত্বাধীন Climate Resilient Entrepreneurship এবং তরুণদের অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য শক্তি উদ্যোগগুলো নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।
বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কেবল পরিবেশগত সংকট নয়, এটি অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা, শ্রমবাজার ও মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলছে। IPCC–এর ২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৫০ বছরে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই উষ্ণায়নের প্রধান কারণ মানবসৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ—যার ৭৫ শতাংশের বেশি এসেছে শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে। এর ফলেই দেখা দিয়েছে হিমবাহ গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, খরা ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা।
বাংলাদেশ, যদিও বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে মাত্র ০.৪৭ শতাংশ অবদান রাখে (World Bank, 2024), তবুও এটি জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। Global Climate Risk Index 2024 অনুযায়ী, গত দুই দশকে জলবায়ুজনিত দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ বছরে গড়ে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছরে গড়ে ৩.৮ মিলিমিটার করে বাড়ছে, যার ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে (World Bank, South Asia Climate Roadmap, 2023)।
কৃষি খাত, যা বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০ শতাংশের জীবিকা নির্ভর করে, জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে ধান, মাছ ও সবজি উৎপাদন ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলে খরা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ফসলের উৎপাদন চক্রে বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)-এর তথ্যানুসারে, ২০৪০ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদন ১৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে যদি বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকে।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য SDG 13—“Climate Action”—এই সংকট মোকাবিলার নীতি কাঠামো তৈরি করেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতায় ভুগছে। প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিলের আওতায় প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তার কথা থাকলেও, OECD (২০২৩)-এর তথ্যানুযায়ী এখন পর্যন্ত গড়ে মাত্র ৮৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছে, যার বেশিরভাগই ঋণ। ফলে দরিদ্র ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো নতুন ঋণের ফাঁদে পড়ছে।
বাংলাদেশ সরকার এ পরিস্থিতিতে ২০০৯ সালে BCCSAP গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে “Mujib Climate Prosperity Plan 2022–2041” প্রণয়ন করে একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করেছে। এর লক্ষ্য কেবল অভিযোজন নয়, বরং জলবায়ু সহনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা। পরিকল্পনাটির আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৪০ শতাংশ পূরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের হার মাত্র ৪.৩ শতাংশ, যেখানে সৌরবিদ্যুৎ প্রধান উৎস।
তবে নীতিগত এই অগ্রগতি বাস্তবে এখনো বড় চ্যালেঞ্জের মুখে। নগরায়নের অনিয়ম, নদী ভরাট, বনভূমি ধ্বংস ও শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করছে। ঢাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বের শীর্ষ তিন দূষিত শহরের তালিকায় রয়েছে (IQAir, ২০২৫)। একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হচ্ছে—এই দ্বৈত চাপে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন নীতিগুলো এক জটিল ভারসাম্য রক্ষার লড়াইয়ে আছে।
তবুও আশার আলো আছে। বাংলাদেশের উপকূলে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ২০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, এবং ৭০০টির বেশি ক্লাইমেট স্মার্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী ও স্থানীয় সম্প্রদায়কে জলবায়ু অভিযোজন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা, কাঁকড়া ও লবণ সহনশীল ফসল চাষ, মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প জীবিকা প্রশিক্ষণ—এসব উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা এনেছে।
লেখক : গণমাধ্যমকর্মী।
পাঠকের মতামত:
- ‘বিএনপির সঙ্গে জোট করার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি’
- ধামরাইয়ে রাতের আঁধারে কৃষকের এক বিঘা জমির লাউ গাছ কাটল দুর্বৃত্তরা
- ফরিদপুরে মসজিদের ভেতরে কন্যাশিশু ধর্ষণকারী ইমাম জেল হাজতে
- দেশজুড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর ও স্মৃতিচিহ্নে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থীদের
- ফরিদপুরে মাদক মামলায় সাজা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব
- 'ভারতীয় ব্রিগেট জামালপুরের উপর আক্রমণ চালায়'
- কর্ণফুলীতে ন্যাশনাল সিমেন্ট মিলসের স্পোর্টস কার্নিভাল অনুষ্ঠিত
- খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় রাইখালী সার্বজনীন লোকনাথ মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা
- ‘আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বদলি হলেও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবো না’
- মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ডিএফপিতে রক্তদান কর্মসূচি
- কাপাসিয়ায় নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
- ঝালকাঠি ও নলছিটি মুক্ত দিবস বিজয়োল্লাসের এক অবিস্মরণীয় দিন
- ঘোষণার ৬ মাস পর টুঙ্গিপাড়ায় এনসিপির সমন্বয় কমিটি
- ভক্তদের পদচারনায় আনন্দমুখর ছোট কুমার দিয়া কালী মন্দির
- ভৈরব পৌরসভার আয়োজনে নাগরিক সুবিধার্থে এই প্রথম ভিন্নধর্মী মেলা
- সোনারগাঁয়ের সাংবাদিকদের সাথে ইউএনও'র মতবিনিময় সভা
- জামায়াত প্রার্থী শিশির মনিরের নামে মামলা
- টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়নে পরিবর্তন চায় তৃণমূল
- সোনাতলায় আইনশৃঙ্খলা মিটিং ও বিজয় দিবসের প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত
- ফেরদৌসের পর এবার পপিকে বাদ দিলেন নির্মাতা
- বিটিভি-বেতারকে তফসিল রেকর্ড করতে প্রস্তুত থাকতে বললো ইসি
- লোহাগড়ায় হানাদার মুক্ত দিবস পালিত
- পাংশায় আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
- ৮ ডিসেম্বর লোহাগড়া হানাদার মুক্ত দিবস
- সখিনাকে খুঁজছেন আবুল হায়াত
- ভণ্ডামি আর নাটক থেকে মুক্তি চান আঁখি আলমগীর
- নরসিংদীতে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ৫
- ভোলায় ১৩ জেলে নিয়ে ট্রলারডুবি, নিখোঁজ ৮
- বরাদ্দ সংকটে বরগুনার ৪৭৭ কি.মি. সড়ক, চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা
- কক্সবাজারে পাহাড় ধসে শিশুসহ ৪ মৃত্যু
- ‘ক্ষমতা ছেড়ে দিন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবো’
- আবদুল হামিদ মাহবুব'র একগুচ্ছ লিমেরিক
- বরগুনায় আওয়ামীলীগের ২৪ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা
- চুয়াডাঙ্গায় দুই আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত
- বই পড়ার অভ্যাসে তলানিতে বাংলাদেশ, বছরে পড়ে ৩টিরও কম
- পঞ্চগড়ে ভাষা সৈনিক সুলতান বইমেলায় নতুন তিনটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
- সিলেটে কমছে বন্যার পানি, দেখা মিলেছে রোদের
- শেখ হাসিনার সাথে মুঠোফোনে কথা বলায় গ্রেফতার আ.নেতা জাহাঙ্গীর
- একদিনে ডেঙ্গুতে ১০ জনের মৃত্যু
- নোয়াখালীর বানভাসিদের পাশে শরীয়তপুরের শিক্ষার্থীরা
- মহম্মদপুরে শহীদ আবীর পাঠাগারসহ মুক্তিযোদ্ধাদের স্থাপনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি
- সন্ত্রাসীদের ঠাঁই নাই
- অনলাইন সাংবাদিকতায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল ‘চট্টগ্রাম জার্নাল’
- 'নির্লজ্জ বেহায়া হতেই কী আমরা তোমাকে খুন করেছি কিংবা তোমাকে রক্ষা করিনি?'
- 'তোমার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম যে ব্যক্তিটি খুনি মোশতাককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তিনি মাওলানা হামিদ খান ভাসানী, যাকে তুমি পিতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে'
-1.gif)
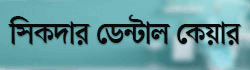

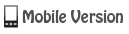































-2.jpg&w=60&h=50)























.jpg&w=60&h=50)


-1.jpg&w=60&h=50)




