বিশ্ব শহর দিবসের বার্তা
শহর কেবল অবকাঠামো নয়, এক মানবিক পরিবেশ

ওয়াজেদুর রহমান কনক
বিশ্ব শহর দিবস (World Cities Day) কেবল একটি স্মারক নয়, এটি মানব সভ্যতার নগরভিত্তিক বিকাশের ধারাকে টেকসই, ন্যায়ভিত্তিক ও পরিবেশসম্মত করার বৈশ্বিক আহ্বান। প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর জাতিসংঘ ও তার নগর উন্নয়ন সংস্থা UN-Habitat এই দিবসটি উদযাপন করে “Better City, Better Life” স্লোগানের আলোকে, যার মূলে রয়েছে একটি সুসংগঠিত বার্তা—“শহর হলো মানব উন্নয়নের কেন্দ্র, তবে তা টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক হতে হবে।”
বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৮.২ বিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৫.১ বিলিয়ন মানুষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ শহরে বসবাস করছে। জাতিসংঘের World Urbanization Prospects 2024 অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে এ হার ৬৮ শতাংশে পৌঁছাবে, অর্থাৎ বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ তখন নগরায়ণের মধ্যে বসবাস করবে। কিন্তু এই নগরায়ণ একই সঙ্গে সম্ভাবনা ও সংকট—শহরসমূহ বিশ্বের মোট GDP-এর প্রায় ৮০ শতাংশ উৎপাদন করে, আবার একই সময়ে কার্বন নিঃসরণের প্রায় ৭০ শতাংশ শহর থেকেই আসে। অর্থাৎ শহর মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইঞ্জিন, আবার জলবায়ু পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিও বটে।
বিশ্ব শহর দিবসের বার্তা তাই এই বাস্তবতার মুখোমুখি এক দার্শনিক আহ্বান—অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানবকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে। টেকসই শহর গড়ে তুলতে হলে অবকাঠামো, বাসস্থান, পানি, স্বাস্থ্য, বর্জ্য, জ্বালানি, পরিবহন ও প্রযুক্তি—সবকিছুতেই মানবিক ও পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। UN-Habitat-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে বিশ্বে প্রায় ১.১ বিলিয়ন মানুষ স্লাম বা অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাস করে, যা শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ২৪ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশের দ্রুত নগরায়ণ সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে নগর পরিকল্পনা কেবল স্থাপত্যের নয়, এটি সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নেও পরিণত হয়েছে।
জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG-11) সঙ্গে এই দিবসের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। “Sustainable Cities and Communities” লক্ষ্যটি বলে, শহরগুলোকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive), নিরাপদ (safe), সহনশীল (resilient) এবং টেকসই (sustainable)। শহর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কেন্দ্র নয়, বরং সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মানবসম্পর্কের সংমিশ্রণস্থল। একে টেকসই করতে হলে প্রযুক্তি, নীতি ও নৈতিকতার সমন্বিত প্রয়োগ প্রয়োজন।
এই দিবস বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়—আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে বাস করছি, যখন পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে শহরে। আজ পৃথিবীতে ৩৩টিরও বেশি মেগাসিটি (যাদের জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়েছে) গড়ে উঠেছে; ২০৫০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫০ ছাড়াতে পারে, যার বেশিরভাগই এশিয়া ও আফ্রিকায়। এই মেগাসিটিগুলোই ভবিষ্যতের মানবজীবনের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হবে। বাংলাদেশের মতো দেশে ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় ১,৫০০–২,০০০ নতুন মানুষ বসতি স্থাপন করছে, ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৪৮,০০০ জন—এটি বিশ্বের সর্বোচ্চগুলোর একটি। এই পরিস্থিতি নগর পরিকল্পনার জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
বিশ্ব শহর দিবসের মূল বার্তা হলো—নগরকে প্রযুক্তিনির্ভর নয়, মানুষকেন্দ্রিক করতে হবে। “People-Centered Smart Cities” ধারণা এই বার্তার কেন্দ্রস্থলে। প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট ও ডিজিটাল গভর্ন্যান্সকে কাজে লাগিয়ে যদি নাগরিক জীবনের মান উন্নত করা যায়, তবে শহর হয়ে উঠবে টেকসই উন্নয়নের মূল চালক। কিন্তু প্রযুক্তি যদি কেবল ধনী শ্রেণির সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে সেটি নতুন বৈষম্যের জন্ম দেবে।
পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে শহর আজ জলবায়ু অভিযোজনের কেন্দ্র। IPCC-এর রিপোর্ট বলছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব শহরাঞ্চলে দ্বিগুণ গতিতে বাড়ছে। শহরের “Urban Heat Island” প্রভাবের কারণে শহরের তাপমাত্রা আশপাশের গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায় গড়ে ৩–৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বিশ্ব শহর দিবসের আহ্বান এই সংকট মোকাবিলায়—সবুজ অবকাঠামো, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি, শহুরে বন, ছাদ-বাগান ও পরিবেশবান্ধব নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে শহরকে অভিযোজনযোগ্য করে তুলতে হবে।
এ দিবসের অন্তর্নিহিত দার্শনিক বার্তা হলো, শহর মানবতার আয়না। শহরের মধ্যে প্রতিফলিত হয় সভ্যতার দিক ও অদিক উভয়ই—অগ্রগতি, প্রযুক্তি, জ্ঞান ও অর্থনীতি যেমন একদিকে, তেমনি দারিদ্র্য, একাকিত্ব, দূষণ ও বৈষম্য অন্যদিকে। তাই “Better City, Better Life” মানে কেবল উন্নত শহর নয়, বরং উন্নত মানুষ। শহর উন্নয়ন মানে এমন সমাজ নির্মাণ যেখানে প্রতিটি মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে পারে, যেখানে প্রকৃতি ও প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক হয়।
বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য এই দিবস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ঢাকাসহ প্রধান শহরগুলোকে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করতে হলে সমন্বিত নীতিমালা, নাগরিক অংশগ্রহণ, জলবায়ু অভিযোজন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দিকগুলোকে একসঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। বিশ্ব শহর দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়—শহর শুধুমাত্র বসবাসের স্থান নয়, এটি মানবতার পরীক্ষাগার। টেকসই শহর গঠনের মাধ্যমে আমরা কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশই নয়, মানব সভ্যতার স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারি।
নগরায়ণ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অনিবার্য অধ্যায়, যার শিকড় প্রাগৈতিহাসিক সমাজের কৃষি বিপ্লব থেকে শুরু হয়ে আধুনিক শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তিগত বিকাশ ও ডিজিটাল যুগে প্রবাহিত হয়েছে। শহর হলো সভ্যতার কেন্দ্রস্থল—যেখানে জ্ঞান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক উদ্ভাবনের মিলন ঘটে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি বছরের ৩১ অক্টোবর পালিত “বিশ্ব শহর দিবস” (World Cities Day) মানবজাতির এই নগর সভ্যতার যাত্রাকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার প্রতিশ্রুতির প্রতীক। দিবসটির মূল স্লোগান, “Better City, Better Life”, কেবল একটি উন্নয়নমূলক আহ্বান নয়; এটি মানব অস্তিত্বের সঙ্গে নগর-জীবনের নৈতিক ও দার্শনিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনারও একটি বৈশ্বিক অনুপ্রেরণা।
বিশ্ব শহর দিবস ২০১৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত এক প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি জাতিসংঘের নগর উন্নয়ন সংস্থা UN-Habitat-এর অধীনে পালিত হয়। দিবসটির সূচনা ঘটে ২০১০ সালে সাংহাই এক্সপো-র থিম “Better City, Better Life”-এর ধারাবাহিকতায়, যা আধুনিক নগরায়ণের ইতিবাচক দিক ও তার অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্বব্যাপী আলোচনায় আনে। UN-Habitat-এর মতে, বিশ্ব শহর দিবস হলো “Urban October”-এর সমাপনী দিবস—এক মাসব্যাপী বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম, যেখানে নগর পরিকল্পনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, আবাসন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও ডিজিটাল অবকাঠামো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। এই দিবসের প্রতিটি বছরের জন্য নির্ধারিত হয় একটি নির্দিষ্ট থিম ও একটি “Global Observance City”, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও নগর কর্তৃপক্ষ নিজেদের অভিজ্ঞতা, নীতি ও উদ্ভাবন উপস্থাপন করে।
নগরায়ণ আজকের পৃথিবীতে এক জটিল বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া। জাতিসংঘের “World Urbanization Prospects 2024” রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৫.১ বিলিয়ন মানুষ শহরে বসবাস করে—যা বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা পৌঁছাবে ৬.৮ বিলিয়নে, অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ তখন নগরভিত্তিক জীবনযাপনে সম্পৃক্ত হবে। শহরগুলো বর্তমানে বিশ্বের মোট স্থুল দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রায় ৮০ শতাংশ অবদান রাখে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী। এ এক দ্বৈত বাস্তবতা—একদিকে শহর মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন, অন্যদিকে জলবায়ু সংকট, বর্জ্য, জ্বালানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দূষণের কেন্দ্রবিন্দু।
UN-Habitat-এর ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ১.১ বিলিয়ন মানুষ এখনও অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বা স্লামে বসবাস করে, যাদের বেশিরভাগই এশিয়া ও আফ্রিকায়। এটি নগরায়ণের বৈষম্য ও কাঠামোগত অসমতার প্রমাণ। নগরায়ণ যদি মানব উন্নয়নের জন্য হয়, তবে তা অবশ্যই “inclusive urbanization”-এর পথে এগোতে হবে—যেখানে দরিদ্র, নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী নাগরিকদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। নগরায়ণের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক দিকই Sustainable Development Goals (SDGs)-এর লক্ষ্য ১১ (“Sustainable Cities and Communities”)-এর কেন্দ্রীয় বিষয়। এটি কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের প্রশ্নও।
অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শহর হলো এক সামাজিক প্রপঞ্চ। জর্জ সিমেল তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ “The Metropolis and Mental Life”-এ দেখিয়েছেন যে, শহর মানসিক উদ্দীপনা, প্রতিযোগিতা ও একাকিত্বের একটি মিশ্র রূপ—যেখানে ব্যক্তির আত্মপরিচয় ক্রমে জটিলতর হয়। আধুনিক শহর এই মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরকে বহুগুণ বাড়িয়েছে। প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেটাভার্স, স্মার্ট সিটি, ডিজিটাল সার্ভিস—সব মিলিয়ে নগরজীবন এখন তথ্য-নির্ভর বাস্তবতায় আবদ্ধ। “People-centered Smart City” ধারণাটি তাই মানবিক নগর পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা হিসেবে দেখা যায়, যেখানে প্রযুক্তি নয়, বরং নাগরিক সুবিধা, সামাজিক সহনশীলতা ও পরিবেশগত সামঞ্জস্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
শহর উন্নয়ন আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও পরিবেশ নীতির কেন্দ্রবিন্দু। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায় শহরে—বন্যা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জল সংকট, দূষণ ও জ্বালানি ঘাটতি এখন শহরের দৈনন্দিন বাস্তবতা। বাংলাদেশের মতো নিম্নভূমি উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৫ কোটিরও বেশি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হওয়ার ঝুঁকিতে, সেখানে টেকসই শহর পরিকল্পনা কেবল একটি উন্নয়ন লক্ষ্য নয়, বরং একটি অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল।
ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর মতো শহরগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইতিমধ্যে অবকাঠামোগত সক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ঢাকা মহানগর বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের আবাসস্থল, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৪৮,০০০ জনেরও বেশি। এমন বাস্তবতায় শহর পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নকে অবশ্যই বহুমাত্রিক করতে হবে—যেখানে সাশ্রয়ী আবাসন, গণপরিবহন, পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজ স্থান সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ডিজিটাল সংযোগ—সবকিছুই একসঙ্গে ভাবতে হয়।
শহর দিবসের দার্শনিক তাৎপর্য এখানেই—এটি মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে এক নতুন চুক্তির প্রতীক। শহর কেবল স্থাপত্য নয়, এটি এক জীবন্ত প্রাণ—যার হৃদস্পন্দন মানুষের স্বপ্ন, শ্রম, সংস্কৃতি ও সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। “Better City, Better Life” তাই কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়নের স্লোগান নয়; এটি একটি সামাজিক ন্যায়ের ডাক—যেখানে উন্নয়ন মানে কেবল অট্টালিকা নয়, বরং প্রতিটি মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা।
বিশ্ব শহর দিবস (World Cities Day) মানবসভ্যতার এক জটিল ও গতিশীল বাস্তবতার প্রতিফলন। এটি কেবল শহরের উন্নয়ন উদযাপনের দিন নয়—বরং নগরজীবনের বৈষম্য, পরিবেশগত ভারসাম্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই অর্থনীতির এক বিশ্লেষণাত্মক দিন। নগরায়ন আজ এক অনিবার্য বাস্তবতা—বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশেরও বেশি মানুষ শহরে বসবাস করছে, যা ১৯৫০ সালে ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। জাতিসংঘের অনুমান অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে। অর্থাৎ, প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। এই অনবরত নগরায়ন প্রক্রিয়া শহরগুলোর ওপর ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করছে—পরিবেশ, আবাসন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অবকাঠামো সবকিছুর ওপর।
তবুও শহর মানব সভ্যতার উদ্ভাবনের কেন্দ্র, অর্থনীতির হৃদস্পন্দন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতীক। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে শহরগুলো মোট জিডিপির প্রায় ৮০ শতাংশ উৎপাদন করে। আবার একই সঙ্গে শহরগুলোই বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ৭০ শতাংশেরও বেশি দায় বহন করছে। এই দ্বিমুখী বাস্তবতা আমাদের সামনে এক নৈতিক ও নীতিগত প্রশ্ন তোলে—কিভাবে আমরা এমন শহর গড়ে তুলব যা একদিকে উন্নয়নের ইঞ্জিন, অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ?
“Better City, Better Life”—জাতিসংঘ ঘোষিত এই মূল স্লোগান কেবল নগর পরিকল্পনার আহ্বান নয়, এটি মানবতার ভবিষ্যতের নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। শহর কেবল অবকাঠামোর সমষ্টি নয়, এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, নাগরিক অধিকার, অর্থনৈতিক সমতা ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির এক জীবন্ত চিত্র। একটি শহর তখনই সত্যিকার অর্থে “উন্নত” হয়, যখন সেটি সকল নাগরিকের জন্য সুযোগ, সেবা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।
বিশ্ব শহর দিবস তাই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়—নগরায়নের স্রোত থামানো যাবে না, কিন্তু তার দিকনির্দেশনা পরিবর্তন করা সম্ভব। আমাদের প্রয়োজন “smart” নয়, “sustainable” শহর—যেখানে প্রযুক্তি মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হবে, এবং উন্নয়ন প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত হবে। ভবিষ্যতের শহর হতে হবে মানবিক, অংশগ্রহণমূলক ও পরিবেশ-সচেতন—যেখানে প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠস্বর পরিকল্পনার অংশ হবে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, দ্রুত নগরায়ন যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতীক, তেমনি এটি দারিদ্র্য, আবাসন সংকট, পানি দূষণ, যানজট, বায়ু দূষণ ও সামাজিক বৈষম্যের এক চ্যালেঞ্জও বটে। বিশ্ব শহর দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা বা রংপুরের উন্নয়ন কেবল অবকাঠামোগত নয়; এটি একটি সমন্বিত সামাজিক প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষা, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণ দরকার।
সবশেষে বলা যায়, বিশ্ব শহর দিবসের মূল বার্তা হলো—“উন্নত শহর মানেই উন্নত জীবন, কিন্তু উন্নত জীবন কেবল তখনই সম্ভব, যখন শহর হবে সবার জন্য, প্রকৃতির জন্য, ভবিষ্যতের জন্য।” শহরের উন্নয়ন মানে ভবিষ্যতের উন্নয়ন; আর সেই ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব আজ আমাদের সবার। শহরকে মানবিক, সবুজ ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলাই এই দিবসের চূড়ান্ত আহ্বান—যা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG 11)-এর প্রাণকেন্দ্র: “Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.”
শহর মানে কেবল উঁচু ভবন, প্রশস্ত সড়ক বা ঝলমলে আলো নয়—শহর হলো এক জীবন্ত সামাজিক প্রাণতন্ত্র, যেখানে মানুষ, প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি একে অপরের সঙ্গে জটিলভাবে যুক্ত। বিশ্ব শহর দিবসের মূল বার্তা আমাদের এই মৌলিক সত্যটি মনে করিয়ে দেয়—একটি শহরের উন্নয়ন তখনই অর্থবহ, যখন সেটি মানুষকেন্দ্রিক হয়। শহর যতই প্রযুক্তিনির্ভর বা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হোক না কেন, যদি তাতে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার অনুপস্থিত থাকে, তবে সেই উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী নয়, বরং তা এক ধরনের বৈষম্যমূলক উন্নয়ন।
আজকের পৃথিবীতে নগরায়ন দ্রুততর হচ্ছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৫৮ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করছে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৬৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এই বিপুল নগরবাসীর জীবনের মান নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ সভ্যতার চরিত্র। অথচ অধিকাংশ শহরেই আজ দেখা যাচ্ছে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য—অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দূষণ, যানজট, দারিদ্র্য, বস্তিবাস, মানসিক চাপ, এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। ফলে শহর ক্রমে এক যান্ত্রিক বাস্তবতায় পরিণত হচ্ছে, যেখানে মানুষের মানবিক সম্পর্ক, পরিবেশের ভারসাম্য ও সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে।
এই প্রেক্ষাপটে বিশ্ব শহর দিবসের বার্তা এক নতুন দিকনির্দেশনা দেয়। এটি বলে—শহর উন্নয়নের লক্ষ্য কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, বরং মানবিক সুষম বিকাশ। শহরকে হতে হবে এমন এক পরিবেশ যেখানে মানুষ শুধু টিকে থাকবে না, বরং ভালোভাবে বাঁচবে। যেখানে শিশুরা নিরাপদে খেলবে, প্রবীণরা সম্মান পাবে, শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাবে, নারী ও প্রতিবন্ধীরা সমান সুযোগ পাবে। শহরের স্থাপত্য, পরিকল্পনা, পরিবহন ও প্রযুক্তি—সবকিছুর মধ্যেই এই মানবিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হতে হবে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বার্তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকাসহ বড় শহরগুলো দ্রুত বেড়ে উঠলেও সেখানে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। নগর পরিকল্পনায় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত থাকায় শহরগুলো ধীরে ধীরে জীবনবিরোধী হয়ে উঠছে। একদিকে আধুনিক স্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প, অন্যদিকে বস্তি, বর্জ্য, জলাবদ্ধতা ও সামাজিক বৈষম্য—এই দুই বাস্তবতা আমাদের শহরগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর প্রশ্ন তোলে। তাই এখন সময় এসেছে মানুষকেন্দ্রিক নগর দর্শন পুনর্গঠনের—যেখানে প্রতিটি উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হবে নাগরিক জীবনের মান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
শহর হলো মানব সভ্যতার আয়না। যদি শহর মানবিক হয়, তবে সভ্যতাও মানবিক হবে। যদি শহর অমানবিক হয়ে ওঠে, তবে প্রযুক্তি যতই অগ্রসর হোক না কেন, তা মানবকল্যাণ বয়ে আনবে না। তাই আজকের বার্তা একটাই—শহরকে যান্ত্রিক নয়, মানবিক করো; উন্নয়নকে কেবল কাঠামোয় নয়, মানুষে ও প্রকৃতিতে স্থাপন করো। এটাই বিশ্ব শহর দিবসের চূড়ান্ত আহ্বান, এবং ভবিষ্যৎ সভ্যতার টেকসই পথনির্দেশনা।
শহর উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ ও প্রকৃতির পুনর্মিলন
বিশ্ব শহর দিবসের মূল বার্তা স্পষ্ট ও গভীর—শহর কেবল অবকাঠামোর সমষ্টি নয়, এটি মানুষের জীবন, ন্যায্যতা ও প্রকৃতির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার এক মানবিক প্রতিশ্রুতি। নগর সভ্যতার এই যুগে আমরা বুঝতে পারছি, ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়ন শহর থেকেই নির্ধারিত হবে। কারণ আজ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ শহরে বসবাস করছে, অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে শহরের কেন্দ্র থেকে, এবং একই সঙ্গে পরিবেশ সংকটও শহরের মাঝেই সর্বাধিক প্রকট হচ্ছে। এই দ্বৈত বাস্তবতা আমাদের সামনে এক গভীর প্রশ্ন তুলে ধরছে—আমরা কেমন শহর চাই: যান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক, নাকি মানবিক ও টেকসই?
জাতিসংঘ ঘোষিত “Better City, Better Life” স্লোগানটি মূলত এক নৈতিক ও দার্শনিক ঘোষণা—শহর তখনই “better” হবে, যখন তা মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধ হবে। এটি শুধুমাত্র ভবন, সড়ক, সেতু ও প্রযুক্তির বিষয় নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, নাগরিক অধিকার, সংস্কৃতি ও মানব মর্যাদার বিষয়।
একটি শহরের সাফল্য মাপা উচিত কতোজন মানুষ সুখে বাস করছে, কতোজন শিশু নিরাপদে বেড়ে উঠছে, কতোজন নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সমান সুযোগ পাচ্ছে—এই সূচক দিয়ে; GDP বা টাওয়ারের উচ্চতা দিয়ে নয়।
আজকের বিশ্ব শহর দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নগরায়ণ থামানো যাবে না, কিন্তু তার চরিত্র পরিবর্তন করা সম্ভব। শহরকে হতে হবে এমন এক “মানবিক ইকোসিস্টেম”, যেখানে প্রযুক্তি মানুষের সেবায় ব্যবহৃত হবে, আর উন্নয়ন হবে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নগর পরিকল্পনা তাই এখন এক নতুন দর্শনের দাবি রাখে—যেখানে স্মার্ট সিটি নয়, পিপল-সেন্টার্ড সিটি গড়ে তোলাই হবে লক্ষ্য।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বার্তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের শহরগুলো দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে যানজট, দূষণ, অসমতা ও মানসিক চাপ। ঢাকা মহানগরের প্রতিটি ভবন যদি কংক্রিটের প্রতীক হয়, তবে তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি হলো আমাদের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি—যার স্বপ্ন, শ্রম ও মানবিক প্রয়োজনই শহর উন্নয়নের প্রকৃত মানদণ্ড। এই মানুষদের কেন্দ্র করে শহরকে নতুনভাবে ভাবা—এটাই বিশ্ব শহর দিবসের সারবস্তু।
বিশ্ব শহর দিবস তাই কেবল নগর উদযাপনের দিন নয়, এটি এক নৈতিক আত্মসমালোচনার দিন। এটি আমাদের প্রশ্ন করতে শেখায়—শহর কি সত্যিই সবার? নাকি এটি কেবল বিশেষ সুবিধাভোগীদের? যদি শহর মানবিক না হয়, তবে তার উন্নয়নও শূন্যার্থক। শহরকে মানুষের, সংস্কৃতির ও প্রকৃতির সংলগ্নতায় ফিরিয়ে আনা—এই সচেতনতা তৈরি করাই এই দিবসের সবচেয়ে বড় অর্জন।
অতএব, বিশ্ব শহর দিবসের বার্তা মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ হয়ে দাঁড়ায়— শহরকে যান্ত্রিক নয়, মানবিক করো; উন্নয়নকে কেবল কাঠামোয় নয়, মানুষ ও প্রকৃতিতে স্থাপন করো। যে শহর মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, প্রকৃতিকে সম্মান করে, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী আশ্রয় গড়ে তোলে—সেই শহরই প্রকৃত অর্থে “Better City, Better Life”-এর বাস্তব প্রতিফলন। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির শহরই হবে আগামী পৃথিবীর টেকসই ও শান্তিময় সভ্যতার প্রতীক।
লেখক : গণমাধ্যমকর্মী।
পাঠকের মতামত:
- ইসির প্রতীক তালিকায় এবার ‘শাপলা কলি’
- ‘গণভোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন প্রধান উপদেষ্টা’
- এবার জুলাই শহীদদের লাশ শনাক্তে আনা হবে বিদেশি বিশেষজ্ঞ
- পাট্টায় বিএনপির মিছিল সমাবেশ
- হিন্দু সম্প্রদায়ের জমিতে রাস্তা নির্মাণে বাধা দেওয়ায় পাঁচ নারীকে পিটিয়ে জখম
- বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস: খরচ কমাও, সচেতনতা বাড়াও
- চাটমোহরে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ী নিহত
- জুলাইয়ের সরকারি গেজেট থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন জুলাই যোদ্ধা আবরার
- রবীন্দ্র সংগীতে প্রথমস্থান অধিকার করেছে প্রিয়ন্তী পোদ্দার
- টোয়াবের আয়োজনে তিন দিনের পর্যটন মেলা শুরু
- ফরিদপুরে নারীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ৪ জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
- শ্যামনগর হাসপাতালের চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন
- শিক্ষা কর্মকর্তাকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ
- ধর্ষণ মামলা দিয়ে জেলে পাঠানো বিকাশ গাইনের রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর
- কাপ্তাইয়ের তম্বপাড়া ধর্মরত্ন বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান ও কোংন্ওয়ং জাদিতে বুদ্ধ ধাতু প্রতিস্থাপন
- দিনাজপুরে কৃষি প্রণোদনায় বিনামূল্যে ৭৭৫ কৃষককে বীজ ও সার প্রদান
- ঝিনাইদহে নবগঙ্গা নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
- নোয়াখালীতে সাবেক সেনা কর্মকর্তার জায়গা দখল ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগ
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরম পূরণ ও ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে গোপালগঞ্জে মানববন্ধন
- কাপাসিয়ায় কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ-সার প্রদান
- শহর কেবল অবকাঠামো নয়, এক মানবিক পরিবেশ
- সাতক্ষীরায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৮ দোকান পুড়ে ছাই
- ফোন করে চাঁদা দাবি, থানায় অভিযোগের পর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ
- সালথার ইউসুফদিয়া স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত
- একক গানে কানেকটিকাটের দর্শকদের মুগ্ধ করলেন ব্রিয়ানা বিশ্বাস
- খ্যাতিমান সাংবাদিক রতন সরকারের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী আজ
- প্রকাশিত হয়েছে এস এম জাহিদ হাসানের ভ্রমণগ্রন্থ ‘চলতি পথের বাঁকে’
- সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে দিনরাত কথা বলছে ‘বিবর্তন যশোর’
- ‘শিল্পের প্রতি টান থেকেই কলকাতায় যাওয়া’
- ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে অ্যাম্বুলেন্সে বাসের ধাক্কা, নিহত ৫
- ফেক আইডি থেকে উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক পোস্ট, পাথরঘাটায় সংবাদ সম্মেলন
- ক্রিকেটের মাধ্যমে ভালো নাগরিক তৈরি করতে চান বিসিবি সভাপতি
- ‘ক্ষমতা ছেড়ে দিন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবো’
- র্যাংকিংয়েও আফগানিস্তানকে টপকে গেল বাংলাদেশ
- বাভাসি’র বিচারক হলেন শামীম জামান
- পাকিস্তানের মাটিতে শেখ মুজিবের ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি টিকবে না
- ‘স্বৈরাচারের দোসররা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে’
- ফোবানার নতুন সভাপতি বেলাল, নির্বাহী সচিব রউফ
- ‘ফ্যাসিস্ট আ.লীগের প্রত্যাবর্তনের সব দরজা বন্ধ করতে হবে’
- ২০২৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল মাদ্রিদে
- ঢাবিতে কারাগার, সংস্কার ও পুনর্বাসন বিষয়ক সেমিনার সোমবার
- সব দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানালেন মির্জা ফখরুল
- ‘বাংলাদেশের জার্সি আর গায়ে দেওয়া হলো না’
- ডেঙ্গুতে একদিনে চারজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১১৪৩
- অবশেষে চালু হলো চীন-ভারত সরাসরি ফ্লাইট
-1.gif)
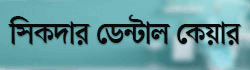

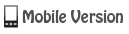








.jpg&w=60&h=50)





.jpeg&w=60&h=50)









.jpeg&w=60&h=50)












.jpg&w=60&h=50)
-12.07.25.jpg&w=60&h=50)


.jpg&w=60&h=50)





















