মানবিক দায়বোধ থেকে নীতিগত সংস্কার: সড়ক–নিরাপত্তার বৈশ্বিক পাঠ

ওয়াজেদুর রহমান কনক
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত মানুষের স্মরণকে কেন্দ্র করে যে বৈশ্বিকভাবে একটি স্মরণ–অনুশীলন গড়ে উঠেছে, তার পিছনে গভীর মানবিক, সামাজিক ও নীতিগত যৌক্তিকতা রয়েছে। এই যৌক্তিকতা মূলত এক তীব্র বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে—বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন হাজারো পরিবার হঠাৎ করেই তাদের প্রিয় মানুষটিকে হারায়, অথবা তাকে চিরস্থায়ী অক্ষমতার সঙ্গে বাঁচতে দেখে। সড়ক দুর্ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি আধুনিক নগরায়ণ, পরিবহন ব্যবস্থা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সামাজিক আচরণের অসংগতি থেকে জন্ম নেওয়া এক বহুমাত্রিক সংকট। তাই এই স্মরণচর্চা শুধুমাত্র আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি সমাজের নৈতিক ও কাঠামোগত ব্যর্থতার বিরুদ্ধে একটি নীরব ও শক্তিশালী জবাবদিহির দাবি।
দিবসটি পালনের যৌক্তিকতা প্রথমেই উঠে আসে মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন থেকে। সড়কে মৃত্যু হঠাৎ ঘটে—প্রায়ই অবহেলা, ত্রুটি, দায়িত্বহীনতা বা নীতিগত ব্যর্থতার ফলে। পরিবারগুলো এই মৃত্যুকে কোনোভাবেই স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে পারে না; কারণ এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধযোগ্য। নিহতদের স্মরণ তাই তাদের মর্যাদাকে সম্মান জানায় এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজকে মনে করিয়ে দেয় যে প্রতিটি মানুষই নিরাপদভাবে চলাফেরা করার মৌলিক অধিকার রাখে। এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে তা শুধু একটি দুর্ঘটনা নয়; এটি একটি সুস্পষ্ট ন্যায়ের ঘাটতি।
যৌক্তিকতার আরেকটি মূল উৎস হলো আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের দীর্ঘমেয়াদি সংকট প্রকাশ করা। দুর্ঘটনায় অক্ষম হয়ে যাওয়া মানুষদের জীবন প্রতিদিন নতুন চ্যালেঞ্জে ভরা—চিকিৎসা, কাজ হারানো, পরিবারে আর্থিক চাপ, মানসিক আঘাত, পুনর্বাসনের অভাব—এসব সমস্যার অনেকটাই সামাজিক আলোচনার বাইরে থেকে যায়। এই স্মরণ–অনুষ্ঠান দৃশ্যমান করে যে সড়ক–নিরাপত্তা শুধু একটি ট্রাফিক বিষয় নয়; এটি জনস্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও মানবাধিকারের সমন্বিত প্রশ্ন।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যৌক্তিকতা হলো সড়ক–নিরাপত্তা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অগ্রাধিকার তৈরি করা। মৃত্যুর সংখ্যা যতই বাড়ুক, তা যদি নীতি–স্তরে তেমন প্রভাব সৃষ্টি না করে, তবে কোনো পরিবর্তনই কার্যকর হয় না। স্মরণচর্চা সেই শূন্যস্থান পূরণ করে—কারণ এটি একটি আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় চাপ তৈরি করে; সরকার, নীতিনির্ধারক, পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক সমাজকে বাধ্য করে ব্যবস্থাগত দুর্বলতা স্বীকার করতে এবং নিরাপদ সড়কের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে। এই স্মরণই বহু দেশে আইন শক্তিশালী করা, দ্রুতগতির নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণ, শিশু ও পথচারী–সুরক্ষা নিশ্চিত করা, এবং জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে ভূমিকা রেখেছে।
দিবসটি পালনের আরেকটি যৌক্তিকতা হলো নিরাপদ আচরণের সংস্কৃতি গড়ে তোলা। সমাজে যখন নিহতদের স্মরণ করা হয়, তখন চালক, পথচারী, যাত্রী, তরুণ প্রজন্ম—সবার কাছে একটি বার্তা যায় যে সড়কে দায়িত্বহীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়, বরং সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ। এভাবে স্মরণচর্চা আচরণগত পরিবর্তনের জন্য একটি নৈতিক ভিত্তি তৈরি করে, যা আইন প্রয়োগের বাইরেও সচেতনতার মাধ্যমে জীবনরক্ষার পথ খুলে দেয়।
সবশেষে, এই স্মরণচর্চা সামগ্রিকভাবে একটি ন্যায়–সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবির সঙ্গে যুক্ত—যেখানে কোনো মৃত্যু অবহেলার কারণে ঘটে না, কোনো পরিবার অন্যায্য ক্ষতি বইতে বাধ্য হয় না, এবং যেখানে নিরাপদ সড়ক মানবজীবনের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়। তাই দিবসটি পালনের যৌক্তিকতা শুধু স্মৃতি রক্ষায় নয়; বরং এক নিরাপদ, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তোলার অনিবার্য সামাজিক অঙ্গীকারে।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের স্মরণ যে গভীর মানবিক দায়বোধের জন্ম দেয়, তার স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা—এমন কর্মপরিকল্পনা যা শোককে পরিবর্তনের শক্তিতে রূপান্তর করে। উপসংহারে করণীয় বিষয়ে যে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আসে, তা কেবল কিছু নীতিগত নির্দেশ নয়; বরং একটি সমাজ–রাষ্ট্রের নতুন সড়ক–নৈতিকতা গড়ে তোলার পথরেখা।
প্রথমত, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবকাঠামোই সবচেয়ে ভিত্তিগত জায়গা। নিরাপদ সড়ক নকশা—দ্রুতগামী ও ধীরগতির যানবাহনের পৃথক লেন, পথচারী সেতু, আন্ডারপাস, রাউন্ডঅ্যাবাউট, সিগন্যাল ব্যবস্থা, আলোকসজ্জা—এসবের আধুনিক পুনর্গঠন ছাড়া দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব নয়। বর্তমানে যে “উন্নয়ন” হয়, তার বড় অংশই সড়কের গতিমুখ বাড়ায়, নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে না; তাই উন্নয়নের ধারণায়ই নিরাপত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রয়োজন সড়ক নির্মাণে মাননিয়ন্ত্রণ, কাজের গুণগত তদারকি এবং দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের বাধ্যবাধকতা।
দ্বিতীয়ত, আইন প্রয়োগে সমন্বিত ও কঠোর ব্যবস্থা জরুরি। গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ক্যামেরা–ভিত্তিক মনিটরিং, স্বয়ংক্রিয় জরিমানা, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের কঠোরতা—এসব আন্তর্জাতিকভাবে সফল পদ্ধতি। বাংলাদেশসহ অনেক দেশে লাইসেন্সবিহীন চালনা, ভুয়া লাইসেন্স, অতিরিক্ত যাত্রী, প্রতিযোগিতামূলক চালনা ও ক্লান্ত চালকের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট; তাই এসব ক্ষেত্রে জিরো–টলারেন্স নীতি অপরিহার্য। একইসঙ্গে পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে মানবিক ও নিরাপত্তাকেন্দ্রিক কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে আইনের প্রয়োগ শ্রমিকের জীবিকাকে বিপন্ন না করে বরং তাকে দক্ষ, দায়িত্বশীল ও সুরক্ষিত করে।
তৃতীয়ত, যানবাহনের নিরাপত্তা মান উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। পুরনো, অপ্রস্তুত, ব্রেক–লাইটহীন, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ি বাতিল করার পাশাপাশি নতুন গাড়িতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য—এয়ারব্যাগ, ABS, স্ট্যান্ডার্ড সেফটি রেটিং—অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। গণপরিবহনে সীটবেল্ট বাধ্যতামূলক করা, মোটরসাইকেলে মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহার, ট্রাক–বাসে গতি নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইনস্টল—এসব পদক্ষেপকে আইনি ও বাস্তবায়নের কাঠামোতে আনতে হবে।
চতুর্থত, চালক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা–উন্নয়ন ও মানসিক স্বাস্থ্য–সংক্রান্ত কাঠামো নতুনভাবে সাজাতে হবে। চালকেরা প্রায়ই দীর্ঘ সময় বিশ্রামহীন কাজ করেন, তাদের অনেকেই ট্রমা, ক্লান্তি, চাপ ও অনভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গাড়ি চালান—এই বাস্তবতা পরিবর্তন করতে হবে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন, বিশ্রাম–পদ্ধতি, লাইসেন্স নবায়নে দক্ষতা–পরীক্ষা—এসব ব্যবস্থা চালু না হলে সিস্টেমিক নিরাপত্তা সম্ভব নয়।
এছাড়া জরুরি চিকিৎসা–সেবার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী না করলে দুর্ঘটনা–পরবর্তী মৃত্যুহার কমানো সম্ভব নয়। “গোল্ডেন আওয়ার”–এর ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স, প্রশিক্ষিত ফার্স্ট–রেসপন্ডার, নিকটবর্তী হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসা সুবিধা ও রুট-ক্লিয়ার সিস্টেম থাকা জরুরি। উন্নত দেশে যেমন হাইওয়ে মেডিকেল রেসপন্স ইউনিট রয়েছে, বাংলাদেশেও এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। প্রতিটি মিনিট এখানে জীবনরেখা নির্ধারণ করে।
একই সঙ্গে জনসচেতনতা একটি দীর্ঘমেয়াদি ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্র। নিরাপদ আচরণ—হেলমেট, সিটবেল্ট, জেব্রাক্রসিং ব্যবহার, মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা, মাদকমুক্ত চালনা—এসবকে শুধু প্রচারণায় নয়, বিদ্যালয়ের পাঠক্রম, স্থানীয় সরকার কার্যক্রম এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গল্পভিত্তিক বার্তা, দুর্ঘটনাজনিত বাস্তবতা, পরিবার–কেন্দ্রিক প্রভাব—এসব মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগাতে সহায়ক হতে পারে।
সবশেষে, মানবিক সমর্থন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে জাতীয় কর্মসূচিতে যুক্ত করা জরুরি। নিহত ও আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, কর্মক্ষমতা হারানো ব্যক্তিদের জন্য পুনঃকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ, শিশুদের শিক্ষাবৃত্তি, দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল—এসব ব্যবস্থা স্মরণচর্চাকে বাস্তব মানবিকতায় পরিণত করে। একইসঙ্গে, সড়ক-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা জোরদার করতে হবে; নির্ভুল তথ্য ছাড়া কোনো নীতি কার্যকর হয় না।
সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি মানুষের স্মৃতি আমাদের দুর্বলতার মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং আমাদের দায়িত্বের পথনির্দেশ দেয়। এই স্মরণ যদি সত্যিই অর্থবহ হয়, তবে তা নীতিমালা, অবকাঠামো, আচরণ ও মানবিক সহায়তা—সবক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটিয়ে নিরাপদ সড়কের সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। জীবন রক্ষার জন্য নিরাপদ সড়ক কোনো বিলাসিতা নয়; এটি রাষ্ট্র ও সমাজের অপরিহার্য নৈতিক দায়, যা আজই বাস্তবায়নের জন্য সুসংহত পদক্ষেপ দাবি করে।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত মানুষদের স্মরণ করার যে বৈশ্বিক প্রয়াস গড়ে উঠেছে, তার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজীবনের প্রতি সম্মান ও নিরাপত্তার নৈতিক দায়বোধকে সমাজের সামনে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য মূলত চারটি গভীর মানবিক ও নীতিগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে—যেখানে প্রতিটি সড়ক–মৃত্যুকে কেবল একটি সংখ্যা নয়, বরং একটি পরিবারের ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, হারিয়ে যাওয়া ভবিষ্যৎ এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতার নির্মম প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়। তাই এই স্মরণচর্চার লক্ষ্য প্রথমেই হচ্ছে নিহতদের মর্যাদাকে নিশ্চিত করা; তাদের জীবনকে অবজ্ঞার সংখ্যা হিসেবে গণ্য না করে সামাজিক স্মৃতির অংশ করে তোলা, যাতে নীতিনির্ধারকের কাছে প্রতিটি প্রাণের মূল্য স্পষ্ট ও অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।
একই সঙ্গে এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আহত ও অক্ষম হয়ে যাওয়া লাখো মানুষের দুর্বিষহ বাস্তবতার দিকে বিশ্ব-সমাজের মনোযোগ টেনে আনা। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা, পুনর্বাসন, জীবিকার সংকট, মানসিক আঘাত—এসবই এক ধরনের নীরব ট্র্যাজেডি, যা অধিকাংশ সময় জনআলোচনার বাইরে থেকে যায়। স্মরণ–অনুষ্ঠানগুলো মানুষের এই সংগ্রামকে দৃশ্যমান করে, পরিবারগুলোর কষ্টকে প্রকাশিত করে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর নৈতিক কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়।
এ উদ্দেশ্যের আরেকটি অন্তরের সুর হলো জবাবদিহি সৃষ্টি করা। সড়ক-ব্যবস্থাপনা, আইনপ্রয়োগ, অবকাঠামো, যানবাহনের নিরাপত্তা মান, চালকের প্রশিক্ষণ—যে যেখানে ঘাটতি আছে, তা স্পষ্ট করে দেখানোই এই স্মরণচর্চার একটি মৌলিক লক্ষ্য। কারণ সড়কে মৃত্যু “অপরিহার্য” নয়; অধিকাংশই প্রতিরোধযোগ্য। তাই স্মরণই এখানে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়—যেখানে নিহতদের স্মৃতিকে সম্মান দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ভুলগুলো স্বীকার করা, ব্যর্থতার দায় নেওয়া, এবং ভবিষ্যতে এমন মৃত্যু কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।
এটির আরেকটি গভীর উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ সড়কের চেতনায় শিক্ষিত করা। সমাজ যখন নিহতদের কথা স্মরণ করে, তখন তা ভবিষ্যতের চালক, পথচারী, নীতি–নির্ধারক ও অভিভাবকদের কাছে একটি সতর্ক বার্তা পাঠায়—মানবজীবনের মূল্য অসীম এবং নিরাপত্তা অবহেলার কোনো জায়গা নেই। এই সচেতনতা ধীরে ধীরে আচরণগত পরিবর্তনের জন্ম দেয়; আইন মানার সংস্কৃতি তৈরি করে, দায়িত্বশীল চালনা, হেলমেট-সিটবেল্ট ব্যবহার, গতি নিয়ন্ত্রণ, মাদক–বর্জন—এসবকে সামাজিক মূল্যবোধের অংশে পরিণত করে।
অবশেষে, এই স্মরণচর্চার লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ সড়ককে মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ যেমন পরিচ্ছন্ন পানি, ন্যায্য বিচার বা নিরাপদ পরিবেশের অধিকার দাবি করে, তেমনই নিরাপদ চলাচলের সুযোগও মৌলিক অধিকার। স্মরণ–উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে এই অধিকারকে আন্তর্জাতিক নীতিমালায় ও জাতীয় শাসনব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার প্রচেষ্টা চলে, যা দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্য, টেকসই ও সুরক্ষিত সড়কব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।
এইভাবে, সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্মরণ করার উদ্দেশ্য আসলে শোক থেকে পুনর্গঠন, স্মৃতি থেকে পরিবর্তন, এবং মানবিক বেদনা থেকে ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তা নির্মাণের এক ব্যাপক সামাজিক অঙ্গীকার—যার কেন্দ্রবিন্দু একটাই: যাতে আর কোনো পরিবার একই বেদনার সম্মুখীন না হয়।
প্রতিবছর নভোম্বরের তৃতীয় রবিবার (বহুজাতিকভাবে পালন করা ১৭ নভেম্বরও পড়তে পারে) বিশ্ববাসী সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ও আহত পরিবারদের স্মরণে দাঁড়ায় — World Day of Remembrance for Road Traffic Victims। এই দিনটি ১৯৯৩ সালে ব্রিটেনে শুরু হয় এবং ২০০৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়ে “সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও তাদের পরিবারদের যথাযথ শ্রদ্ধানুযায়ী স্মরণ” হিসেবে পালিত হওয়ার সুস্পষ্ট মানদণ্ড পেয়েছে।
স্মৃতির এই দিনে যে সংখ্যা-পটভূমি সামনে আসে, তা হৃদয়হত করে এবং নীতিনির্ধারকদের প্রতি জোরালো আহ্বান ছাড়ে। WHO–এর সাম্প্রতিক Global Status Report on Road Safety 2023 অনুযায়ী ২০২১ সালে অনুমানিতভাবে বিশ্বজোড়ে প্রায় ১.১৯ মিলিয়ন (১,১৯০,০০০) মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন — যা মোট জনসংখ্যার প্রতি প্রায় ১৫ জন-মৃত্যু প্রতিটি ১০০,০০০ জনে। একই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সড়ক-আঘাত এখন ৫–২৯ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে মৃত্যুর শীর্ষ কারণ; প্রাণহানিতে পথচারী, সাইকেলচালক ও মোটরসাইকেলচালকরা অনুপাতগতভাবে বেশি ঝুঁকিতে আছে। এই বড় সংখ্যাগুলো শুধু পরিসংখ্যা নয় — এটি প্রতিটি সংখ্যার পেছনে থাকা পরিবারের ধ্বংস-স্তব্ধতা, চিকিৎসা-খরচ, জীবিকা ও মানসিক আঘাতের সমষ্টিগত বেদনা।
এশিয়া, আফ্রিকা ও নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশগুলোতে সড়ক নিরাপত্তা সবচেয়ে দুর্বল এবং তাদের জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। WHO–এর দেশভিত্তিক প্রোফাইল অনুযায়ী বাংলাদেশেও সড়ক দুর্ঘটনা একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য—সমস্যা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ২০২৩ সালের বাংলাদেশ প্রোফাইলে উল্লেখ আছে, ২০২১ সালে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় আনুমানিক ৩১,৫৭৮ জন প্রাণ হারিয়েছে — অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় একশতাধিক মানুষই এই ধরনের ঘটনায় জীবন হারাচ্ছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হচ্ছে; দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোতে এর প্রভাব অতি গভীর। দেশীয় সার্ভে ও সাম্প্রতিক বিশ্লেষণগুলো দেখায় ঢাকাসহ ঘনবসতি অঞ্চলগুলোতে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে বেশি, এবং দ্রুতগতির যানবাহন, দায়িত্বহীন চালনাপথ, অপর্যাপ্ত পথচারী-ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও দ্রুত-প্রতিক্রিয়া চিকিৎসা-সেবার অভাব নিয়মিত কারণ হিসেবে চিহ্নিত।
পরিসংখ্যানে আরও কিছু করুণ দিক লক্ষ্যণীয়: WHO–র ২০২3 রিপোর্টে বলা হয়, গত কয়েক বছরে বিশ্বব্যাপী নীতিগত প্রচেষ্টা ও নিরাপত্তা উদ্যোগের ফলে মোট মৃত্যুর হার কিছুটা কমেছে — ২০১৮-এর পরিসংখ্যান (প্রায় ১.৩৫ মিলিয়ন) থেকে ২০২১ পর্যন্ত সংখ্যা নেমে এসেছে ১.১৯ মিলিয়নে; তবু বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বানচাল — দ্রুত এগোতে না পারলে আগামী দশকে লক্ষ লক্ষ জীবন সংকটাপন্ন থাকবে। দ্রুতগতির সীমাবদ্ধতা, নিরাপদ রাস্তাঘাত, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার, নীরব ড্রাইভিং/ড্রাগ-সদ্ব্যবহার রোধ এবং কার্যকর জরুরি চিকিৎসাসেবা — এগুলোই ক্ষতি কমাতে প্রমাণভিত্তিক হস্তক্ষেপ।
World Day of Remembrance কেবল সংখ্যা পাঠ করে না; এটি নীতিনির্ধারককে জিজ্ঞাসা করে—এই মৃত্যুগুলো বন্ধ করতে আমরা কী করছি? এটি সমাজকে স্মরণ করায় যে শাস্তিমূলক আইনপ্রয়োগের পাশাপাশি অবকাঠামো বিনিয়োগ (নিরাপদ সড়ক, আলোকসজ্জা, সাইকেল ও পথচারী লেন), যানবাহন-নিরাপত্তা মান তাৎপর্যপূর্ণ, এবং চালক-শিক্ষা ও জনসচেতনতা কর্মসূচি অবিলম্বে শক্তিশালী করা দরকার। একই সঙ্গে হতাহত পরিবার ও রেসকিউ কর্মীদের প্রতি মানসিক সহায়তা, আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-পরিকল্পনা থাকা অতীব জরুরি।
স্মরণ দিবসটির মানে হচ্ছে কেবল অতীতকে শ্রদ্ধা করা নয়—এটি ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার সামাজিক অঙ্গীকার। প্রতিটি জীবন যে অনন্য তা আমরা ভুলতে পারি না; প্রতিটি পরিসংখ্যান হল একটি সুযোগ—নিরাপদ নীতি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নতুন প্রাণ বাঁচানোর। আজকের স্মরণে আমরা নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াই, আহতদের দ্রুত ও সম্মানজনক চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবি জানাই, এবং সরকার ও নাগরিক সমাজকে আহ্বান জানাই — নির্দিষ্ট সময়সীমা ও সম্পদ বরাদ্দ করে বাস্তবতাভিত্তিক পথচিত্র গ্রহণ করুন, যাতে পরবর্তী স্মরণদিবসে সংখ্যা কমে এবং পথগুলো নিরাপদ হয়।
লেখক : গণমাধ্যমকর্মী।
পাঠকের মতামত:
- ঈশ্বরদীতে নেসকোর প্রি-পেইড মিটার বাতিলের দাবিতে গণঅনশন
- গ্রামীণ ব্যাংকের শেরপুর শাখায় আগুন দেওয়ার চেষ্টা
- শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শিশু পার্ক আধুনিকায়নের দাবিতে কুষ্টিয়ায় মানববন্ধন
- কবরস্থানে পার্ক নির্মাণ করে বেহায়াপনার অভিযোগ
- টুঙ্গিপাড়ায় দুই দিনে দুই যুব মহিলালীগ নেত্রী গ্রেপ্তার
- সুবর্ণচরে শ্রমিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ
- টাঙ্গাইলে অর্ধকোটি টাকার হেরোইনসহ কারবারি গ্রেফতার
- অপরিণত নবজাতকের জীবন রক্ষায় হোমিওপ্যাথি
- খুলনা বরিশালের ৭ জেলায় অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ডাক
- ঈশ্বরদীতে দুই ছেলেসহ মাকে ৬ ঘণ্টা জিম্মি করে ডাকাতি
- আমাদের বন্দী অর্থনীতি: বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার অদৃশ্য স্থাপত্যের ভিতর
- মধ্যরাতে ঈশ্বরদী–ঢাকা মহাসড়কে টায়ারে আগুন, আতঙ্কে সাধারণ মানুষ
- লালপুরে দুই কমিটির দ্বন্দ্বে গোঁসাই আশ্রমের নবান্ন উৎসব নিয়ে শঙ্কা
- মানবিক দায়বোধ থেকে নীতিগত সংস্কার: সড়ক–নিরাপত্তার বৈশ্বিক পাঠ
- ‘শেখ হাসিনার রায় ঘিরে নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা রুখে দিতে হবে’
- দিনাজপুর-২ আসনে বিএনপির ঘোষিত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে উত্তাল
- সালথায় ইউপি সদস্য আবুল হাসান গ্রেপ্তার
- নড়াইলে দুর্বৃত্তের হামলায় ব্যবসায়ী জখম, অভিযুক্ত গ্রেফতার
- নোয়াখালীতে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা
- ঢাকা-গোপালগঞ্জসহ চার জেলায় নিরাপত্তার দায়িত্বে বিজিবি
- ‘ভোটে ব্যাঘাত ঘটানোর মতো শক্তি আ. লীগের নেই’
- যশোর বোর্ডে এইচএসসিতে নতুন করে জিপিএ-৫ পেল ৭২ জন
- ‘কোনো গোষ্ঠী বিশেষের কাছে যেন আমাদের অর্থনীতি জিম্মি না থাকে’
- কোক স্টুডিও বাংলায় গাইবেন রুনা লায়লা
- কাশিয়ানীতে গভীর রাতে গাছ ফেলে মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা
- নিমে নিরাময় হয় যে সব রোগের
- ‘ঐ চেয়ার নির্লজ্জদের জন্যই’
- নিরাপদ সমুদ্র পর্যটনের জন্য জরুরি নির্দেশনা
- হাজারো মানুষের তারুণ্যের জাগরণ ‘অনন্যা’
- ‘ক্ষমতা ছেড়ে দিন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবো’
- উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন
- আবারো রগ কেটে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে : মোমিন মেহেদী
- ‘ভারত নোংরা খেলা খেলতে পারে, দ্বিমুখী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত পাকিস্তান’
- রাজশাহীতে আশুরা পালনে মানতে হবে যেসব বিধিনিষেধ
- ‘সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন’
- মেক্সিকোতে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৪
- আজ জালালপুর গণহত্যা দিবস
- অপরিণত নবজাতকের জীবন রক্ষায় হোমিওপ্যাথি
- ‘বঙ্গবন্ধু একটি সুন্দর ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন’
- ডহর রামসিদ্ধি : নৌকার গ্রাম
- সবার আমি ছাত্র
- মামদানির জয়, প্রথম মুসলিম মেয়র পেলো নিউইয়র্ক
- টাঙ্গাইলে অর্ধকোটি টাকার হেরোইনসহ কারবারি গ্রেফতার
- ভণ্ডামি আর নাটক থেকে মুক্তি চান আঁখি আলমগীর
- গাজীপুরে ৩৯ দফা দাবিতে সাংবাদিক ইউনিয়নের বিক্ষোভ
১৬ নভেম্বর ২০২৫
- অপরিণত নবজাতকের জীবন রক্ষায় হোমিওপ্যাথি
- মানবিক দায়বোধ থেকে নীতিগত সংস্কার: সড়ক–নিরাপত্তার বৈশ্বিক পাঠ
-1.gif)
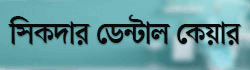

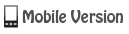













-4.jpeg&w=60&h=50)



















-3.jpeg&w=60&h=50)


.jpg&w=60&h=50)
-12.07.25.jpg&w=60&h=50)


.jpg&w=60&h=50)





















