নব্য মীরজাফর, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ ইলিয়াস
জাতি হিসেবে বাঙালিকে সরাসরি রসিক জাতি বলা যাবে না হয়তো, কিন্তু বাঙালির রসবোধ বা ‘সেন্স অব হিউমার’ বেশ প্রবল। এর ব্যবহার আমরা প্রাত্যহিক জীবনেও দেখতে পাই। আশপাশের মানুষের ব্যবহার, সামাজিক রীতি, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে আমরা উপমা হিসেবে ব্যবহার করি। আবার কোনো কোনো সময় ব্যক্তির পরিচয়কে ঊর্ধ্বে রেখে সেই ব্যক্তির নামকে ব্যবহার করি বিশেষণ কিংবা হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক শব্দ হিসেবে। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির চেয়ে আমরা বেশ এগিয়েই আছি বলা যায়। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ঐতিহাসিক চরিত্রের ব্যবহারেও আমরা সিদ্ধহস্ত। এই যেমন ‘মীরজাফর’ শব্দটি। এটি একটি ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও চরিত্রটির বিশ্বাসঘাতকতা পুরো নামটিকেই একটি গালিতে পরিণত করেছে। আমরাও প্রতিদিনের জীবনে চারপাশের বিশ্বাসঘাতক মানুষদের ‘মীরজাফর’ বলে ডেকে থাকি। আবার বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক হিসেবে ‘মীরজাফরি’ শব্দটিও ব্যবহার করতে দেখা যায়। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত অভিধানে এ শব্দ দুটি স্থান পেয়েছে কি না জানি না, তবে বহু দিন ধরেই বাঙালির দৈনন্দিন শব্দভান্ডারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে শব্দ দুটি। মানুষের কল্পনায়ও শব্দটির এমন একটি নেতিবাচক অবয়ব তৈরি হয়েছে যে, কোনো বাঙালি-ই তার সন্তানের নাম মীরজাফর রাখতে চায় না! যত দিন বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সজীব থাকবে, তত দিন পর্যন্ত এই নামটিও নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হবে। ভাষার ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবহার নিয়ে আমি লিখতে বসিনি, আমি লিখছি মীরজাফর চরিত্রটির প্রেতাত্মাদের নিয়ে!
মীরজাফরের বিশ্বাস ভঙ্গের কাহিনি জানেন না- এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। ১৭৫৭ সালের কথা। জুন মাসের ২৩ তারিখ পলাশীর প্রান্তরে মুখোমুখি হয়েছে ইংরেজ সেনাবাহিনী ও নবাব সিরাজ-উদণ্ডদৌলার সৈন্যবহর। এই সেই সিরাজ-উদণ্ডদৌলা, ইতিহাসে যার নাম ঠাঁই পেয়েছে বাংলা, বিহার, ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নগণ্য। অস্ত্র, গোলাবারুদও ছিল নেহায়েতই কম। এর বিপরীতে নবাবের বহরে ছিল হাজার হাজার সৈন্য। ছিল কামানের মতো ভয়াবহ আগ্নেয়াস্ত্র। সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রও ছিল ইংরেজ বাহিনীর তুলনায় অধিক। এই যুদ্ধে সিরাজ-উদণ্ডদৌলার জয় সুনিশ্চিত। নবাব খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না এ নিয়ে।
ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নবাবের সেনাবাহিনী জয়লাভ করবে- এটি-ই ছিল অনুমেয়। কিন্তু যুদ্ধের দিন দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। নবাবের সৈনিকরা হাত গুটিয়ে বসে আছে। আর ইংরেজদের পক্ষ থেকে মুহুর্মুহু হামলা চালানো হচ্ছে নবাবের শিবিরে। নবাব ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার প্রধান সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন। নবাব সিরাজ-উদণ্ডদৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর। এই সেই মীরজাফর, ২০০ বছর ধরে যার লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফল ভোগ করেছে বাঙালি জাতি। মীরজাফর এসে নবাবকে উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করল। কিছু সময় পরই যুদ্ধ শুরু করবে- এমন আশ্বাসও দিল। কিন্তু এই যুদ্ধ ছিল মূলত নাটকের একটি দৃশ্যের মঞ্চায়ন, যে নাটকটি সাজিয়েছে চতুর ইংরেজ বণিক দল ও তাদের এ দেশীয় দোসররা। আর এ নাটকের শেষভাগে পুরস্কৃত করা হয়েছে মীরজাফরকে। যুদ্ধের এই নাটক সাজানো হয়েছিল আরো কিছুদিন আগেই।
মীরজাফরের মনে ছিল নবার হওয়ার বাসনা। আর ইংরেজদের মনে ছিল সমগ্র বাংলাজুড়ে ব্যবসা ছড়িয়ে বাংলাকে দখল করার এক ভয়াল নীলনকশা। দুই পক্ষের এই মনোবাসনা এসে মিলিত হয়েছে পলাশীর প্রান্তরে। যুদ্ধের আগেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, মীরজাফর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করবে না। বিনাযুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ জয় করে হত্যা করবে সিরাজ-উদণ্ডদৌলাকে। নতুন নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসানো হবে মীরজাফরকে। আর এর বিনিময় হিসেবে অঢেল অর্থের ভাগ পাবে ইংরেজ বণিকরা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী-ই কাজ সম্পাদিত হয়। সিরাজ-উদণ্ডদৌলার মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসানো হয় মীরজাফরকে। ১৭৫৭ সালের ২৯ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় মীরজাফরের শাসনকার্য পরিচালনা।
গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। চতুরতা আর বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজ-উদণ্ডদৌলাকে পরাজিত করেছিল মীরজাফর, কিন্তু এবার ইংরেজদের চাতুর্যে নিজেই হয়েছে পরাজিত। সিংহাসনে বসার অল্প কিছুদিনের ভেতরেই পাওনা টাকা নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে মীরজাফর। ইংরেজরা ছাড় দেওয়ার পাত্র নয়। যে ইংরেজদের হাত ধরে সিংহাসনে বসেছিল মীরজাফর, সেই ইংরেজরাই তাকে হটিয়ে দেয় সিংহাসন থেকে। এর পরও বছর কয়েকের জন্য ক্ষমতা পেয়েছিল মীরজাফর, কিন্তু সেটিও খুব বেশি সুখকর হয়নি। বরং তার এই ক্ষমতা পাওয়ার লোভই উপমহাদেশে ব্রিটিশদের আধিপত্যের দরজা খুলে দিয়েছে। মীরজাফরের কারণেই ২০০ বছর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে এ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষকে।
১৭৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করে মীরজাফর। কিন্তু ইতিহাসের নিকৃষ্ট এক চরিত্র কিংবা প্রচলিত শব্দভান্ডারের নিকৃষ্টতম গালি হিসেবে মীরজাফর যেন এখনো বর্তমান। বর্তমান তার আদর্শিক দোসররা। মরে গেলেও বিশ্বাসঘাতকের বেশে মীরজাফরের প্রেতাত্মারা যেন এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের চারপাশজুড়ে। এই মীরজাফররা ছড়িয়ে আছে আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত। প্রতিনিয়ত তারা আমাদের নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। বন্ধুবেশে সহমর্মিতা লাভ করে ঘাতকবেশে ছুরি বসাচ্ছে আমাদেরই শরীরে। দেশকে, দেশের ভাবমূর্তিকে করছে কলুষিত। উদীয়মান অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশকে ঘিরে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র এখনো চলমান। আর এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এ দেশীয় কিছু মীরজাফর। দেশকে, দেশের স্বার্থকে রক্ষা করতে হলে সবার আগে এসব মীরজাফরকে খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের ব্যক্তিজীবনেও এর রেশ ছড়িয়ে রয়েছে। বারবার নাজেহাল করছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে।
আমাদের আশপাশের মানুষের মধ্যে যে মীরজাফরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিদ্যমান, তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে। এ সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল এ দেশেরই কতিপয় বিশ্বাসঘাতক। হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণসহ প্রতিটি অপরাধের সঙ্গেই তারা জড়িত ছিল; বাঙালি হত্যায় শুরু থেকেই সহযোগিতা করে আসছিল পাকিস্তানিদের। রাজাকার, আলবদর, আলশামস নামক এই যুদ্ধাপরাধীরা তো মীরজাফরেরই অন্য একটি রূপ। নিজের স্বার্থে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল দেশের সঙ্গে। দেশকে মেধাশূন্য করতে বুদ্ধিজীবীদের তুলে দিয়েছিল পাকিস্তানিদের হাতে। স্বাধীনতার পরও তারা ছিল সক্রিয়। স্বাধীন বাংলায় মীরজাফরদের আরেকটি ষড়যন্ত্রের উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে। এ দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। আর এ হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল এ দেশেরই কতিপয় বিশ্বাসঘাতক। এ যেন পুরোনো দৃশ্যেরই একাধিক পুনরাবৃত্তি। এই বিশ্বাসঘাতকরা কখনোই আমাদের পিছু ছাড়বে না। যুগে যুগে মীরজাফরের বেশে হামলে পড়বে আমাদের ওপর। এই মীরজাফরদের রুখে দিতে তাই হতে হবে বদ্ধপরিকর।ভালোবাসতে হবে সবুজ -শ্যামল সোনার বাংলা কে। একসাথে মোকাবিলা হবে সকল অপশক্তিকে; ভেঙে দিতে নব্য মীরজাফরদের সকল ইন্দ্রজাল।
লেখক : ৩১তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)।
পাঠকের মতামত:
- মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ১
- নিখোঁজের ৬ মাস পরেও খোঁজ মেলেনি স্কুল ছাত্র শাকিবের, এলাকাবাসীর মানববন্ধন
- মহম্মদপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অবহিতকরণ বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত
- দেশে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমাতে হবে
- উদ্বোধনের ৭ মাস পর শনিবার থেকে মোংলা রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু
- যশোরে তামাককে লাল কার্ড প্রদর্শন, পরিহারের শপথ তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর
- যশোর জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি মতিয়ার সম্পাদক জাহিদ
- রাজবাড়ীতে আরামঘর শিশু নিকেতনের চড়ুই ভাতি অনুষ্ঠিত
- 'সেবিকারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে মানুষের সেবা করে সুস্থ করে তোলেন'
- সুন্দরবনে প্রবেশে ৩ মাসের নিষেধাজ্ঞা
- বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসে মহম্মদপুরে র্যালি আলোচনা সভা
- ‘ভোটাধিকার প্রয়োগে কোনো অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না’
- দখল ও দূষণমুক্ত করা হবে প্রতিটি জলাশয় : এমপি আজাদ
- সাতক্ষীরায় আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে গাছ কেটে ও লাঙ্গল চাষ করে অন্যের জমি জবরদখলের চেষ্টা
- সভাপতি রফিক উদ্দিন, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম
- ‘বিএনপির হাতেই দেশের স্বাধীনতা নিরাপদ’
- মেলান্দহে ৮ লাখ টাকার গাঁজা উদ্ধার, ইউপি সদস্য গ্রেফতার
- মহম্মদপুরে সর্পদংশনে এক ব্যক্তির মৃত্যু সর্প দংশনে
- ফরিদপুরে সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে চোখের লেন্সসহ ছানি অপারেশন
- সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ তিন জেলে
- ‘যে কোন দুর্যোগে জনগণের পাশে থাকে শেখ হাসিনা’
- ফরিদপুরে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত
- ‘রাজনৈতিক কর্মকান্ড জনবিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে ব্যবস্থা’
- ২ উপজেলার ৫০ হাজার মানুষের যাতায়াতে দুর্ভোগ
- হাসপাতালে মারা গেলেন গুলিবিদ্ধ ইউপি চেয়ারম্যান আতুমং মারমা
- ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীকে কী গ্রেপ্তার করতে পারবে আইসিসি?
- ফুলপুরে লেয়ার মুরগি পালন করে বিপাকে দুই খামারি
- দুধের স্বাস্থ্য উপকারিতা ও অপকারিতা
- ‘বাংলাদেশ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার’
- দেশের বাজারে বিশ্বের নাম্বার ওয়ান স্মার্টফোন অনার ম্যাজিক ৬ প্রো
- মার্কিন ইতিহাসে প্রথম একজন প্রেসিডেন্ট ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন
- এমপি আনার হত্যা: এবার ৫ দিনের রিমান্ডে তিন আসামি
- গণমাধ্যম সাংবাদিকতা আমার কথা
- কলারোয়ায় আ.লী নেতা মজনুর নেতৃত্বে পুলিশের ওপর হামলা, আহত ৪
- কল্যাণপুর যুদ্ধ
- শ্যামনগরে বাঘের দুইটি নখসহ আটক ১
- কালিগঞ্জে বিদ্যুৎস্পর্শে প্রাণ গেল জেলের
- এমপি আনারকে কলকাতায় রিসিভের দায়িত্বে ছিলেন সিলিস্তি
- ইউরোপের পর্তুগালে টিভি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ওয়ালটনের
- টুঙ্গিপাড়ায় ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষের আধুনিক কলাকৌশল নিয়ে মাঠ দিবস
- নড়াইল জেলা যুবলীগের ৫ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা
- দিনাজপুরে কালবৈশাখী তান্ডবে আহত রুবেল মারা গেছেন
- আলফাডাঙ্গা পৌরসভার নতুন অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা
- গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ২৪ ফিলিস্তিনি নিহত
- লাইফ সাপোর্টে সীমানা
- ‘২০৪০ সালে তামাকমুক্ত দেশ গড়তে কাজ করছি’
- সৌদিতে পৌঁছেছেন ৫১ হাজার ৪০৩ জন হজযাত্রী
- ‘বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের বুলি ভুতের মুখে রাম রাম’
- ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ছাত্রলীগ
- আরও একটি বিশ্বকাপ খেলার প্রত্যাশা সাকিবের
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- এবারও মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ফাঁদে শিক্ষার্থীরা
- এবারও মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ফাঁদে শিক্ষার্থীরা
- সিলেটের ভ্রমণ কাহিনী
- শুধু প্রভাবশালীদের পক্ষেই আইন!
- অম্ল-মধুর যন্ত্রণায় অপু বিশ্বাস
- লাইন ধরে খেতে হয় লিখনের জগা খিচুড়ি !
- আমার বোন শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি : চিনে নিন কে এই বরকত!
- 'ইতিহাসের ইতিহাস'
- ধনী হওয়ার আট কার্যকর উপায়
- লক্ষাধিক রাখাইন জনগোষ্ঠী আড়াই হাজারে নেমে এসেছে
- মেয়ে পটানোর কৌশল!
- উত্তরাধিকার ৭১ নিউজের নতুন যাত্রা ১ বৈশাখ
- আমায় ক্ষমা কর পিতা : পর্ব ১৪'তোমার সহজাত উদারতা তোমাকে আকাশের সীমানায় উন্নীত করলেও তোমার ঘনিষ্ঠ অনেকের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ তোমার নৃশংস মৃত্যুর পথে কোনই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি'
- লোভী মানুষ চেনার সহজ উপায়
- বাংলা বই পড়ার ওয়েবসাইট
- শাকিবের নায়িকা শ্রাবন্তী, অপুর নায়ক জিৎ
- হুমায়ূনের মৃত্যুর কারণ মদের পার্টি !
- মঠবাড়িয়ায় ৯ বছরের শিশুকে পাশবিক নির্যাতনের পর হত্যা
- দেশে ফিরছেন তারেকস্ত্রী জোবায়দা রহমান
- বোরকা পরা মেয়ের গণধর্ষণের ভিডিও নিয়ে সিলেটে তোলপাড়
- ইউটিউবে নায়লার আত্মপ্রকাশ
- নেপালের ভূমিকম্প প্রাকৃতিক নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি !
- বিএনপির আন্দোলন হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে !
-1.gif)


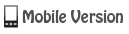









.jpg&w=60&h=50)


































.jpg&w=60&h=50)











