বাংলাদেশে সমান পারিশ্রমিকের বাস্তবতা ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

ওয়াজেদুর রহমান কনক
সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক কেবল ন্যায়বিচারের নীতি নয়, এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম মৌলিক শর্ত। আন্তর্জাতিকভাবে দেখা যায়, এখনও নারীরা পুরুষদের তুলনায় গড়ে প্রায় ১৬–২০ শতাংশ কম আয় করেন, যা বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজারের একটি স্থায়ী বৈষম্য হিসেবে রয়ে গেছে। বাংলাদেশেও একই ধারা বিদ্যমান—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপ অনুযায়ী নারীরা গড়ে পুরুষদের তুলনায় ১০–২০ শতাংশ কম আয় করেন। শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৪৩–৪৪ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের অংশগ্রহণ ৭৮–৮০ শতাংশ এবং বৈশ্বিক গড় প্রায় ৫০–৫১ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রায় ৫৯.৮ শতাংশ নারী অনানুষ্ঠানিক বা ঝুঁকিপূর্ণ খাতে নিযুক্ত, যেখানে বেতন কাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা দুর্বল, ফলে সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০২৪ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৯৯তম, যা ইঙ্গিত করে যে সমান পারিশ্রমিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেশ এখনও পিছিয়ে। এই বাস্তবতা ইন্টারন্যাশনাল ইক্যুয়াল পে ডে-র মূল বার্তা—লিঙ্গভিত্তিক আয় বৈষম্য দূরীকরণ ও শ্রমবাজারে সমতা নিশ্চিত করা—বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।
বাংলাদেশে সমান পারিশ্রমিকের অবস্থা গ্লোবাল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৈষম্য এখানে এখনও একটি গভীর সমস্যা। আন্তর্জাতিকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় গড়ে ১৬–২০ শতাংশ কম আয় করেন, এবং বাংলাদেশেও এই প্রবণতা প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দেশে নারীরা গড়ে পুরুষদের তুলনায় ১০–২০ শতাংশ কম আয় করেন। শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের দিক থেকেও বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএলও’র সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, কাজযোগ্য বয়সের নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ প্রায় ৪৩–৪৪ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৭৮–৮০ শতাংশ এবং বৈশ্বিক গড় প্রায় ৫০–৫১ শতাংশ। এর মানে হলো, বাংলাদেশের নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের তুলনায় অনেক কম সক্রিয় এবং কাজ পাওয়ার পরেও কম আয় করছেন।
বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে প্রায় ৫৯.৮ শতাংশই ঝুঁকিপূর্ণ বা অনির্দিষ্ট ধরনের কাজে নিযুক্ত, যেগুলো মূলত অনানুষ্ঠানিক খাত, কৃষি বা অস্থায়ী স্ব-নিযুক্ত কাজে কেন্দ্রীভূত। এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে স্থায়ী বেতন বা সামাজিক সুরক্ষার অভাব থাকে, যা সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার পথে একটি বড় বাধা। গার্মেন্টস, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতগুলোতে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এসব ক্ষেত্র ন্যায্য বেতন কাঠামো ও সুরক্ষা ব্যবস্থার বাইরে থাকায় একই মূল্যমানের কাজ করেও তারা কম আয় করেন। পেশাভিত্তিক বিভাজন বা occupational segregation এই বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দেয়। নারীরা সাধারণত কম মজুরি ভিত্তিক কাজে বেশি জড়িত, আর উচ্চ বেতনের কাজ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত।
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০২৪ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৯৯তম স্থানে ছিল। এই অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও সমান পারিশ্রমিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেশ এখনও পিছিয়ে। সংবিধান ও শ্রম আইন সমতার নীতি সমর্থন করলেও, বাস্তবে আইন প্রয়োগ দুর্বল, বেতন কাঠামো ও পারিশ্রমিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা কম এবং সামাজিক সুরক্ষার সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বলছে, বাংলাদেশের জন্য এখন জরুরি হলো বেতন স্বচ্ছতা নীতি বাস্তবায়ন করা, মাতৃত্ব ও পরিবার যত্ন সম্পর্কিত সুবিধা সম্প্রসারণ, এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে থাকা বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিককে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা।
এই সমস্ত পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে যে সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের অবস্থান বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় দুর্বল এবং কার্যকর নীতি সংস্কার ও বাস্তবায়ন ছাড়া এই বৈষম্য কমানো সম্ভব নয়।
বাংলাদেশে মহিলাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ এখনও বিশ্ব গড়ের চেয়ে কম ও শ্রমের গুণগত দিক দিয়ে অনেকখানি অনিশ্চিত; ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী মহিলা কর্মবাহিনীর মধ্যে প্রায় ৫৯.৮% অনির্দিষ্ট বা ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) কাজের মধ্যে থাকেন — অর্থাৎ এরা অসংগঠিত/আণবিক/অস্থায়ী কর্মার্জন বা কৃষি/স্ব-নিযুক্ত ধরনের কাজে জড়িত, যা স্থায়ী মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষায় দুর্বল। এই অনির্দিষ্ট কর্মসংস্থানের অংশগ্রহণ মহিলাদের আয়ের স্থিতিশীলতা কমায় এবং সমান পারিশ্রমিক অর্জনের পথে বড় বাধা সৃষ্টির কারণ হিসেবে কাজ করে।
শ্রমবাজারে সক্রিয়তার হারেও বাংলাদেশে নির্দিষ্ট উন্নতি দেখা গেলেও এখনও বিশাল লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান আছে; সাম্প্রতিক (ILO/World Bank মডেল-অনুমানভিত্তিক) হিসাব দেখায় ২০২৩-২৪ সময়কালে বাংলাদেশের কাজযোগ্য বয়সী মহিলাদের শ্রমবাহিনীতে অংশগ্রহণ শতকরা ৪৩–৪৪%-এর কাছাকাছি — যা অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও বিশ্ব গড় (প্রায় ৫০%/৫১% পর্যায়ে) থেকে নীচে এবং দেশের পুরুষদের অংশগ্রহণ (প্রায় ৭৮–৮০% পর্যায়ে) থেকে অনেক পিছিয়ে। কাজের সুযোগ ও শ্রমের ধরনে এই পার্থক্যই আয় বৈষম্য বাড়াতে সহায়ক।
পারিশ্রমিক-শহরের নিরপেক্ষ “গ্যাপ” নিয়ে জাতীয় গবেষণা ও শ্রম জরিপগুলোতে বিভিন্ন মান পাওয়া গেছে; পুরাতন বাংলাদেশ লেবার ফোর্স সার্ভে বিশ্লেষণগুলি দেখায় কখনো কখনো গড়ে ১০–২০% স্তরের লিঙ্গ আয় পার্থক্য রেকর্ড করা হয়েছে, এবং আধুনিক বিশ্লেষণে (সমন্বয়/শর্তগুলো বিবেচনায় নেওয়া হলে) মোট পার্থক্যের কিছু অংশ ব্যাখ্যা করা গেলেও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অবশিষ্ট অঙ্ক অগ্রহণযোগ্য রয়ে যায় — অর্থাৎ বাস্তব জায়গায় নারী গড়ে পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম উপার্জন করেন। বিভিন্ন গবেষণা ও লং-রান ডিকম্পোজিশন বিশ্লেষণ ২০১০-এর দশকেও ঘণ্টা/দিবস ভিত্তিক আয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ১২-২০% গ্যাপ দেখিয়েছে।
পেশা-বিভাজন (occupational segregation) অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের উচ্চ অংশ, এবং মাতৃত্ব-সংক্রান্ত “penalty” মিলিতভাবে বাংলাদেশে নারীদের আয় ও ক্যারিয়ার প্রবাহকে সীমিত করে। বিশেষত গার্মেন্টস, কৃষি ও স্ব-নিযুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসা-খাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীরা থাকলেও সেগুলোর অধিকাংশই ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা ও বেতন কাঠামো থেকে বঞ্চিত, ফলে একই কাজের অনুরূপ মূল্য থাকা সত্ত্বেও আয়ের বৈষম্য গভীর হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই ধরনের কাজের অসংগঠিত প্রকৃতি ও নীতি-শূন্যতাকেই সমাধানের বড় বিষয়ে চিহ্নিত করে।
গ্লোবালের তুলনায় অবস্থান বোঝাতে যদি বিশ্বস্ত সূচক দেখা হয়, তাহলে World Economic Forum-এর Global Gender Gap-এ ২০২৪ সালে বাংলাদেশকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৯৯-তম অবস্থানে (সদ্যপ্রকাশিত ২০২৪ সংস্করণে) অবস্থান ধরা হয়েছিল — যদিও পরবর্তী বছরগুলোর সূচকে পরিবর্তন হতে পারে। WEF-এর সূচকে বাংলাদেশের স্কোর-ও গত সংস্করণগুলোর তুলনায় ওঠানামা দেখিয়েছে; এটি ইঙ্গিত দেয় যে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, সুযোগ ও নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতি ঐতিহাসিকভাবে অনিশ্চিত ও পরিমাপনীয়।
আইনি ও নীতিগত স্তরে বাংলাদেশের সংবিধান ও বিভিন্ন শ্রম আইন নারী-পুরুষ সমতার কথা বলে; তবু কার্যকর বাস্তবায়ন, বেতন-স্বচ্ছতা নীতি, সংস্থাগত নজরদারি ও সামাজিক সুরক্ষা-পক্ষপাতমূলক কর্মসূচি প্রয়োগে ঘাটতি থাকার ফলে ম্যাল-অ্যালোকেশন ও আয়ের বৈষম্য রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দৃঢ়ভাবে বলছে—দেশের অভ্যন্তরে পারিশ্রমিক-স্বচ্ছতা, শিল্প ভিত্তিক সমীক্ষা, মাতৃত্ব ও যত্ন সংক্রান্ত নীতির বিস্তার, অসংগঠিত খাতের সরকারি রেজিস্ট্রি ও সামাজিক নিরাপত্তা বাড়ানো হলে বৈষম্য দ্রুত কমানো সম্ভব।
সংক্ষেপে—গ্লোবালি নারীরা গড়ে পুরুষদের তুলনায় প্রায় ১৬–২০% কম আয় করেন বলার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বাস্তবতা সামগ্রিকভাবে অনুরূপ বা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কিছুটাই ভিন্ন; এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো হলো (১) অতি-উচ্চ অনির্দিষ্ট/অসংগঠিত কর্মসংস্থানের হার (মহিলাদের মধ্যে ≈৬০% ঝুঁকিপূর্ণ), (২) তুলনামূলকভাবে নিম্ন শ্রমবাজার অংশগ্রহণ (≈৪৩–৪৪%), এবং (৩) পেশা-ভিত্তিক বিভাজন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা যা আয়ের বৈষম্যকে স্থায়ী করে। এসব কারণে বাংলাদেশে গ্লোবাল গড়ের সঙ্গে তুলনা করলে নীতিগত হস্তক্ষেপ, বেতন-স্বচ্ছতা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানকে বিচার করে লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়াই সবচেয়ে কার্যকর পথ।
বাংলাদেশে সমান পারিশ্রমিকের অবস্থা গ্লোবাল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৈষম্য এখানে এখনও একটি গভীর সমস্যা। আন্তর্জাতিকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় গড়ে ১৬–২০ শতাংশ কম আয় করেন, এবং বাংলাদেশেও এই প্রবণতা প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দেশে নারীরা গড়ে পুরুষদের তুলনায় ১০–২০ শতাংশ কম আয় করেন। শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের দিক থেকেও বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএলও’র সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, কাজযোগ্য বয়সের নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ প্রায় ৪৩–৪৪ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৭৮–৮০ শতাংশ এবং বৈশ্বিক গড় প্রায় ৫০–৫১ শতাংশ। এর মানে হলো, বাংলাদেশের নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের তুলনায় অনেক কম সক্রিয় এবং কাজ পাওয়ার পরেও কম আয় করছেন।
বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে প্রায় ৫৯.৮ শতাংশই ঝুঁকিপূর্ণ বা অনির্দিষ্ট ধরনের কাজে নিযুক্ত, যেগুলো মূলত অনানুষ্ঠানিক খাত, কৃষি বা অস্থায়ী স্ব-নিযুক্ত কাজে কেন্দ্রীভূত। এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে স্থায়ী বেতন বা সামাজিক সুরক্ষার অভাব থাকে, যা সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার পথে একটি বড় বাধা। গার্মেন্টস, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতগুলোতে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এসব ক্ষেত্র ন্যায্য বেতন কাঠামো ও সুরক্ষা ব্যবস্থার বাইরে থাকায় একই মূল্যমানের কাজ করেও তারা কম আয় করেন। পেশাভিত্তিক বিভাজন বা occupational segregation এই বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দেয়। নারীরা সাধারণত কম মজুরি ভিত্তিক কাজে বেশি জড়িত, আর উচ্চ বেতনের কাজ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত।
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০২৪ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৯৯তম স্থানে ছিল। এই অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও সমান পারিশ্রমিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেশ এখনও পিছিয়ে। সংবিধান ও শ্রম আইন সমতার নীতি সমর্থন করলেও, বাস্তবে আইন প্রয়োগ দুর্বল, বেতন কাঠামো ও পারিশ্রমিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা কম এবং সামাজিক সুরক্ষার সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বলছে, বাংলাদেশের জন্য এখন জরুরি হলো বেতন স্বচ্ছতা নীতি বাস্তবায়ন করা, মাতৃত্ব ও পরিবার যত্ন সম্পর্কিত সুবিধা সম্প্রসারণ, এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে থাকা বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিককে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা।
এই সমস্ত পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে যে সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের অবস্থান বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় দুর্বল এবং কার্যকর নীতি সংস্কার ও বাস্তবায়ন ছাড়া এই বৈষম্য কমানো সম্ভব নয়।
বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা ও আঞ্চলিক গবেষণা থেকে স্পষ্ট যে লিঙ্গভিত্তিক আয় বৈষম্য কেবল সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়, বরং একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জও বটে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নতুন বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে যে যদি লিঙ্গ সমতা ও সমান পারিশ্রমিক সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা যায়, তবে বৈশ্বিক জিডিপি প্রায় ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে—যা দক্ষিণ এশিয়ার মতো উন্নয়নশীল অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা এখনও ক্ষুদ্র ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং প্রযুক্তি বা উচ্চ আয়ের খাতে তাদের উপস্থিতি ন্যূনতম, ফলে আয় বৈষম্য আরও গভীর হচ্ছে। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ডিজিটাল ও ই-কমার্স সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে বটে, তবে আয়ের কাঠামোতে বৈষম্য রয়ে গেছে এবং নেতৃত্বস্থানীয় পদের মাত্র ১০ শতাংশ নারী দখল করে আছেন। একই সঙ্গে, দেশের মোট বেতনভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নারী কোনো ধরনের সামাজিক সুরক্ষা বা মাতৃত্ব সুবিধার আওতায় আছেন, যা সমান পারিশ্রমিকের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।
এই বাস্তবতাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক অর্জন শুধু নীতিগত ঘোষণা দিয়ে সম্ভব নয়; প্রয়োজন শক্তিশালী প্রয়োগ, বেতন স্বচ্ছতা, শ্রমবাজার সংস্কার, মাতৃত্ব ও শিশুযত্ন নীতির উন্নয়ন এবং অনানুষ্ঠানিক খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার আওতায় আনার মতো কাঠামোগত পদক্ষেপ। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা, যেখানে নারীর শ্রমশক্তি অংশগ্রহণ এবং আয় এখনও পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে, তা দেখায় যে আন্তর্জাতিক সমান পারিশ্রমিক দিবস কেবল একটি প্রতীকী দিবস নয় বরং দেশের জন্য এক ধরনের উন্নয়ন-চ্যালেঞ্জের আয়না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের জন্য লিঙ্গভিত্তিক আয় বৈষম্য দূরীকরণ এখন আর বিলম্বযোগ্য নয়।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারন্যাশনাল ইকুয়াল পে ডে পালনের ধরন বৈচিত্র্যময় হলেও এর মূল উদ্দেশ্য সর্বত্র একই—নারী ও পুরুষের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা। জর্ডানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও জাতীয় পে-ইকুইটি কমিটি একত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বৃহৎ সচেতনতা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে, যেখানে ভিডিও, পোস্ট ও অনলাইন আলোচনা মানুষের মধ্যে সমান পারিশ্রমিকের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে এ দিনটি ঘিরে নীতি-সংলাপ, বিতর্ক সভা, সংবাদ সম্মেলন এবং সেমিনার আয়োজন করা হয়, যেখানে সর্বশেষ পরিসংখ্যান ও আইনগত অগ্রগতির আলোকে বেতন বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নীতি শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়। চেক প্রজাতন্ত্রে প্রতি বছর দু’দিনব্যাপী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যাতে বিশেষজ্ঞ বক্তা, নেটওয়ার্কিং সেশন ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের বেতন বৈষম্য হ্রাসের উপায় আলোচনা করা হয়।
সুইডেনে “১৬:০২ মুভমেন্ট” নামের একটি আন্দোলন প্রতীকী সময় ব্যবহার করে দেখায়, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে নারীরা কার্যত বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছেন—পুরুষদের তুলনায় যে সময় পর্যন্ত তারা সমান বেতন পেতে পারতেন তা চিহ্নিত করতে এই কৌশল ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন ও শ্রম অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ওয়েবিনার, অনলাইন আলোচনা ও কর্মশালার আয়োজন করে যাতে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি ও নীতি উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়। এসব উদযাপনের মধ্যে মূলত বার্তা থাকে যে সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক শুধু ন্যায্যতার প্রশ্ন নয়, এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।
পাঠকের মতামত:
- জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই অধ্যাদেশ অনুমোদন
- অর্থনীতি ও সমাজের প্রেক্ষাপটে উদ্যোক্তার ধারণার ঐতিহাসিক বিবর্তন
- কোটালীপাড়া পৌরসভার সাবেক মেয়রের ছেলে ছাত্রলীগ কর্মী তৌকির গ্রেফতার
- মাদারীপুরে ৬টি অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারকে ৬টি গাভী বিতরণ
- বাগেরহাটে পুকুরে ডুবে দাদা নাতির মৃত্যু
- কাপ্তাই বিএসপিআই’র শিক্ষার্থীদের ৩ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ
- বাগেরহাটে তৃতীয় দিনেও ১০টি নির্বাচন অফিসে অবস্থান ধর্মঘট
- ‘আমার ভোট আমি নিজেই দেব’
- ছাত্রছাত্রীদের এআই শেখাতে এগিয়ে আসলো রবি ও টেন মিনিট স্কুল
- মাদারীপুরে দেড়মাস পর কবর থেকে ঠিকাদারের লাশ উত্তোলন
- সোনারগাঁয়ে ডাকাত সর্দার ও মাদক ব্যবসায়ী মনির মেম্বারের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর মানববন্ধন
- কাপাসিয়ায় ৭১টি দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি চলছে
- ঈশ্বরদীতে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা
- প্রাণসায়ের খাল বাঁচাতে সাতক্ষীরায় মানববন্ধন সমাবেশ
- বরিশাল শহর রক্ষা বাঁধের ব্লক লুট, ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে আটক ১
- গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা
- বাংলাদেশে সমান পারিশ্রমিকের বাস্তবতা ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট
- লিবিয়ার জেলে আটক গৌরনদী-আগৈলঝাড়ার ৩৮ যুবক
- বাসদ’র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কামরুন নাহার বেবী মারা গেছেন
- তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে এক ব্যক্তি নিখোঁজ
- টাইমস স্কয়ারে দুর্গাপূজা
- গানের শিক্ষক নিয়োগে বাধা হচ্ছে উগ্রবাদীরা
- ‘উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে’
- কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সরকারি সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের
- ‘রাকসু-চাকসু নির্বাচনও ভালোভাবে হবে’
- দুঃসাহসী এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ও কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধের কথা
- রাজবাড়ীতে ৯ মাস নয় ৩ মাসেই পচছে পেঁয়াজ
- চীন সফরে বাংলাদেশ সিডস ফর দ্য ফিউচার বিজয়ীরা
- কুমিল্লার নতুন মেয়র নৌকার রিফাত
- ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৬ জনের মৃত্যু
- সালথায় সাদা শাপলার সৌন্দর্যে মন কেড়েছে সবার
- ‘ক্ষমতা ছেড়ে দিন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবো’
- একাত্তরের কথা
- আটলান্টায় ফোবানা সম্মেলন পরিণত হলো পারিবারিক অনুষ্ঠানে
- রাহুল রাজের প্রেমের কবিতা
- মে দিবসের কবিতা
- মজাদার তালের বড়া বানাবেন যেভাবে
- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস : লক্ষণ ও প্রতিরোধে করণীয়
- বানভাসিদের পাশে দাঁড়ালেন শাহরুখ খান
- গোলমরিচ ও তেজপাতার গল্প
- বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন শুরু আজ
- ‘দলের নির্দেশ অমান্য করে প্রভাব বিস্তার করার ঘটনা ইসির বোধগম্য নয়’
- আগুনে পুড়ে গেলে তাৎক্ষণিক যা করবেন
- অবশেষে দেশে ফিরছে বাংলাদেশ ফুটবল দল
- রাজধানীতে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬
-1.gif)
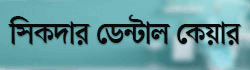

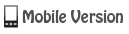








.jpg&w=60&h=50)

.jpg&w=60&h=50)


























-12.07.25.jpg&w=60&h=50)


.jpg&w=60&h=50)






















