উৎপাদন খরচ ছাড়া ইলিশের এত দাম কেন?

মীর আব্দুল আলীম
বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ বাঙালির রান্না ও স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্ষার পদ্মা-মেঘনা কিংবা বঙ্গোপসাগরের ইলিশের ঘ্রাণ মনে করিয়ে দেয় শৈশবের রান্নাঘরের সুখ-স্মৃতি। কিন্তু আজ সেই আনন্দ এক ধরনের ব্যথা হয়ে গেছে—কারণ সাধারণ ভোক্তার নাগালের বাইরে চলে গেছে ইলিশ। রুই, কাতলা বা পাঙ্গাসের মতো চাষ করা মাছের জন্য কোটি কোটি খরচ হয়—পুকুর, পোনা, খাবার, ওষুধ—কিন্তু ইলিশের ক্ষেত্রে প্রকৃতি স্বয়ংই উৎপাদন করে, জেলের খরচও সীমিত। তবু বাজারে এই জাতীয় মাছের দাম আকাশছোঁয়া। কারণ স্পষ্ট—সিন্ডিকেট কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ইলিশকে ‘সোনার হরিণ’ বানিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির অবদান তুচ্ছ করা হয়, সাধারণ মানুষ কেবল ছায়া দেখছে; আর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বা ন্যায্য বাজার ব্যবস্থা এখনো অনুপস্থিত। এই পরিস্থিতি শুধুই ভোক্তার ক্ষতির কারণ নয়, বরং দেশের জাতীয় মাছের মর্যাদা ও জনগণের আস্থা উভয়কেই হুমকির মুখে ফেলেছে।
ইলিশ বনাম চাষের মাছের খরচের অঙ্ক: চাষের মাছ উৎপাদনে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। পুকুর খনন, পোনা সংগ্রহ, প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ, পানি পরিষ্কার, অক্সিজেনের মান বজায় রাখা, রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা—সব কিছুতেই নির্দিষ্ট খরচ রয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মাছ মারা গেলে লোকসানের ঝুঁকিও থেকে যায়। অথচ ইলিশ মাছ প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়। কোনো পুকুর নেই, পোনা নেই, খাবার নেই। জেলেদের নৌকা, জাল আর শ্রমই মূল পুঁজি। তবু ইলিশের দাম কাতলার চেয়েও বেশি। এতে স্পষ্ট হয়—দাম বাড়ানো হচ্ছে কৃত্রিমভাবে। খরচের অঙ্ক দিয়ে বাজারের হিসাব মেলে না।
উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু বাজারে সঙ্কট! বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, ২০০৮ সালে দেশে ইলিশ উৎপাদন ছিল প্রায় ২.৯ লাখ টন। এর পরবর্তী এক যুগে ধারাবাহিকভাবে এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় প্রায় ৩.৮ লাখ টন, আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উৎপাদন ছুঁয়ে ফেলে ৫ লাখ টনের ঘর। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি হিসাব বলছে, উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ লাখ টনে, যা দেশের সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনের মোট অংশের প্রায় ১২ শতাংশ। অর্থাৎ পনেরো বছরে উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
অর্থনীতির মৌলিক তত্ত্ব বলছে-যদি কোনো পণ্যের উৎপাদন বাড়ে এবং যোগান বাজারে বেশি থাকে, তবে দাম কমার কথা। কিন্তু ইলিশের ক্ষেত্রে ঘটছে তার সম্পূর্ণ উল্টো। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারে দামের গ্রাফও বেড়েছে প্রায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ সালে এক কেজি মাঝারি ইলিশ পাওয়া যেত ২৫০ থেকে ৩০০ টাকায়। ২০১৫ সালে একই মাপের ইলিশের দাম দাঁড়ায় ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। আর ২০২৪ সালে ঢাকার বাজারে মাঝারি আকারের এক কেজি ইলিশের দাম প্রায় ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত গিয়েছে। অর্থাৎ উৎপাদন দ্বিগুণ হলেও দাম বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদনের বাড়তি সুবিধা কৃষক বা জেলে পাচ্ছে না, ভোক্তাও পাচ্ছে না। বরং এ মুনাফার সিংহভাগ চলে যাচ্ছে কিছু মজুতদার, পাইকার ও সিন্ডিকেটভুক্ত ব্যবসায়ীর পকেটে। এভাবে ইলিশের প্রকৃত আর্থিক সাফল্য কাগজে-কলমে বৃদ্ধি পেলেও বাস্তবে তা জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।
সিন্ডিকেটের খপ্পরে ইলিশ! প্রকৃত সমস্যার মূল শিকড় এখানেই লুকিয়ে আছে। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় মাছ ইলিশকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী সিন্ডিকেট। কয়েকটি বড় মজুতদার ও প্রভাবশালী পাইকারি ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরেই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে নিজেদের মতো করে। তারা জেলেদের কাছ থেকে জোরপূর্বক বা প্রভাব খাটিয়ে অনেক কম দামে ইলিশ কিনে নেয়। মাছের মৌসুমে যখন জেলেরা ন্যায্য দামে মাছ বিক্রি করতে চায়, তখনও সিন্ডিকেট তাদের বাধ্য করে অস্বাভাবিক কম দামে বিক্রি করতে। এই মাছ পরে তারা বিশাল গুদামে মজুত রাখে। পরবর্তীতে যখন বাজারে সরবরাহ কিছুটা কমে যায় বা চাহিদা বেড়ে যায়—যেমন পূজা, ঈদ, বা জাতীয় উৎসবের সময়—তখন এই সিন্ডিকেট ইচ্ছাকৃতভাবে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। ফলে খুচরা বাজারে ইলিশের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যায়। বাংলাদেশ প্রতিদিন বা সমকালের মতো সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত রিপোর্ট হয় যে, বরিশাল, চাঁদপুর, ভোলা, পটুয়াখালী বা মেঘনা-পদ্মা অঞ্চলের মৎস্যঘাটে জেলেরা তাদের ধরা মাছ খুবই কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন। এক কেজি ইলিশ যেখানে ঘাটে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, একই মাছ ঢাকায় পৌঁছানোর পর দাম দাঁড়াচ্ছে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। অর্থাৎ উৎপাদকের হাতে ন্যায্য দাম পৌঁছাচ্ছে না, আর ভোক্তাকে দিতে হচ্ছে তিনগুণ মূল্য। পুরো মুনাফা চলে যাচ্ছে সিন্ডিকেটের হাতে।
ভোক্তা পর্যায়ের সমস্যা রয়েছে: ভোক্তা পর্যায়ের সমস্যা ইলিশের বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। সাধারণত অন্য মাছ কেউ একসাথে তিন-চার কেজির বেশি কেনেন না। কিন্তু ইলিশের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। একজন ভোক্তা যদি সামর্থ্যবান হন, তিনি একবারে দশটি কিংবা তারও বেশি ইলিশ কিনে ফেলেন। এটি কেবল ব্যক্তিগত রুচির বিষয় নয়, বরং সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবেও কাজ করে। ইলিশ খাওয়ানো এখন অনেক পরিবারের কাছে এক ধরনের ঐতিহ্য ও প্রতচৎবংঃরমব হিসেবে ধরা হয়। ফলে অনেক ভোক্তা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি কিনে ফ্রিজে জমিয়ে রাখেন। এই অযৌক্তিক কেনাকাটা বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। কারণ, উৎপাদন বাড়লেও বাজারে ইলিশের প্রাপ্যতা কমে যায় এবং সাধারণ ক্রেতারা উচ্চমূল্যে কিনতে বাধ্য হন কিংবা একেবারেই কিনতে পারেন না।
অন্য মাছের ক্ষেত্রে যেখানে চাহিদা ও সরবরাহ তুলনামূলক ভারসাম্যপূর্ণ থাকে, সেখানে ইলিশের ক্ষেত্রে এই ভোক্তা আচরণ বড় সমস্যা তৈরি করছে। সরকার ও বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে তাই শুধু সিন্ডিকেট নয়, ভোক্তার এই অযৌক্তিক আচরণ নিয়েও ভাবতে হবে। না হলে “জাতীয় মাছ” কেবল ধনী ও সামর্থ্যবানদের জন্যই উৎসবের খাদ্য হয়ে উঠবে, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যাবে।
জেলের অবস্থা: পরিশ্রমে ঘাম, আয়ে চোখের জল! মেঘনা বা পদ্মার বুক চিরে জেলে সারারাত জাল ফেলে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, অন্ধকার, নদীর গর্জন—সবকিছুকে উপেক্ষা করে তাদের শ্রম চলে। অথচ সকালে তারা মাছ বিক্রি করতে গেলে স্থানীয় আড়তদারদের কাছে বাধ্য হয়ে কম দামে ইলিশ বেচতে হয়। কারণ পাইকাররা সিন্ডিকেটের বাইরে গেলে বাজারে তাদের জায়গা থাকবে না।
এভাবে প্রকৃত উৎপাদক নিজের শ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় না। অথচ সেই মাছই ভোক্তার কাছে পৌঁছায় তিন-চার গুণ দামে। প্রশ্ন উঠতেই পারে—সরকারি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কিংবা জেলা প্রশাসন কোথায়? অভিযান হয়, কিন্তু তা নিছক নাটক। কদিন পর সব আগের মতো চলে। সরকার দেখেও না দেখার ভান করে। কেন? কারণ সিন্ডিকেটের শেকড় রাজনৈতিক শক্তির ভেতর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে প্রশাসন অক্ষম নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে অচল। ভোক্তার দুর্দশা: ইলিশ বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। একসময় বাঙালির ঘরে বর্ষায় অন্তত একদিন ভাতের সঙ্গে ইলিশ ভাজা ছিল রীতির মতো। এখন সেই দৃশ্য বিরল। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য এক কেজি ইলিশ কেনা মানে মাসিক বাজেটে বড় ধাক্কা। নিম্নবিত্ত পরিবারের কথা বলাই বাহুল্য। বাজারে গেলে তাদের মুখে একটি কথাই শোনা যায়—“ইলিশ এখন শুধু ধনীদের মাছ।” এটি কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়, সাংস্কৃতিক বৈষম্যও।
শুভঙ্করের ফাঁকি: সরকারি প্রচারণা বনাম বাস্তবতা- সরকার প্রায়ই ঘোষণা দেয়—“এবার ইলিশ উৎপাদনে রেকর্ড।” পত্রিকায় ছবির জন্য সাজানো খুশি মুখ, কর্মকর্তাদের হাসিমুখে বর্ণনা, মিডিয়ায় আনন্দঘন প্রতিবেদনের ছাপ। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন বাজারে যায়, তখন তার চোখে পড়ে বাস্তবের অন্য ছবি—১ কেজি ইলিশের দাম ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা, যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য প্রায় অচল্য। উৎপাদন বেড়েছে, সরকার বলছে, কিন্তু ভোক্তার ঝুড়ি বলছে অন্য কথা। এই ব্যবধানই তৈরি করছে “শুভঙ্করের ফাঁকি।” কাগজে-কলমে উৎপাদন যেমন রেকর্ড করছে, বাস্তবে সেই সাফল্য পৌঁছাচ্ছে না সাধারণ মানুষের কাছে। এর মূল কারণ হল বাজারে সিন্ডিকেট ও অসাধু ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণ। তারা উৎপাদনকে কৃত্রিম সংকটে পরিণত করছে, দাম বাড়াচ্ছে এবং দেশের জাতীয় মাছকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, সরকারি প্রচারণা ও বাস্তব জীবনের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। একদিকে উৎপাদনের পরিসংখ্যান, অন্যদিকে ভোক্তার টানাপোড়েন—এই মিলের অভাবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দেশের জাতীয় মাছ ইলিশের “জাতীয় মর্যাদা” নিয়ে সত্যিকারের প্রশ্ন।
রপ্তানি নীতি ও ভোক্তার ক্ষতি: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের ইলিশ উৎপাদন ছিল প্রায় ৫.৭১ লাখ টন। এত বিপুল উৎপাদনের পরও সাধারণ ভোক্তার জন্য মাছটি দিন দিন নাগালের বাইরে যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ রপ্তানি নীতি। সরকার প্রতিবছর বিদেশি মুদ্রা আয়ের যুক্তিতে রপ্তানি অনুমোদন দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারতকে রপ্তানি হয়েছিল ১,৩৯১ টন ইলিশ, আয় হয়েছিল ১.৩৮ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ এ রপ্তানি কমে দাঁড়ায় মাত্র ৮০২ টন, আয় হয় প্রায় ৮০ লাখ ডলার। চলতি অর্থবছরের শুরুতে এ আয় আরও কমে ৫.৩৭ মিলিয়ন ডলার এ নেমেছে। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অজুহাতে রপ্তানি হলেও, এর সুবিধা সীমিত গোষ্ঠীর হাতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। অন্যদিকে ঢাকার বাজারে এক কেজি ইলিশের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,৪০০–১,৬০০ টাকা, অথচ ঘাটে জেলেরা বিক্রি করছে ৪০০–৫০০ টাকায়। ফলে জেলে বঞ্চিত, ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত—আর লাভবান হচ্ছে রপ্তানিকারক ও সিন্ডিকেট। জাতীয় মাছ ইলিশ তাই কূটনৈতিক কারবারের অংশে পরিণত হচ্ছে, দেশের মানুষের খাবার টেবিল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
ইলিশ রক্ষায় সরকার জাটকা ধরা নিষিদ্ধ, প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরা বন্ধ—এসব আইন করেছে। কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনো কার্যকর আইন নেই। কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে শাস্তির কথা বলা হলেও বাস্তবে তেমন নজির নেই। ফলে সিন্ডিকেট আইনের চোখে অদৃশ্য থেকে যায়। আইনের প্রয়োগহীনতা সিন্ডিকেটের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতির নিয়ম বলে, সরবরাহ বাড়লে দাম কমে। কিন্তু ইলিশের বাজারে ঠিক উল্টো দৃশ্য। উৎপাদন বাড়ছে, দামও বাড়ছে। এটি প্রমাণ করে—এখানে বাজার স্বাধীন নয়। অদৃশ্য শক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দাম বাড়াচ্ছে। এভাবে অর্থনীতির মৌলিক নিয়মকেই ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের জেলেদের ঘরে ইলিশ সহজলভ্য হলেও ঢাকাসহ বড় শহরের বাজারে তার দাম আকাশচুম্বী। অর্থাৎ এক দেশের ভেতরেই অঞ্চলভেদে মূল্যবৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এটি কেবল বাজারের ব্যর্থতা নয়, সরকারিভাবে সরবরাহ চেইন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতারও প্রতিফলন।
জাতীয় মাছের মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন?
জাতীয় প্রতীক মানে সেটি হবে সবার জন্য সমান অধিকারসম্পন্ন ও সহজলভ্য। বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ তাই শুধু একটি খাবার নয়, বরং সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতিসত্তার অংশ। কবিতা, গান, প্রবাদ-প্রবচনে ইলিশকে ঘিরে যে আবেগ গড়ে উঠেছে, তা আসলে জাতীয় পরিচয়েরই অংশ। কিন্তু যখন এই জাতীয় মাছ ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন এর “জাতীয়” মর্যাদা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। ইলিশ যদি কেবল অভিজাত শ্রেণির প্লেটে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তবে সেটি আর জাতীয় থাকে না—বরং বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক পণ্য হয়ে দাঁড়ায়। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি। উৎপাদন বাড়লেও বাজারে সিন্ডিকেটের কারসাজির কারণে দামে আগুন লাগে। অথচ সরকারের নীরবতা ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে এই সংকট টিকে যায়। এর মধ্য দিয়ে কেবল অর্থনৈতিক শোষণই ঘটে না, বরং জাতীয় প্রতীকের সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণা হয়। কারণ “জাতীয়” মর্যাদার যে প্রতিশ্রুতি—সবাই সমানভাবে ভোগ করবে—তা বাস্তবে বিলীন হয়ে যায়। জাতীয় মাছ হয়ে ওঠে কাগুজে মর্যাদার প্রতীক, কিন্তু বাস্তবে তা মানুষের জন্য অধরা বিলাসে পরিণত হয়।
ভোক্তার প্রতিবাদ কোথায়?
বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মাঝে মাঝে জনঅসন্তোষ দেখা যায়, বাজারে বা সামাজিক মাধ্যমে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে। কিন্তু ইলিশের দামে অস্বাভাবিক উল্লম্ফন ঘটলেও সেই তুলনায় তেমন কোনো প্রতিবাদ বা আন্দোলন চোখে পড়ে না। এর মূল কারণ হলো—ইলিশকে ধীরে ধীরে বিলাসী পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ভাবতে শিখেছে, “না খেলেও চলে।” অর্থাৎ ইলিশকে অপরিহার্য খাবার হিসেবে না দেখে এখন বিশেষ দিনে বা উৎসবে খাওয়ার একটি বিলাসবস্তু হিসেবে গ্রহণ করছে। এই মানসিকতা সিন্ডিকেটকে আরও বেপরোয়া করে তুলছে। কারণ বাজারে যদি ক্রেতার প্রতিরোধ বা গণচাপ না থাকে, তবে ব্যবসায়ীরা অবাধে দাম বাড়াতে পারে। ধীরে ধীরে একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠছে, যারা ইলিশকে প্রতিদিনের খাবার হিসেবে চিনেই না, বরং মনে করে এটি শুধু উৎসবের জন্য। এর ফলে জাতীয় মাছের সামাজিক গুরুত্ব ক্ষয় হচ্ছে, আর ভোক্তার নীরবতা ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়ে তুলছে। রাষ্ট্র যখন কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করছে না, তখন জনগণের নীরবতাও হয়ে উঠছে বাজার নিয়ন্ত্রণে একটি অদৃশ্য সহায়ক শক্তি।
ইলিশের দামে আগুন, কারা পুড়ছে? ইলিশ উৎপাদন বেড়েছে, চাষ করতেও খরচ নেই কিন্তু বাজারে আগুন। এই বৈপরীত্যের দায় কেবল সিন্ডিকেটের নয়, সরকারের নীরবতাও সমানভাবে দায়ী। আজ সময় এসেছে সরকারের কাছে কঠিন প্রশ্ন রাখার—জাতীয় মাছের দামে এই শুভঙ্করের ফাঁকি আর কতকাল চলবে?
লেখক: সাংবাদিক, সমাজ গবেষক, মহাসচিব-কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ।
পাঠকের মতামত:
- চাটমোহরে মহিলা দল নেত্রী রহিমা রেজা বহিষ্কার
- ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে পাঁচ দফা দাবি ‘সংগ্রাম কমিটি’র
- ফরিদপুরে সেলিম ফকিরের বাড়িতে দুই দিনব্যাপী বাৎসরিক ওয়াজ শুরু
- ফতেপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে মানববন্ধন
- চাটমোহরে রাজার উদ্যোগে বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন
- সাতক্ষীরায় মুক্তি সাউথ এশিয়া প্র জেলা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ অ্যাডভোকেসি সভা
- নাটোর থেকে অপহৃত বিকাশ কর্মীকে টাঙ্গাইল থেকে উদ্ধার
- নড়াইলে নবাগত পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলামের যোগদান
- যশোরে সিআইডি পুলিশের ওপর হামলা, মাদক ব্যবসায়ীকে ছিনিয়ে নিল চক্র
- নড়াইলে ৫ দিনব্যাপী আইজিএ ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী
- ‘পাবনা-৩ এর জনগণ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে আপনার উচিত সম্মানের সাথে চলে যাওয়া’
- নড়াইলে মধুমতী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও পরিবহন, ২ শ্রমিককে জেল জরিমানা
- বিপদের বন্ধু লোকনাথ বাবা ও তাঁর অলৌকিক কাহিনী
- দেশের বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে অনার ৪০০ লাইট ফাইভজি স্মার্টফোন
- ‘তোমরা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের মান রাখবে’
- শেখ হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ দিতে দুদকের চিঠি
- ‘র্যাবের বন্দিশালায় থাকা ব্যারিস্টার আরমানের মুক্তির চেষ্টা করেছি’
- অন্যকে সাহায্য করুন, নিজের হৃদয়ও পূর্ণ করুন
- শিক্ষক পরিষদের নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন
- ফুলপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি সমাবেশ
- সাতক্ষীরায় চিহিৃত সন্ত্রাসী কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার
- উৎপাদন খরচ ছাড়া ইলিশের এত দাম কেন?
- সুবর্ণচরে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত
- বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প
- কোটচাঁদপুরে শেয়াল মারা বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে গরুসহ কৃষকের মৃত্যু
- অপারেশন থিয়েটারে রোগীর সাথে টিকটক, সিলগালা করলো স্বাস্থ্য বিভাগ
- ড. ইউনূসকে নিয়ে বই লিখে তাকে উপহার দিলেন ব্রাজিলের সেকেন্ড লেডি লু
- ‘৭ কলেজ নিয়ে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় দাবি যৌক্তিক নয়’
- মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে রুমা বেগম
- দেশের বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে অনার ৪০০ লাইট ফাইভজি স্মার্টফোন
- নোয়াখালীতে সাংবাদিক কল্যাণ এসোসিয়েশনের ইফতার ও ঈদ উপহার বিতরণ
- দুরারোগ্য রোগে প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছেন উৎপল সরকার
- নতুন বছর
- বিপদের বন্ধু লোকনাথ বাবা ও তাঁর অলৌকিক কাহিনী
- পদ্মা নদীর ভরাট বালু বিক্রির অভিযোগে দেড় লাখ টাকা জরিমানা
- স্লিম ডিজাইন ও শক্তিশালী পারফরম্যান্সে হট সিরিজের নতুন ফোন আনছে ইনিফিনিক্স
- ঝালকাঠিতে ৩ মামলায় কৃষক লীগ নেতা ও সাবেক পিপি আবদুল মান্নান কারাগারে
- বুধবার প্রদান করা হবে 'গ্র্যাজুয়েট স্বাধীনতা এওয়ার্ড ২০২৪'
- লক্ষ্মীপুরে ভূমিসেবা সপ্তাহ উপলক্ষে জনসচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত
- মালদ্বীপ থেকে রেমিট্যান্স পাঠাতে ভোগান্তি, স্থায়ী সমাধান চান প্রবাসীরা
- পঞ্চগড় গভর্নমেন্ট অ্যান্ড টেন্ডারার্স ফোরামের কর্মশালা
- সভাপতির বিরুদ্ধে সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগ
- বিশাল জয়ে লিগসেরা হয়েই ফাইনালে বাংলাদেশ
- পীযূষ সিকদার’র কবিতা
- ‘ক্ষমতা ছেড়ে দিন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবো’
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
- বিপদের বন্ধু লোকনাথ বাবা ও তাঁর অলৌকিক কাহিনী
- উৎপাদন খরচ ছাড়া ইলিশের এত দাম কেন?
- রাজাকার অপশক্তি: কত দূর যেতে চায় ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ
-1.gif)
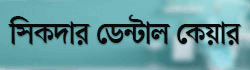

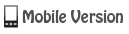




































-12.07.25.jpg&w=60&h=50)


.jpg&w=60&h=50)






















